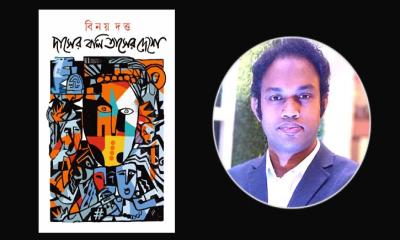দুইটি কারণে নবীন লেখক সৈয়দ মুস্তাফিজুর রহমান—ওরফে মুস্তাফিজ সৈয়দ—লিখিত ‘শিক্ষা সঞ্জীবনী’ বইটি আমার মনে ধরিয়াছে। প্রথম কারণ বইটির নাম। দ্বিতীয় কারণ আহমদ ছফা। বইয়ের শেষ নিবন্ধে আহমদ ছফার চিন্তার সহিত আমাদের পরিচয় ঘটাইবার যে উদ্যোগ মুস্তাফিজ সৈয়দ গ্রহণ করিয়াছেন তাহা এই বইয়ের সবচেয়ে বড় গৌরবের জিনিশ।
কথাটা একটু গোছাইয়া বলিতে হয়। আহমদ ছফা ১৯৯৩ সালের নবেম্বর মাসে ‘অনানুষ্ঠানিক শিশুশিক্ষা প্রসঙ্গে’ শিরোনাম দিয়া একটি নাতিদীর্ঘ নিবন্ধ লিখিয়াছিলেন। ঐ নিবন্ধে তিনি নিজের জীবনের একটি স্মরণীয় ঘটনার বিবরণ দিয়াছিলেন। ইহা ১৯৮২ সালের কথা। আপনকার ঘনিষ্ঠ বন্ধু নাজিম উদ্দীন মোস্তানের সহায়তায় নীলক্ষেতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উত্তরদিকে কাঁটাবন বস্তিতে শিশুদের শিক্ষা দেওয়ার একটা পাঠশালা তিনি খুলিয়াছিলেন। পাঠশালাটি তাঁহারা সাত-আট মাসের বেশি চালাইতে পারেন নাই।
আহমদ ছফার চরিত্রে—সত্যপ্রীতি না বন্ধুবাৎসল্য—কোন জিনিশটি বড় ছিল তাহা নির্ণয় করা কঠিন। নীচের এই কয়টি বাক্যেও তাহার প্রমাণ মিলিবে: ‘এখানে বলে রাখা ভালো, স্কুল চালানোর ব্যাপারে আমার কোন কৃতিত্ব ছিল না। সিলেবাস তৈরি, শিক্ষকতার কাজ সবকিছু একা মোস্তান ভাই করতেন। তাঁকে রেজা নামের একটি যুবক সাহায্য করতো। অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে এই সুন্দরপ্রাণ যুবকটি অকালে মারা যায়। নাজিম উদ্দীন মোস্তান সাহেবের মতো এরকম নিষ্ঠাবান শিশুদের দরদী মানুষ আমি জীবনে দুটি দেখিনি। সব মিলিয়ে স্কুলটি আমরা সাত-আট মাসের বেশি চালাতে পারিনি।’
এই সাত-আট মাসের অভিজ্ঞতা হইতে আহমদ ছফা একপ্রস্ত অমূল্য শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। এই শিক্ষার কথাটাই মুস্তাফিজ সৈয়দের চোখে পড়িয়াছে। আমি তাই, শুদ্ধ আহমদ ছফাকে নহে, তাঁহাকেও অভিনন্দন জানাইতেছি। আহমদ ছফা লিখিয়াছিলেন: ‘বস্তির শিশুদের লেখাপড়া শেখাতে গিয়ে যে জিনিশটি আমাদের সর্বপ্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করে সেটি হল বস্তির শিশুদের গ্রহণশক্তি গড়পড়তা মধ্যবিত্ত শিশুদের চেয়ে অনেক প্রখর। শেখানোর পদ্ধতিটি যদি আনন্দময় হয়, তাহলে তারা খুব তাড়াতাড়ি আয়ত্ত করতে পারে।’
সাফাইস্বরূপ তিনি আরো একটু লিখিয়াছেন: ‘বস্তির শিশুদের নিয়ে আমরা একটা ফুটবল টিম করেছিলাম। আমাদের অভিজ্ঞতা এই যে, ওই বয়সের মধ্যবিত্ত শিশুদের চেয়ে তারা অনেক বেশি চৌকস। আমরা যে শিশুদের লেখাপড়া শেখাতাম তারা ছিল একেবারে বিত্তহীন মা-বাবার ছেলেমেয়ে। এই শিশুরা নিজেরাই নানারকম কাজকর্ম করে মা-বাবাদের সাহায্য করতো। কেউ রাস্তায় ছেঁড়া পুরনো কাগজ কুড়াতো, কেউ লোহা-লক্কড়ের টুকরো সংগ্রহ করতো। আবার কেউ নিউ মার্কেট অঞ্চলে মিনতির কাজ করতো। এরকম নানা ধরনের কাজ করে শিশুরা দৈনিক ৮/১০ টাকা উপার্জন করতো।’
এই রোজগারে শিশুদের দেখিয়া আহমদ ছফা মনে মনে আরেকটি শিক্ষালাভ করেন। সে কথাটা তাঁহার জবানিতেই বলি: ‘আমাদের দেশের প্রাইমারি স্কুলগুলোতে যে পরিমাণ ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি হয়, দ্বিতীয় কিংবা তৃতীয় বছরে গিয়ে দেখা যায় তার পরিমাণ অর্ধেকে চলে এসেছে। সংখ্যাটি হ্রাস পাওয়ার একটি কারণ এই যে, শিশুদের বাবা-মাকে নানা কাজে সহায়তা করতে হয়। ছেলেদের বাবার জন্য মাঠে ভাত নিয়ে যেতে হয়, হুঁকোটি দিয়ে আসতে হয়, গরু রাখতে হয় এবং মেয়েদের মাকে রান্নাবাড়ার কাজে সাহায্য করতে হয়। যেহেতু বেশির ভাগ মা-বাবা অভাবী, ছেলেমেয়েদের দিয়ে এসব কাজ না করিয়ে তারা পারেন না। তাই ছেলেমেয়েদের স্কুল থেকে ছাড়িয়ে আনতে হয়।’
এই সত্য জানেন বলিয়াই আহমদ ছফা পরামর্শ দিলেন: ‘স্কুলে যদি ছেলেমেয়েদের কোন কাজের ব্যবস্থা করা হতো, যেগুলো করতে শিশুদের বিশেষ বেগ পেতে হতো না, বরং শরীর গঠনের সহায়ক হতো এবং সপ্তাহে কিংবা মাস অন্তর শিশুদের কিছু টাকা শ্রমের মূল্য হিসাবে পরিশোধ করা হতো, আমার বিশ্বাস অভিভাবকরা তাদের ছেলেমেয়েদের স্কুল থেকে ছাড়িয়ে নিতেন না।’ এই দেশে এখনও যাহারা স্কুল হইতে শিশুদের ‘ঝরিয়া পড়া’ লইয়া মায়াকান্না করিতেছেন তাহাদের জন্য এখানেও একটি বড় শিক্ষার জিনিশ আছে।
মাত্র এই একটি অন্তর্দৃষ্টি আর একটি অভিজ্ঞতার কথা ভাবিয়া দেখিলেও বুঝিতে পারা যায় আহমদ ছফা কেমন মানুষ ছিলেন। হাজারো চোখধাঁধানো কথার অরণ্যে তাঁহার যে কথাটি কোনদিন হারাইবার নহে—যাহা অপরিমেয় সত্য—তাহা এই: ‘মানুষ যে জ্ঞানে-বিজ্ঞানে এতদূর উন্নতি সাধন করেছে তার মূল কারণ শিক্ষা। কিন্তু মনে রাখতে হবে, মানুষের শিশুকে শিক্ষা দেয়ার পদ্ধতি অনেক বেশি ধৈর্য ও পরিশ্রমসাপেক্ষ এবং যথেষ্ট পরিমাণে ধীরগতিসম্পন্ন।’
আহমদ ছফার এই অমর কথাগুলির সঙ্গে আমাদের নতুন করিয়া পরিচয় করিয়া দিবার জন্য মুস্তাফিজ সৈয়দকে কৃতজ্ঞতা নিবেদন করিতেছি। আশঙ্কার মধ্যে, এই দেশের যাঁহারা হর্তা-কর্তা-বিধাতা তাঁহারা এখনও আহমদ ছফার লেখা পড়িবার যোগ্য হইয়া ওঠেন নাই। ইহাই আমাদের ভাষায় যাহাকে বলে ভাবের ঘরে চুরি।
২৯ নবেম্বর ২০২১
দোহাই
১. আহমদ ছফা, ‘অনানুষ্ঠানিক শিশুশিক্ষা প্রসঙ্গে,’ আহমদ ছফা রচনাবলি, ২য় খণ্ড, নূরুল আনোয়ার সম্পাদিত (ঢাকা: খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানি, ২০০৮), পৃ. ২৮৬-২৮৯।