লালন মানবতা, আধ্যাত্মিকতা কিংবা মনস্তাত্ত্বিক দর্শনের এক মূর্ত প্রতীক। যার মানবতাবাদী দর্শন পৌঁছে গেছে এক কাঁটাতার পেরিয়ে অন্য কাঁটাতারে। বর্তমান সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে লালনকে শুধু একজন বাউল বলে আখ্যা দিলে তা হবে মৌলিক মূর্খতা। বর্তমান সময়কে সঙ্গে নিয়ে চলতে লালনকে একজন আদর্শ হিসেবে ধরা যেতেই পারে, কারণ তার মতো ইতিহাসে কেউ মানবতা, মনু্ষ্যত্বের দর্শন তুলে আনেনি।
লালন মানুষকে শুধু মানুষ বলেই গণ্য করতেন। কারণ, তিনি মনে করতেন ‘মানুষ ভজলে সোনার মানুষ হবি।’ ধর্মের নামে মানুষে মানুষে যে ব্যবচ্ছেদের দেয়াল গড়ে উঠেছে, তা অনেক আগেই ভেঙে ফেলে মানুষের জন্য সুন্দর একটা পৃথিবী প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেছেন এবং তা বাস্তবায়নের চেষ্টা করেছেন লালন। এ ছাড়া লালন শাহ ছিলেন সমাজ সংস্কারক, তিনি সমাজে গোত্র-বর্ণের বিভেদ ভেঙে দিয়েছিলেন, যা পরিলক্ষিত হয় শুধু তার শিষ্যত্ব গ্রহণ করা শিষ্যদের মধ্যে। কারণ, সাধারণ মানুষ সব সময়ই বর্ণ, গোত্র, ধর্ম এসবের বিভেদকে ধুতরা ফুল ভেবে পরিহার করতেন এবং বর্তমানেও করেন। মোল্লার ঘরের পানি কিংবা পূজারির প্রসাদ আহার নিষিদ্ধতা, এসব মূলত ধর্মে ধর্মে ব্যবচ্ছেদের যে দেয়াল তারই প্রমাণ দেয়, কিন্তু লালন তা পরিহার করেছিলেন।
লালন সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন:
“লালন ফকির নামে একজন বাউল সাধক হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, জৈন ধর্মের সমন্বয় করে কী যেন একটা বলতে চেয়েছেন, আমাদের সবারই সেদিকে মনোযোগ দেওয়া উচিত।’
রবিঠাকুরের সেই কথা ধরে এগোলে লালন সব সময় বলেছেন মানুষের কথা, মানবতার কথা, মানবতাবাদী দর্শনের কথা, আমাদের সেদিকে মনোযোগ দেওয়া উচিত। কারণ, এখন সময় এসেছে সমাজের সব কুসংস্কার ভেঙে দিয়ে শুধু মানুষ ভজবার সময়। মানুষ ভজলেই আমরা পরিপূর্ণ হব ধ্যানে, জ্ঞানে, দর্শনে সবদিকে।
লালন তার জীবনযাত্রায় যত দিন বেঁচে ছিলেন, কখনোই তাকে কোনো ধর্মের অনুশাসন মানতে দেখা যায়নি। তিনি পালন করতেন বাউল মতবাদ, সব সময় বাউলতত্ত্বের কথা বলতেন মানুষের সামনে। বাউল মতবাদকে একটি মানস পুরাণ বলা হয়। দেহের আধারে যে চেতনা বিরাজ করছে, সে-ই আত্মা। এই আত্মার খোঁজ বা সন্ধানই হচ্ছে বাউল মতবাদের প্রধান লক্ষ্য। ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে একে পৃথক দর্শন বোঝায়। বাউলতত্ত্ব হলো দেহের ভেতর আত্মার সাধন। বাউলরা ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, জাত-পাত এসব কিছুতে বিশ্বাস করতেন না তারা বিশ্বাস করতেন দেহের ভেতরে আত্মার বাস আর আত্মাকে যদি সন্তুষ্ট করতে হয়, তবে দেহের ভেতর তার সাধনা করতে হবে, সব সময় পবিত্র রাখতে হবে দেহকে। কারণ, আত্মার সন্তুষ্টি লাভে পবিত্রতা এক অনিবার্য প্রক্রিয়া। এ জন্যই লালন তার গানে বলেছিলেন, ‘খাঁচার ভেতর অচিন পাখি কেমনে আসে যায়।’ এখানে তিনি বলতে চেয়েছেন নিজের দেহের ভেতর আত্মার বসবাস, সে কখন যায় কখন আসে কিছুই বোঝার সাধ্য নেই, তবু এই আসা-যাওয়া বুঝে ওঠার ক্ষমতা এই মানবদেহের নেই, শুধু পবিত্রতার মাধ্যমেই তাকে সন্তুষ্ট করা যায়, এতে বাউলদের ঘটে আত্মতুষ্টি।
লালনের ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে ঔপন্যাসিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় বলেছেন, “লালন ধার্মিক ছিলেন, কিন্তু কোনো বিশেষ ধর্মের রীতিনীতি পালনে আগ্রহী ছিলেন না। সব ধর্মের বন্ধন ছিন্ন করে মানবতাকে সর্বোচ্চ স্থান দিয়েছিলেন জীবনে।”
তার মৃত্যুর পর প্রকাশিত প্রবাসী পত্রিকার মহাত্মা লালন নিবন্ধে প্রথম লালন জীবনী রচয়িতা বসন্ত কুমার পাল বলেছেন, “সাঁইজি হিন্দু কি মুসলমান, এ কথা আমিও স্থির বলিতে অক্ষম।”।
লালন অনুসারী মন্টু শাহের মতে, তিনি হিন্দু বা মুসলমান কোনোটিই ছিলেন না বরং তিনি ছিলেন ওহেদানিয়াত নামক একটি নতুন ধর্মীয় মতবাদের অনুসারী।
লালনের গানে মানুষ ও তার সমাজই ছিল মুখ্য। লালন বিশ্বাস করতেন সকল মানুষের মাঝে বাস করে এক মনের মানুষ। আর সেই মনের মানুষের সন্ধান পাওয়া যায় আত্মসাধনার মাধ্যমে। দেহের ভেতরেই মনের মানুষ বা যাকে তিনি অচিন পাখি বলেছেন, তার বাস। সেই অচিন পাখির সন্ধান মেলে পার্থিব দেহ সাধনার ভেতর দিয়ে দেহোত্তর জগতে পৌঁছানোর মাধ্যমে। আর এটাই বাউলতত্ত্বে ‘নির্বাণ’ বা ‘মোক্ষ’ বা ‘মহামুক্তি’ লাভ এবং নির্বাণ হলো দেহের সাত গুণের সমন্বয়, যে সাত গুণ মানুষের দেহকে পবিত্রতা দান করে। তিনি সবকিছুর ঊর্ধ্বে মানবতাবাদকে সর্বোচ্চ স্থান দিয়েছেন। তাঁর বহু গানে এই মনের মানুষের প্রসঙ্গ উল্লিখিত হয়েছে। তিনি বিশ্বাস করতেন মনের মানুষের কোনো ধর্ম, জাত, বর্ণ, লিঙ্গ, কুল নেই। মানুষের দৃশ্যমান শরীর এবং অদৃশ্য মনের মানুষ পরস্পর বিচ্ছিন্ন, কিন্তু শরীরেই মনের বাস। সব মানুষের মনে ঈশ্বর বাস করেন। লালনের এই দর্শনকে কোনো ধর্মীয় আদর্শের অন্তর্গত করা যায় না। লালন, মানব আত্মাকে বিবেচনা করেছেন রহস্যময়, অজানা এবং অস্পৃশ্য এক সত্তা রূপে। খাঁচার ভিতর অচিন পাখি গানে তিনি মনের অভ্যন্তরের সত্তাকে তুলনা করেছেন এমন এক পাখির সঙ্গে, যা সহজেই খাঁচারূপী দেহের মাঝে আসা-যাওয়া করে, কিন্তু একে বন্দি করে রাখা যায় না।
বাউলদের আদি জগন্মোহিনী সম্প্রদায়ের জপতপের মূলমন্ত্র ‘গুরু সত্য’। এরা পরলোকগত গুরুর পাদুকা বা জুতাকে সযত্নে সংরক্ষণ করে ভক্তি শ্রদ্ধা করে। বিবাহ-শাদিও হয় তাদের নিজস্ব তরিকায়। এরা কোনো ধরনের জাতপাতের ধার ধারে না। এদের মধ্যে ছোঁয়াছুঁইরও কোনো বালাই নেই। এ সম্প্রদায়ের বাউলরা তিন ভাগে বিভক্ত। গৃহী, সংযোগী ও উদাসী। এটি বেশ প্রাচীন ধারা। তারা মনে করেন, এই এক জীবনে স্রষ্টার ভালোবাসা পাওয়া যথেষ্ট, তবে সে ভালোবাসা খুব সহজে পাওয়া সম্ভব নয়। এর জন্য প্রচুর সাধনা করতে হবে। আনুমানিক ১৪৫০ খ্রিষ্টাব্দে হবিগঞ্জ জেলার মাধবপুর উপজেলার বাঘাসুরা গ্রামে জগমোহন গোসাঈর জন্ম হয়। তার পিতার নাম সুধবানন্দ, মাতার নাম কমলা। তিনি জগন্মোহিনী বাউল সম্প্রদায়ের প্রবর্তক। তাকে আদি বৈষ্ণব ধর্মের প্রবর্তক হিসেবেও গণ্য করা হয়। হবিগঞ্জ সদর উপজেলার মাছুলিয়া গ্রামে তার আখড়া বিদ্যমান। মাছুলিয়ার বিজনবনে বসে তিনি ধ্যান করতেন বলে জানা যায়। তার শ্যাম ও সুদাম নামে দুইজন পুত্রসন্তান ছিল। তারা তাদের পিতার কথা জানতে ফেরে মাছুলিয়ার বিজনবনে তপস্যারত জগন্মোহনের নিকট উপস্থিত হন। পিতা, পুত্রের এই করুণ কান্নার ধ্বনি জগন্মোহন গোসাইর প্রথম শিষ্য গোবিন্দ গোসাই তাহা অবলোকন করেন। পরবর্তী সময়ে জগন্মোহিনী গোঁসাইর এই বাউল তত্ত্বে মন মজে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষদের এবং তারা বেশ পবিত্রতার সঙ্গে দেহের ভেতর পাখিরূপী আত্মাকে ধ্যানের মাধ্যমে পরিশুদ্ধ করে তোলেন।
লালনের জীবদ্দশায় তৎকালীন সমাজের দাবি ছিল তিনি তার আখড়ায় সাধক সঙ্গিনী বা সেবাদাসী রূপে একটি প্রথা চালু করেছিলেন। যার ফলে হিন্দু মুসলমান নারী-পুরুষের বিবাহ বা বিবাহবহির্ভূত যৌনাচার সংঘটিত হতো। এ ছাড়া আখড়ায় মাদকসেবনের জন্যও তিনি ও তার শিষ্যগণ সমালোচিত হয়েছিলেন।
আসলে এসব হলো রহস্য যা দুর্ভেদ্য, এসব রহস্য কখনো বের করা যাবে কি না, তা অনিশ্চিত। লালনকে ঘিরে এমন হাজারো রহস্য রয়েছে, যা লালনের সময়ে গিয়ে বিশ্লেষণ না করলে এসব ভেদ করা সম্ভব হবে না। তাই এসব রহস্য নিয়ে কথা না বলে আমরা বরং তার সৃষ্টিকর্ম, সৃজনশীলতা তার দর্শন নিয়েই বিশ্লেষণে মেতে থাকি।
বাউল মতবাদ বিষয়ে দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ বলেছেন, ‘ইদানীং বাউল শব্দের উৎপত্তি নিয়ে নানা বাগবিতণ্ডার সৃষ্টি হয়েছে। কেউবা একে সংস্কৃত “বতুল” (উন্মাদ, পাগল, ক্ষেপা, ছন্নছাড়া, উদাসী) শব্দের অপভ্রংশ বলে মনে করেন। তবে যা থেকেই বাউল শব্দের উৎপত্তি হোক না কেন, বর্তমানে বাউল মতবাদ একটি বিশেষ মতবাদে পরিণত হয়েছে।’
তবে বর্তমান সমটার ঘূর্ণিপাকে বাউলতত্ত্ব বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে সবেচেয়ে শক্তিশালী মনস্তত্ত্বের স্রষ্টা হলো বাউলরা, যারা মানুষের আত্মা, পরিশুদ্ধতা, পবিত্রতা এবং সাধনার গভীরে গিয়ে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন তত্ত্বের উদ্ভাবন ঘটিয়ে তা মানুষের অন্তর্নিহিত করতে চেয়েছেন।
লালনের গান ও দর্শন যুগে যুগে প্রভাবিত করেছেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম, অ্যালেন গিন্সবার্গের মতো অনেক খ্যাতনামা কবি, সাহিত্যিক, দার্শনিক ও বুদ্ধিজীবীদের।
বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ লালনের মৃত্যুর দুই বছর পর তার আখড়া বাড়িতে যান এবং লালনের দর্শনে প্রভাবিত হয়ে ১৫০টি গান রচনা করেন।
আমেরিকান কবি অ্যালেন গিন্সবার্গ লালনের দর্শনে প্রভাবিত হয়ে তার রচনাবলিতেও লালনের রচনাশৈলীর অনুকরণ করতে দেখা যায়। তিনি আফটার লালন (After Lalon) নামে একটি কবিতাও রচনা করেন।
ভারত উপমহাদেশে লালনকে সর্বপ্রথম ‘মহাত্মা’ উপাধি দেওয়া হয়, যা গান্ধীজিকে এই উপাধি দেওয়ারও ২৫ বছর আগে। তাঁর মৃত্যুর ১২ দিন পর তৎকালীন পাক্ষিক পত্রিকা মীর মশাররফ হোসেন সম্পাদিত হিতকরী-তে প্রকাশিত একটি রচনায় সর্বপ্রথম তাঁকে ‘মহাত্মা’ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। রচনার লেখকের নাম রাইচরণ।
লালন তার গানে বলেছেন, ‘মানুষ ছাড়া ক্ষ্যাপা রে তুই মূল হারাবি, মানুষ ভজলে সোনার মানুষ হবি।’ অর্থাৎ মানুষ ছাড়া এই ক্ষ্যাপা মন আত্মতত্ত্বের নিগূঢ়ার্থে কখনোই পৌঁছাতে পারবে না। কারণ আত্মতত্ত্বের নিগূঢ়তম ভাবনায় ডুবতে হলে মানুষ ভজতে হবে ভাঙতে হবে জাতপাতের, ধর্ম, বর্ণের ব্যবচ্ছেদের দেয়াল শুধু খুঁজতে হবে অপাপবিদ্ধ, নির্বাণ আত্মা।
লালন তার আরেকটি গানে বলেছেন, ‘সহজ মানুষ ভজে দেখ না রে মন দিব্যজ্ঞানে।’ অর্থাৎ মানুষকেই ঈশ্বর জ্ঞানে ভজ, কারণ ঈশ্বরের বাস মানুষের মাঝে আত্মারূপে তাই মানুষের মাঝেই উপলব্ধি করো ঈশ্বরকে।
লালন তার আরেকটি গানে বলেছেন, ‘ব্রাহ্মণ, চন্ডাল, চামার, মুচি একজলে সব হয় গো সূচী, দেখে শুনে হয় না রুচি যমে তো কাউকে ছাড়বে না’ এই গানে লালন স্পষ্টতই এই সমাজের জাত-পাত এবং গোত্র, বর্ণের ভেদাভেদকে ইঙ্গিত করেছেন তিনি বলেছেন ব্রাহ্মণ, চন্ডাল, চামার, মুচি সবাই একজলেই শুদ্ধ হবে, পরিতৃপ্ত হবে দেখে শুনে রুচি হয় না, রুচি হয় তার আত্মার পবিত্রতায়, পরিশুদ্ধতায় তবে পবিত্রতা, পরিশুদ্ধতা না থাকলে যমে কাউকে ছাড়বে না, সে যেই হোক ব্রাহ্মণ, চন্ডাল, চামার কিংবা মুচি।
এভাবে আধ্যাত্মিক ভাবধারায় তিনি প্রায় দুই হাজার গান রচনা করেছিলেন। আত্মতত্ত্ব, দেহতত্ত্ব, গুরু বা মুর্শিদতত্ত্ব, প্রেম-ভক্তিতত্ত্ব, সাধনতত্ত্ব, মানুষ-পরমতত্ত্ব, আল্লাহ-নবীতত্ত্ব, কৃষ্ণ-গৌরতত্ত্ব এবং আরও বিভিন্ন বিষয়ে লালনের গান রয়েছে। বাউল গান বাংলার ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতিকে দীর্ঘদিন যাবৎ বহন করে আসছে এখনো বহন করছে। বিভিন্ন দেশের মানুষের কাছে বাংলাদেশের বাউলসংগীত বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ করেছে আর বাউলসংগীত বেশ সমৃদ্ধ এবং সহজিয়া প্রকৃতির, যার জন্য মানুষ তা সহজে আত্মস্থ করতে পারে।
২০০৫ সালে ইউনেসকো বাউল গানকে বিশ্বের মৌখিক এবং দৃশ্যমান ঐতিহ্যসমূহের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদ হিসেবে ঘোষণা করে। এতে বাংলাদেশ উন্নত সাংস্কৃতির পদযাত্রায় আরও এক ধাপ এগিয়ে গেল। কারণ, বাউলসংগীত বাংলার মাটিতে বেশ সমৃদ্ধ এবং মানবতা, মনুষ্যত্ববোধ, মানব হৃদয়কে সমৃদ্ধ করার ভরপুর উপাদান নিয়ে বাউলসংগীত রচিত হয়েছে।
লালনের সংগীত ও ধর্ম-দর্শন নিয়ে দেশ-বিদেশে নানা গবেষণা হয়েছে ও হচ্ছে। ১৯৬৩ ছেউড়িয়ায় আখড়া বাড়ি ঘিরে লালন লোকসাহিত্য কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়। এরপর লালন লোকসাহিত্য কেন্দ্রের বিলুপ্তি ঘটিয়ে ১৯৭৮ সালে শিল্পকলা একাডেমির অধীনে প্রতিষ্ঠিত হয় লালন একাডেমি।
সাম্প্রদায়িক ধর্মবাদীরা লালনের অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গির কারণে তার সর্বাধিক সমালোচনা করতেন এবং এখনো করেন। লালন তার জীবদ্দশায় নিজের ধর্ম পরিচয় কারও কাছে প্রকাশ করেননি। তার ধর্মবিশ্বাস আজও একটি বিতর্কিত বিষয়। লালনের অসাম্প্রদায়িকতা, লিঙ্গবৈষম্যের বিরোধিতা ইত্যাদির কারণে তাকে তার জীবদ্দশায় ধর্মান্ধ এবং মৌলবাদী হিন্দু-মুসলিম সম্প্রদায়ের ঘৃণা, বঞ্চনার এবং আক্রমণের শিকার হতে হয়েছিল। এ ছাড়া তার ধর্মনিরপেক্ষ মানবতাবাদী দর্শন এবং ঈশ্বর, ধর্ম ইত্যাদি বিষয়ে তার উত্থাপিত নানান প্রশ্নের কারণে অনেক ধর্মবাদী তাকে নাস্তিক হিসেবে আখ্যা দেন।
তার জন্মতিথি নিয়ে রহস্যের জাল ঘন হয়ে এলেও মৃত্যুদিন নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই। ১৭ অক্টোবর ১৮৯০ খ্রিষ্টাব্দে ছেউড়িয়া, কুমারখালী, কুষ্টিয়া, অবিভক্ত বাংলায় তিনি দেহত্যাগ করেন। তাঁরই উপদেশ অনুসারে ছেউড়িয়ায় তাঁর আখড়ার মধ্যে একটি ঘরের ভিতর তাঁর সমাধি গড়ে তোলা হয়। আজও বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গ থেকে বাউলেরা ও বিভিন্ন দেশের মানুষেরা অক্টোবর মাসে ছেউড়িয়ায় মিলিত হয়ে লালনের প্রতি তাদের শ্রদ্ধা নিবেদন করেন, গান-বাজনা করেন, লালনকে নিয়ে আলোচনা করেন।
তার মৃত্যুর পনেরো দিন পর কুষ্টিয়া থেকে প্রকাশিত হিতকরী পত্রিকার সম্পাদকীয় নিবন্ধে বলা হয়, “ইহার জীবনী লিখিবার কোন উপকরণ পাওয়া কঠিন। নিজে কিছু বলিতেন না। শিষ্যরা তাঁহার নিষেধক্রমে বা অজ্ঞতাবশত কিছুই বলিতে পারে না।’
তার মৃত্যুদিবসে ছেউড়িয়ার আখড়ায় এখনো স্মরণ উৎসব হয়। দেশ-বিদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে অসংখ্য মানুষ লালন স্মরণোৎসব ও দোল পূর্ণিমায় এই আধ্যাত্মিক সাধকের দর্শন অনুসরণ করতে প্রতিবছর এখানে এসে থাকেন। ২০১০ সাল থেকে এখানে পাঁচ দিনব্যাপী উৎসব হচ্ছে। এই অনুষ্ঠানটি ‘লালন উৎসব’ হিসেবে পরিচিত। ২০১২ সালে এখানে ১২২তম লালন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।
সব দিক বিবেচনা করলে লালন ছিলেন মানবতাবাদী একজন বাউল সাধক, দার্শনিক ও সমাজ সংস্কারক। বর্তমান সমাজের মানুষদের কাছে লালনের কোনো বিকল্প নেই। একমাত্র লালনের পথ অনুসরণ করলেই মানুষ হয়ে উঠবে প্রকৃত মানুষ, সমাজ সুন্দর হবে, পৃথিবী সুন্দর হবে।
তথ্যসূত্র
১. লালন সমগ্র (পাঠক সমাবেশ)
২. উইকিপিডিয়া
৩. মানবতাবাদী লালন শাইজী (সমকাল)
৪. লালন শাহ (কালের কণ্ঠ)
৫. লালন দর্শন (দ্য ডেইলি স্টার)




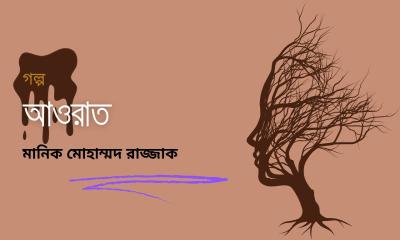
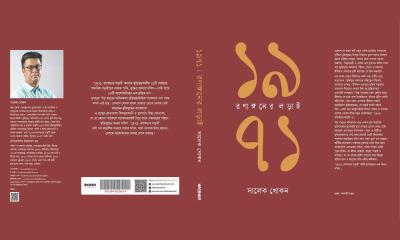


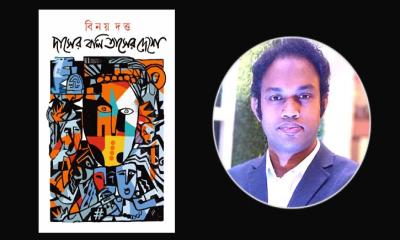




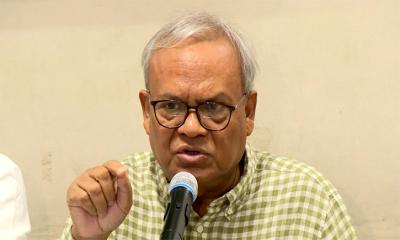






















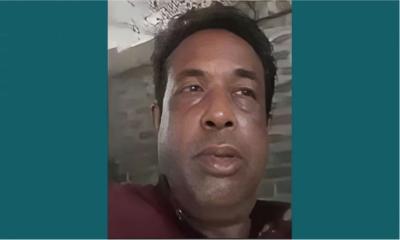



-20230822064119-20250629063054.jpg)








