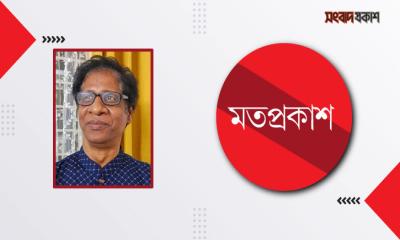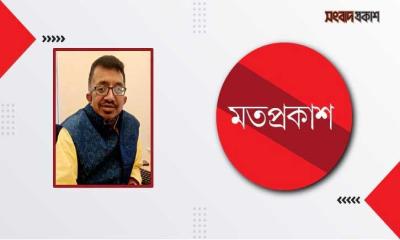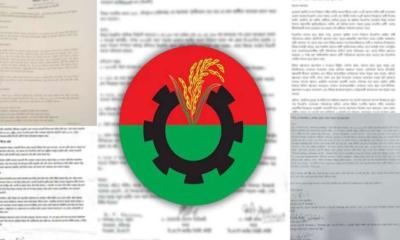সরকার চারদিকে বেশ কিছু বিষয়ে ভালো কাজ করছে, যা আমাদের জন্য অত্যন্ত আনন্দের। কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী উন্নয়নে সব সময় ভূমিকা রাখে শিক্ষা ও সংস্কৃতি। সেই প্রেক্ষিতে সরকারও সাহিত্য-সংস্কৃতি, ইতিহাস-ঐতিহ্যকে গুরুত্ব দেওয়ার কথা বলে। কিন্তু কাজ করতে গেলে হতাশ হতে হয় সংস্কৃতিজনদের। এর মধ্যে গত ৯ জুন ২০২২-২৩ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেট উত্থাপিত হয়। বাজেটের নাম দেওয়া হয়েছে ‘কোভিডের অভিঘাত পেরিয়ে উন্নয়নের ধারাবাহিকতায় পরিবর্তন।’
বাজেটের আকার হলো ৬ লাখ ৭৮ হাজার ৬৪ কোটি টাকার। এতে সংস্কৃতি খাতে ৬৩৭ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে, যা গত অর্থবছরের বাজেটের চেয়ে ৫৮ কোটি টাকা বেশি। ২০২১-২২ অর্থবছরে সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের প্রস্তাবিত বাজেট ছিল ৫৮৭ কোটি টাকার। পরবর্তী সময়ে ৮ কোটি টাকা কমে সংশোধিত হয়ে ৫৭৯ কোটি টাকায় রূপ নেয়।
অর্থমন্ত্রী বাজেট বক্তৃতায় বলেন, সরকার বাঙালি সংস্কৃতির অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ এবং জাতীয় ভাষা, সাহিত্য, শিল্প, সংগীত, নাটক ইত্যাদি সুকুমার শিল্পের সৃজনশীল উন্নয়ন ও বিকাশে কাজ করে যাচ্ছে। কিন্তু বাস্তবতায় হতাশা জামার মতো গায়ে কখনো হ্যাঙ্গারে ঝুলে থাকে আমাদের!
সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সংরক্ষণে রাষ্ট্রযন্ত্রের যে প্রয়াস থাকা উচিত, তা একেবারেই ক্ষীণ। একেবারে নিভু নিভু প্রদীপের মতো। সব মুখে মুখে বুলি, কাজেতে নেই! অনেকটা ‘কাজীর গরু কেতাবে আছে, গোয়ালে নেই’ প্রবাদের মতো। বিষয়টি চিন্তাশীল সমাজের জন্য অত্যন্ত দুঃখজনক।
দেশব্যাপী সংস্কৃতিচর্চাকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ যথেষ্ট নয় বলেও জানান সংস্কৃতিজনেরা। সম্প্রতি ‘সংস্কৃতিকর্মী সমাবেশ’ আয়োজন করে উদীচী। সমাবেশে বক্তারা সংস্কৃতি খাতে জাতীয় বাজেটের ন্যূনতম ১ শতাংশ বরাদ্দের দাবি জানান। সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের সভাপতি গোলাম কুদ্দুছ বলেন, চিন্তা ও মননগত উন্নয়ন না ঘটলে শুধু অর্থনৈতিক উন্নয়ন দিয়ে রাষ্ট্র অগ্রসর হবে না।
আচ্ছা, পুরোনো দিনে আমরা কেমন ছিলাম—ইতিহাসের দিকে চোখ রাখলে একটি জেলার (কুমিল্লা) চিত্র পাই, ১৯৬৮-৬৯ সালে এই জেলায় ৫৬টি গ্রন্থাগার ও ক্লাব ছিল এবং তাদের জন্য ব্যয় ধরা হয়েছিল ৩৯,৩৯০ টাকা। এই পরিমাণের মধ্যে সরকারি রাজস্ব থেকে এসেছিল ৬,৭২০ টাকা, জেলা তহবিল থেকে ২৪,১০০ টাকা এবং চাঁদা বাবদ ৮,৫৫০ টাকা। ১৯৬৬-৬৭ সালের গ্রন্থাগার ও ক্লাবগুলোর সদস্য ছিল ৫,৭১৫। ১৯৬৫-৬৬ সালে এ সংখ্যা ছিল ৪,৫০৩। (বাংলাদেশ প্রথম কুমিল্লা জেলা গেজেটিয়ার/ ১৯৮১)
নিশ্চয় স্বীকার করি, জ্ঞান অর্জনের মাধ্যম পরিবর্তন হয়েছে। পরিবর্তন হয়েছে বিনোদনের কায়দা। সঙ্গে বেড়েছে আমাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। সেটাই দেখব এখন- কেবল চৌদ্দগ্রাম উপজেলায় (১টি পৌরসভা ও ১৩টি ইউনিয়ন) বিভিন্ন মানের ও মনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আছে প্রায় ৫৭২টি, মসজিদ আছে চার শতাধিক, মন্দিরও আছে প্রায় একশ। উপজেলায় শিক্ষার হার ৮০.৩২ শতাংশ।
অন্যদিকে উপজেলায় সাহিত্য সংস্কৃতি সংগঠন ক্লাব, পাঠাগার লাইব্রেরি কয়টা আছে? তার হিসাব প্রশাসনিকভাবে কারও জানা নেই। আমার জানা মতে, ৩টি সংগঠন আছে, ৬টি পাঠাগার আছে, যারা নিয়মিত-অনিয়মিত কাজ করছে। ২৭১.৭৩ বর্গকিলোমিটারের মধ্যে প্রায় ৬ লাখের অধিক জনসংখ্যার জন্য ৬টি পাঠাগার কি যথেষ্ট? ঢাকা ছাড়া এই চিত্র প্রায় সারা দেশের...
চিরায়ত দৃশ্য আমাদের মনে রাখতে হবে মসজিদ-মাদ্রাসায় যায় মুসলমান, মন্দিরে যায় হিন্দুরা। কিন্তু একটা সাহিত্য সংস্কৃতি সংগঠন ক্লাবে, পাঠাগার লাইব্রেরিতে যে কেউ যেতে পারে, যায়। এই জায়গায় আমাদের কাজ করতে হবে, গুরুত্ব দিতে হবে। কারণ, ভালো বই/পাঠাগারের চর্চা হয় সামাজিক মূল্যবোধের, ভূমিকা রাখে নৈতিকতা বিকাশে। দেশ, সমাজ, পরিবারকে এবং প্রাণচঞ্চল জীবনকে ভালোবাসতে শেখায়।
সাম্প্রদায়িক চিন্তা দূর করতে সুস্থ সংস্কৃতিচর্চার কথা সরকার বারবার বলছেন— তাহলে সংস্কৃতি কোথায় চর্চা হচ্ছে, হবে? সেই খবরগুলো রাখতে হবে। আমাদের পরিবারগুলো ভেঙে গেছে। গ্রাম ছাড়াও স্কুলের খেলার মাঠ ভরাট করে ভবন নির্মাণ হচ্ছে। ভুবনে থাকছে না সাধারণ কেউ- সবাই অসাধারণ হয়ে উঠছে। এইভাবে ধীরে ধীরে হারিয়ে যাচ্ছে শান্তি, পিছিয়ে পড়ছে মানুষ! তা কতটা, এটা সবার জানা।
পৌরসভা, ইউনিয়ন, উপজেলা, জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ে বাজেটের কত ভাগ আমরা সংস্কৃতির জন্য বরাদ্দ দিয়েছি? আমাদের আর্থিক সামর্থ্যের ঘাটতি আছে, এই কথা বলে পার পাবার সময় এখন আর নেই। অর্থনীতি বেশ মোটা তাজা, বাজেটের আকারও বিশাল। সরকারি উদ্যোগে সারা দেশে পাঁচশর বেশি মসজিদ নির্মাণ করা হচ্ছে, পাশাপাশি মন্দির ও গির্জাও হোক। মহাশূন্যে যাচ্ছি আমরা, পদ্মায় সেতু করছি, সবই ভালো। অথচ সংস্কৃতি খাতে বাজেটের ১ শতাংশ বরাদ্দ হয় না? সংস্কৃতিকে টিকিয়ে রাখতে হলে, বিস্তার ঘটাতে হলে অর্থায়ন অবশ্য করতে হবে। সরকারের পাশাপাশি অন্যদেরও এগিয়ে আসতে হবে।
খ.
বহুমাত্রিক সংকটের সমাজে আমরা সবাই বাস করছি। নানান চিন্তায় মানুষ আজকাল বিপর্যস্ত হয়ে পার করছে দিনরাত। প্রাক্তন শিক্ষক, সচিব, ব্যবসায়ী মারা যাচ্ছে, স্বজন সন্তান তাদের কাছে কাছে নেই। আধুনিক নিঃসঙ্গতায় কেউ কেউ আত্মহত্যা করছে। হায় শান্তি! আচ্ছা কীভাবে শান্তি আসবে, কে দেবে দুদণ্ড শান্তি—জানা নেই। প্রসঙ্গত মনে পড়ছে, প্রমথ চৌধুরীরর কথা। তিনি বলেছিলেন, ‘লাইব্রেরি হচ্ছে এক ধরনের মনের হাসপাতাল’ আসলে এখনো বইয়ের একটি চিন্তা, কাহিনী কিংবা চরিত্র আপনাকে নিয়ে যাবে দূর থেকে বহুদূর! জটিল অবসাদ থেকে কিছুটা হলে মুক্তি দিতে পারে একটি মনের মতো বই বা একটি কবিতা!
এমন কবিতা ও কবিরা কেমন আছে? কেমন আছে তাদের প্রিয় লাইব্রেরি বা পাঠাগারগুলো? এই নিয়ে দ্য ডেইলি স্টারে গত ৩০ মে ২০২২ তারিখে প্রকাশ হয়েছে দীর্ঘ প্রতিবেদন। ‘গ্রন্থাগারিক সংকটে পাঠাগার, দিন দিন কমছে পাঠক’। জানা যায়, বইকে ঘিরে সারা দেশে রয়েছে অসংখ্য পাঠাগার, তবে কমছে পাঠক। কারণ হিসেবে উঠে আসছে— বেসরকারি বেশির ভাগ পাঠাগারে নেই গ্রন্থাগারিক, পাঠকের চাহিদামতো বইয়েরও সংকট। ব্যক্তিগত উদ্যাগে গড়ে ওঠা পাঠাগারে সরকারি-বেসরকারি পৃষ্ঠপোষকতাও খুব কম। পাঠাগারগুলোর হয়নি আধুনিকায়ন। অন্যদিকে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত বেশির ভাগ পাঠাগারও থাকে বন্ধ।
বিস্তারিত দেখে বল যায় সংকট দেখি সর্বত্র! আমাদের আলো কোথায়। কোথায় আমাদের বাতিঘর? প্রসঙ্গত, অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী সেখানে বলেন, ‘সবাই বলছে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি, কিন্তু কোন দিকে? মনে রাখতে হবে উন্নয়নের বিরাট একটা অংশ সংস্কৃতি, সংস্কৃতির অংশ পাঠাগার। পাঠাগার মানুষকে নানান বিষয় জানতে বুঝতে ভূমিকা রাখে। আধুনিক যুগে মানসিক স্বাস্থ্য ছাড়া কোনো উন্নয়ন দীর্ঘস্থায়ী হবে না। আর মানসিক স্বাস্থ্য সুন্দর রাখতে গভীরভাবে কাজ করে বই ও পাঠাগার, তথা সংস্কৃতির অবিরাম চর্চা।’
সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী আরও বলেন, ‘ব্যক্তিগত উদ্যাগে গড়ে ওঠা পাঠাগারগুলোর দায়িত্ব রাষ্ট্রকেই নিতে হবে, বরাদ্দ বাড়াতে হবে। সেই সঙ্গে গ্রন্থাগারিকদের বারবার প্রশিক্ষণ দিতে হবে। আর পাঠাগারগুলো টিকিয়ে রাখতে সমাজের অন্যদেরও এগিয়ে আসতে হবে।’
কথাসাহিত্যিক ও জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের পরিচালনা পরিষদের সদস্য সেলিনা হোসেন বলেন, ‘পাঠাগার নিয়ে সরকারের বাজেট বাড়ানো নৈতিক দায়িত্ব। তা না হলে সমাজে অন্ধকার নেমে আসবে। গণমানুষের প্রতিষ্ঠানে সংস্কৃতিচর্চা আর কত নিজের থেকে করবে? বেসরকারি পাঠাগারের বিষয়গুলো গুরুত্ব দিয়ে ভাবা উচিত।
প্রতিবেদক জানাচ্ছেন, সারা দেশে সরকারি গ্রন্থাগার আছে ৭১টি। এর বাইরে বেসরকারি ও ব্যক্তিগত উদ্যোগে পরিচালিত ১ হাজার ৫৩২টি গ্রন্থাগার সরকারিভাবে নিবন্ধিত। বাংলাদেশ গ্রন্থসুহৃদ সমিতির প্রকাশনা থেকে পাওয়া যায় বেসরকারি গ্রন্থাগার আছে ১ হাজার ৩৭৬টি। পাঠাগার আন্দোলন বাংলাদেশ নামক সংগঠন দাবি করছে, কেবল ৪৭টি জেলায় ২ হাজার ৫০০টি পাঠাগার আছে। তবে দেশে গ্রন্থাগার বা পাঠাগার কতটি, সে হিসাব সরকারি কোনো সংস্থার কাছে নেই।
গণগ্রন্থাগার সমিতি দেশের সব গণগ্রন্থাগারের তথ্যসংবলিত গ্রন্থ প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছে। জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রও নতুন করে নির্দেশিকা তৈরির উদ্যোগ নিয়েছে বলে জানা গেছে। সরকারি ৭১টি গ্রন্থাগারকে দেখভালের দায়িত্বে আছে সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের অধীন গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর। বেসরকারি গ্রন্থাগারকে পৃষ্ঠপোষকতা দেয় জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র। দুটো প্রতিষ্ঠানই সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের অধীন।
সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের মাধ্যমে বেসরকারি গ্রন্থাগারগুলোকে সরকার বার্ষিক পৃষ্ঠপোষকতা দেয়। এর মধ্যে অর্ধেক টাকা চেকের মাধ্যমে এবং অর্ধেক টাকার বই গ্রন্থকেন্দ্র থেকে সরবরাহ করা হয়। গত বছর দেশের ১ হাজার ১০টি বেসরকারি পাঠাগারকে ক, খ, গ—৩টি শ্রেণিতে ভাগ করে অনুদান দেওয়া হয়। গত অর্থবছরে ক শ্রেণির একেকটি পাঠাগার বছরে ৫৬ হাজার টাকা, খ শ্রেণির পাঠাগার ৪০ হাজার টাকা এবং গ শ্রেণির পাঠাগার ৩৫ হাজার টাকা অনুদান পেয়েছে। মোট বাজেট ছিল ৪ কোটি ৫০ লাখ টাকা।
জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র সূত্রে জানা গেছে, ‘২০১৪ সালের ১৫ জানুয়ারি থেকে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র ৫৮৭টি পাঠাগারকে তালিকাভুক্ত করেছে। এই তালিকাভুক্তি সনদ কেবল সরকারি অনুদানপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে কাজে লাগে। এ ছাড়া পাঠাগারের গ্রন্থাগারিক একবার প্রশিক্ষণ করতে পারেন। অনুদান না পেলে বই উপহার পেতে পারেন।’
অন্যদিকে পাঠাগার উদ্যোক্তারা দীর্ঘদিন ধরেই অনুদান বাড়ানোর দাবি জানিয়ে আসছেন। তারা বলেন, পাঠাগারের ভাড়া, বিদ্যুৎ বিল, গ্রন্থাগারিকের বেতনসহ ঢাকায় একটি পাঠাগার পরিচালনার ব্যয় মাসে ১৫ থেকে ২০ হাজার টাকা। ঢাকার বাইরে জেলা বা উপজেলা সদরে তা ১০ হাজার টাকার কম নয়। কিন্তু জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র থেকে যে সহায়তা দেওয়া হয়, তা একটি পাঠাগারের ২ মাসের খরচও হয় না। বেসরকারি পাঠাগারগুলোর উদ্যোক্তারা অন্তত একজন গ্রন্থাগারিকের বেতনটা সরকারিভাবে দেওয়ার জন্য দাবি জানিয়ে আসছে। কিন্তু কোনো সাড়া পাচ্ছে না।
‘পাবলিক লাইব্রেরি’ এখন ‘ভাগাড়’ শিরোনামে খবরে বলা হয়, মৌলভীবাজারের ‘কুলাউড়া পাবলিক লাইব্রেরি’ নামটি একসময় সিলেট বিভাগসহ বিভিন্ন এলাকার বইপ্রেমীদের ‘বাতিঘর’ হিসেবে পরিচিত ছিল। বইপ্রেমী মানুষদের কাছে এটি ছিল ঐতিহ্যের স্মারক। কয়েক বছর ধরে গ্রন্থাগারটি পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে আছে। সংরক্ষণের অভাবে এটি এখন ময়লা-আবর্জনা ও জলাবদ্ধতায় পরিণত হয়েছে। স্বনামধন্য লেখকদের মূল্যবান বইয়ের সংগ্রহও ধ্বংস হয়ে গেছে।
গ্রন্থাগারের সাবেক গ্রন্থাগারিক খুরশীদ উল্লাহ বলেন, ‘২০১০ থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত সেখানে কর্মরত ছিলাম। আমার অনুপস্থিতিতে সহকারী গ্রন্থাগারিক শামসুদ্দিন দায়িত্ব পালন করতেন। তিনি ২০১৭ সালে মারা যান। গত ৫ বছর এটি সংরক্ষণে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।’ (দ্য ডেইলি স্টার, ২০ জুলাই ২০২২)
চাঁপাইনবাবগঞ্জের নাচোল উপজেলায় ঐতিহাসিক তেভাগা আন্দোলনের নেত্রী ইলা মিত্রের নামে নির্মিত পাঠাগার ও সংস্কৃতি কেন্দ্র আর্থিক সংকটে বন্ধ। (প্রথম আলো, ১৩ অক্টোবর ২০২১)| স্থায়ী গ্রন্থাগারিক না থাকায় এমন চিত্র দেশের প্রায় সব বেসরকারি পাঠাগারের।
গ.
শিক্ষার বাতিঘর বলা হয় গ্রন্থাগারকে। গ্রন্থাগার ছাড়া কোনো সমাজ বা রাষ্ট্র নাগরিককে পরিপূর্ণ শিক্ষার অধিকার নিশ্চিত করতে পারে না। পাঠাগারের সন্ধিবিচ্ছেদ করলে হয় ‘পাঠ+আগার’ অর্থাৎ পাঠাগার হলো পাঠ করার সামগ্রী সজ্জিত আগার বা স্থান। পুঁথিগত বিদ্যার ভারে ন্যুব্জ অধিকাংশ শিক্ষার্থীর মানসিক প্রশান্তির জন্য পাঠাগার অপরিহার্য। পাঠাগার কেবল ভালো শিক্ষার্থীই তৈরি করে না, ভালো মানুষও হতে শেখায়।
হাজার বছর ধরে মানুষের সব জ্ঞান জমা হয়ে রয়েছে বইয়ের ভেতরে। অন্তহীন জ্ঞানের উৎস বই, আর সেই বইয়ের আবাসস্থল পাঠাগার। যেকোনো সমাজের জন্য মনে রাখা জরুরি, বই পড়ার অভ্যাস গড়ে তোলা ছাড়া জাতীয় চেতনার জাগরণ হয় না। শিক্ষার আলো বঞ্চিত কোনো জাতি মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারেনি।
অন্যদিকে বাংলাদেশের শিক্ষার্থীদের মধ্যে পড়ার দক্ষতা ও পাঠাভ্যাস গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে রুম টু রিড ভিন্নভাবে কাজ করছে। এই বিষয় রুম টু রিড বাংলাদেশ-এর কান্ট্রি ডিরেক্টর রাখী সরকার বলেন, “বইয়ের কার্যক্রম নিয়ে আমরা একটা পরিকল্পনায় কাজ করি। তাই আমাদের উদ্যাগে শিক্ষার্থীদের ধীরে ধীরে পাঠ অভ্যাস গড়ে উঠছে। তা ছাড়া আমরা একেবারে শ্রেণিকক্ষে গিয়ে কথা বলি। প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের উপযোগী বই নিয়ে ‘বুক ক্যাপ্টেন’-এর মাধ্যমে কাজ করি। সেই সঙ্গে আগ্রহ ও ক্লাস বিবেচনায় আমরা নিজেরা বই প্রকাশ করি। ঢাকাসহ দেশের ৪টি জেলায় ২০০৯ সাল থেকে শিক্ষার্থীদের বইপাঠ নিয়ে কার্যক্রম চলছে।”
বাংলা একাডেমি এবং জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের সাবেক পরিচালক, গ্রন্থ ও গ্রন্থাগার বিশেষজ্ঞ ফজলে বলেন, ‘গণতন্ত্র, গণশিক্ষা ও গণগ্রন্থগার কোনোটিই তো আমার দেশে সফল ও সুপ্রতিষ্ঠিত নয়। গণতন্ত্র ও গণশিক্ষা উন্নয়নের ক্ষেত্রে আমরা কিছু করতে পারি না। আমাদের মতো সাধারণ মানুষ কিছু কাজ করতে পারি একমাত্র গণগ্রন্থগার উন্নয়ন নিয়ে। এ ক্ষেত্রেও যদি সরকার আন্তরিকতা না দেখায়, সহযোগিতা না করে, তাহলে আগামী অন্ধকার।”
এ বিষয়ে সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ বলেন, “দেশের বেসরকারি পাঠাগারগুলো সক্রিয় রাখার জন্য আপাতত একজন গ্রন্থাগারিকের বেতন দেওয়ার সুযোগ নেই। তবে আমরা অনুদান ছাড়াও কিছু এককালীন অনুদান দিয়ে থাকি, তা থেকে বেতন দিতে পারেন তারা। যদিও সেটা কাগজে লেখা থাকে না কিন্তু সেদিক বিবেচনা করেই অনুদানটা দেওয়া হয়ে থাকে। তবে অনুদানে আর্থিক পরিমাণ বাড়ানোর চিন্তা আছে আমাদের।” (দ্য ডেইলি স্টার/ ৩০ মে ২০২২)
সমাজে যেকোনো মানুষের শরীরের জন্য যেমন খাদ্যের দরকার, তেমনি মনের খাদ্যও তার প্রয়োজন। এই প্রয়োজন মেটাতে পারে বই- পাঠাগার। পাঠাগার মানুষের মনকে আনন্দ দেয়। জ্ঞান প্রসারে রুচিবাধ জাগ্রত করে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লেখেন, “লাইব্রেরির মধ্যে আমরা সহস্র পথের চৌমাথার উপরে দাঁড়াইয়া আছি। কোনো পথ অনন্ত সমুদ্রে গিয়াছে, কোনো পথ অনন্ত শিখরে উঠিয়াছে, কোনো পথ মানব হৃদয়ের অতল স্পর্শ করিয়াছে। যে যেদিকে ইচ্ছা ধাবমান হও কোথাও বাধা পাইবে না। মানুষ আপনার পরিত্রাণকে এতটুকু জায়গার মধ্যে বাঁধাইয়া রাখিয়াছে।”
বই হাতে, মোবাইলে যেভাবে পড়ুক, অন্তত পড়ুক। কিংবা অডিও শুনুক তবু জানুক আগামীকে। কারণ, হতাশা কাটাতে ও দীর্ঘস্থায়ী উন্নয়নের জন্য দরকার পড়ুয়া সমাজ। প্রকৃত জ্ঞানার্জন ও প্রাণশক্তির বৃদ্ধির জন্য দেশের সবখানে পাঠাগার প্রতিষ্ঠা কিংবা অনলাইনে পাঠাগার পরিচালনার জন্য সবার আন্তরিকতা অত্যন্ত জরুরি।
এখনি প্রয়োজন এই ভূখণ্ডের শত বছরের ইতিহাস ঐতিহ্য নতুন প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেওয়া। সেই সঙ্গে যথাযথভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ। না হলে প্রজন্মের একটি অংশ মেরুকৃত হয়ে বিভিন্ন উগ্রবাদী কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে যাচ্ছে, যা আমাদের জন্য উদ্বিগ্নের। আর সুস্থ সংস্কৃতিচর্চা না থাকায় আজকাল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরাও হত্যাকাণ্ডের মতো অপরাধের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ছেন।
অথচ দুনিয়ার কোনো ধর্ম হত্যার কথা বলে না, কাউকে আঘাতের কথা বলে না। একজন নবীর আদর্শ মাথায় থাকলে কাউকে হত্যা করা সম্ভব না। তাহলে আজ যারা ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাতের নামে ভাঙচুর করে তারা কারা? কান্না আসে আমার। বলতে ইচ্ছা করে মা তোর বদনখানি মলিন হলে, আমি নয়ন জলে ভাসি।
পাঠাগারের সংকট দূর করতে ৫টি প্রস্তাব
১. কেবল বই পড়ার কাজ না করে পাঠাগারগুলোকে সাংস্কৃতিক ক্লাবে রূপান্তর করা। যেমন আবৃত্তি, বিতর্ক, রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা। পাশাপাশি গানের আড্ডা করা এবং সেগুলো পাঠাগারের ফেসবুক ইউটিউবে প্রচার করে অন্যদের উৎসাহিত করা। এইভাবে পাঠাগার নতুনভাবে জেগে উঠবে।
২. পাঠকের চাহিদামতো বই সংগ্রহ করা। যে এলাকায় যে মানের পাঠক/ শিক্ষার্থী আছে সে মানের বই রাখা। এলাকাভিত্তিক ইতিহাস ও স্মরণীয় ব্যক্তিদের গুরুত্ব দিয়ে তাদের জীবন ও কর্ম ছড়িয়ে দেওয়া।
৩. অনেক পাঠাগার এখনো হয়নি আধুনিকায়ন। বইয়ের সূত্র ধরে ইন্টারনেট থেকে নতুন কিছু জানার সাহায্য করা। এই বিষয় নজর দেওয়া উচিত। বিখ্যাত বই থেকে সিনেমা নাটক হয়েছে, সেগুলো দেখানোর ব্যবস্থা করা পাঠাগারে।
৪. লেখক আড্ডা ছাড়াও এলাকার কৃতী শিক্ষক, ভাষা আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধের বীর সেনানীদের জীবনের গল্প শোনার আয়োজন করা। এমন আড্ডা আলাপে জ্ঞান বিনিময় হয়, ছড়িয়ে পড়ে আলো। নতুনরা চিনে চিরায়ত মানুষকে।
৫. সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে পাঠাগার নিয়মিত খোলা রাখা। গ্রন্থাগারিক না থাকলে কোনো কাজই ঠিকমত হবে না। তার জন্য দরকার একজন স্থায়ী গ্রন্থাগারিক, যিনি নিজেও বই পড়েন। বেসরকারি বেশির ভাগ পাঠাগারে নেই গ্রন্থাগারিক। ফলে অধিকাংশ পাঠাগারও থাকে বন্ধ। তাই অনুদান দিয়ে হলেও গ্রন্থাগারিক রাখা অত্যাবশক।
লেখক : কবি ও গবেষক, সভাপতি, বিলকিছ আলম পাঠাগার