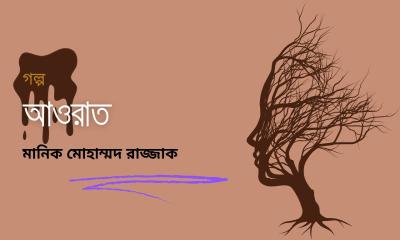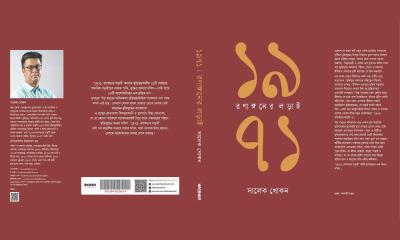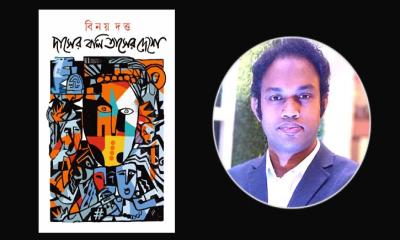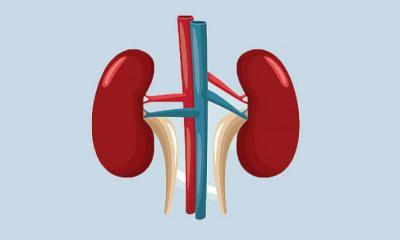ফ্রান্সের লিওঁ শহরে ভিনাতিয়েখ এলাকায় একটি মানসিক হাসপাতাল রয়েছে। রাজা লুই ফিলিপের আমলে তৈরি হয়েছিল এই হাসপাতাল। ১৯৬৭ সালের অক্টোবরে, কোনো এক সন্ধ্যায়, সেখানে বক্তৃতা করতে যান ফরাসি মনোবিশ্লেষক জাক লাকাঁ। ব্ক্তৃতাটি ‘দ্য প্লেস, অরিজিন অ্যান্ড এন্ড অব মাই টিচিং’ শিরোনামে প্রকাশ পায় পরবর্তীকালে। সেখানে লাকাঁ অচেতন বা অজ্ঞান নিয়ে বলছেন: লোকে ভাবে অচেতন ব্যাখ্যার অতীত নয়, বা একে খণ্ডন করা যায়। কিন্তু পরক্ষণেই লোকে এও আবিষ্কার করে অচেতন অকাট্য, একে কোনো কিছু দিয়েই কেটে ভেতরে কী আছে, তা বোঝা যায় না। এটাই অচেতনের বৈশিষ্ট্য। অজ্ঞানকে না বোঝার দায় অজ্ঞানের নয়, আমাদের জ্ঞানের। তবে লাকাঁর মতে, ভাষাকে চিনলে অচেতনকে চিনতে সুবিধা হয়, কারণ ওই দুটির গঠন একই রকম। সলিমুল্লাহ খান আমাদের কখনো অচেতন চেনান ভাষা দিয়ে, কখনো বা ভাষা বোঝান অচেতন দিয়ে। আমার ধারণা, এই ব্রত পালন করতে গিয়ে স্যারও যেন লোকজনের কাছে নিজেই অচেতনে পরিণত হয়ে গেছেন। মানুষ বলে সলিমুল্লাহ খান কথা বললে বোঝা যায়, কিন্তু লিখলে নাকি তা আর বোঝা যায় না। এটি অচেতনের বৈশিষ্ট্যই বটে!
সলিমুল্লাহ খান যেভাবে কথা বলেন, বা সত্য বলেন, তাতে অনেকেরই অহম আহত হয়। মনের সেই ক্ষত কোনো না কোনোভাবে তাদের অচেতনে জায়গা করে নেয় এবং সেই ক্ষত থেকে জন্ম নেয় ব্যক্তিগত ক্ষোভ। সেসবেরই বহিঃপ্রকাশ আমরা দেখি কদিন পরপর, আগ্নেয়গিরির মতো ফেটে বেরোচ্ছে। স্যারের নামে যা-তা বেফাঁস কথা বলা থেকেই বোঝা যায় তাদের অজ্ঞানে যে ভীমরুলের চাক রয়েছে, সেখানে সলিমুল্লাহ খান ঢিল ছুড়েছেন। অথচ তারা বোঝেন না, কঠিন সত্য স্যার ঘুরিয়ে, ভালো কথার মোড়কে, পিঠ চুলকে দেওয়ার মতো করে বলতে চান না, তিনি তাঁর মতো করেই সরাসরি সমালোচনা করেন, ব্যক্তির নয়, কর্মের।
জ্ঞানচর্চাকারী বা জ্ঞানচর্চার ভান করতে থাকা সবার কাজেরই কড়া ভাষায় সমালোচনা করে থাকেন সলিমুল্লাহ খান। তিনি নিয়মিতই সেটা করেন এবং তখনই শুরু হয়ে যায় দল বেঁধে অশিষ্ট শব্দ ছুড়ে দেওয়ার প্রতিযোগিতা। যারা সলিমুল্লাহ খানকে লক্ষ্য করে ব্যক্তি আক্রমণ করেন, তারা বেমালুম হয়ে যান সলিমুল্লাহ খান কখনো ব্যক্তি মানুষকে আক্রমণ করেন না, তাঁর লক্ষ্য থাকে কাজের গুণাগুণ। এই বলাকে কেন্দ্র করে একদল মানুষ যেমন অসহিষ্ণুতা ও অসূয়ার প্রদর্শনীকে ‘সাইবার বুলিং’য়ের পর্যায়ে নিয়ে যান, তেমনি অন্য আরেক দল সলিমুল্লাহ খান কিছু না বললেও, কদিন পরপর নিয়ম করে সলিমুল্লাহ খানকে অযথা চাঁদমারিতে পরিণত করেন, সম্ভবত এটা তারা করেন সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে নিজেদের পোস্টের কাটতির জন্য। তবে এর পেছনের প্রকৃত কারণ আসলে ওটাই: সত্য বললে অহম বেজার। কেউ যদি সলিমুল্লাহ খানের কোনো বই বা প্রবন্ধকে ধরে বৌদ্ধিক (ডিসকার্সিভ) বাহাসের সূচনা করতেন, তাহলে বোঝা যেত তারা মূঢ় নন, কিন্তু সে পথের অনেক দূর দিয়েই তাদের চলাচল। যেকোনো ছুতো নিয়ে স্যারকে অপদস্থ করাতেই যেন তাদের আনন্দ।
ধরা যাক একটি চিঠির কথা, দুজন মানুষের ব্যক্তিগত চিঠি সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে ছড়িয়ে দিয়ে যেভাবে স্যারকে ‘অপমান’ করার চেষ্টা হলো, তা বিস্ময়কর। চিঠিটি আহমদ ছফা লিখেছিলেন সলিমুল্লাহ খানকে। আহমদ ছফা পত্রটি দিয়েছিলেন লেখক মোরশেদ শফিউল হাসানকে, সলিমুল্লাহ খানকে দেওয়ার জন্য। এটি ১৯৭৯ সালের ঘটনা। অথচ সেই চিঠি শফিউল হাসান প্রাপকের হাতে না দিয়ে নিজের কাছে রেখে দেন এবং চার দশক পর প্রাপককে ‘শিক্ষা’ দেওয়ার নিমিত্তে ফেসবুকে রাষ্ট্র করেন। তিনি ভেবেছিলেন আহমদ ছফা যেহেতু ওই চিঠিতে স্যারকে ভর্ৎসনা করেছেন, তাই এটি ছড়িয়ে দিলে স্যার অস্বস্তিতে পড়বেন। কিন্তু গুরুস্থানীয় মানুষের ভর্ৎসনা যে আশীর্বাদ সমান, অতটুকু বুঝ প্রতিশোধপরায়ণ অহমেরা না বুঝলেও সলিমুল্লাহ খান বোঝেন। তাই তিনি মোরশেদ শফিউল হাসানের চিঠির বিষয় গোপন বা গুম করে ফেলা এবং সুযোগ বুঝে সেটি প্রকাশ করা নিয়ে কোনো প্রতিক্রিয়া জানাননি।
ঘটনা হলো, ১৯৭৮ সালে ছালেহ আহমদ ছালু সম্পাদিত সাপ্তাহিক ‘জাগো প্রহরী’ পত্রিকার ৭ম বর্ষ ৭ম সংখ্যায় আহমদ ছফার ‘বিশ্ববিদ্যালয়ে গুপ্তচরবৃত্তি’ শিরোনামের একটি প্রবন্ধ ছাপা হয়। সেই রচনাটি সামান্য সম্পাদনা করে নিজের ‘প্রাক্সিস জর্নাল’ পত্রিকার ২য় সংখ্যায় (এপ্রিল-জুন ১৯৭৯) ছাপান সলিমুল্লাহ খান। রচনাটি পুনঃপ্রকাশের ব্যাপারে মানা করেছিলেন আহমদ ছফা। কিন্তু রচনার গুণ ও লেখকের প্রতি ভালোবাসা থেকেই স্যার লেখাটি ছেপে দেন। তাতে রেগে গিয়ে আহমদ ছফা চিঠি লেখেন এবং সেখানে মন্তব্য করেন, স্যার যা করেছেন তা 'পীত সাংবাদিকতা'। সবাই জানেন আহমদ ছফা আবেগী মানুষ ছিলেন, হুট করে রেগে যেতেন, আবার হুট করেই তাঁর মন গলে যেত। স্যার যখন পরে আহমদ ছফার সঙ্গে দেখা করেন তখন বিষয়টি মিটে যায়।
আহমদ ছফা নিশ্চয় জানতেন একটি লেখা পুনর্মুদ্রণ করা কোনোভাবেই পীত বা হলুদ সাংবাদিকতা নয়, কারণ অর্থপ্রাপ্তির লোভে অবৈধ বা অনৈতিক উপায়ে কোনো কিছু করেনি প্রাক্সিস জর্নাল। বরং ‘জাগো প্রহরী’র সম্পাদকের অনুমোদন নিয়েই স্যার লেখাটি নিজের পত্রিকায় ছেপেছিলেন। এটি পত্রিকার জগতে খুবই প্রচলিত একটি চর্চা। তারপরও স্যার এ ঘটনার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন, আহমদ ছফা স্যারকে পছন্দ করতেন, তাই তিনিও বিষয়টি ভুলে যান। কিন্তু দেখা গেল চল্লিশ বছর পর এই চিঠিকে বানানো হলো আক্রমণের হাতিয়ার! মজার ব্যাপার হলো চিঠিটি আজ অব্দি স্যারের হাতে দেননি মোরশেদ শফিউল হাসান, উল্টো তিনি ফেসবুকে চিঠির ছবি দিয়ে সবাইকে দেখাচ্ছেন আহমদ ছফা কেমন করে সলিমুল্লাহ খানকে ‘বকাঝকা’ করেছেন। স্যারকে আহমদ ছফা স্নেহ করতেন বলেই ও রকম চিঠি লিখেছিলেন। স্নেহ করার প্রধান কারণ স্যারের প্রতিভা। নিজের বুদ্ধিবৃত্তিক সক্ষমতার স্বাক্ষর তিনি রেখেছেন ছাত্রাবস্থা থেকেই।
সলিমুল্লাহ খান সে সময় অনার্সের ফাইনাল পরীক্ষা দিচ্ছেন; পরীক্ষার ফাঁকে ফাঁকে তিনি জাতীয় অধ্যাপক আবদুর রাজ্জাকের বক্তৃতার সমালোচনা লিখেছিলেন, যা তখন বেশ সাড়া জাগিয়েছিল। ‘বাংলাদেশ: জাতীয় অবস্থার চালচিত্র’ বইতে সেই সমালোচনা প্রবন্ধটি রয়েছে। প্রবন্ধে স্যার বলেছিলেন, অধ্যাপক রাজ্জাকের চিন্তা সামাজিক শ্রেণির দ্বারা নির্ণীত। এই বই পড়ে তখন বহু লোক ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন, এখনকার মতোই। তবে যার চিন্তার সমালোচনা করেছিলেন স্যার, সেই মানুষটি কিন্তু এখনকার মানুষদের মতো ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেননি। আহমদ ছফা ‘যদ্যপি আমার গুরু’ বইতে সেসবের বয়ান দিয়েছেন। আহমদ ছফা লিখছেন, “…আমি স্যারের (অধ্যাপক আবদুর রাজ্জাক) কাছ থেকে জানতে চেয়েছিলাম, সলিমুল্লাহর বইটি তিনি পড়েছেন কি না। স্যার বললেন, হ পড়ছি। তাতে কী অইছে। ছেলেটার ত ট্যালেন্ট আছে। কী লিখছে না লিখছে হেইডা মনে কইর্যা কী লাভ। হের ত কিছু করার ক্ষমতা আছে।” প্রবন্ধে সারবত্তা ছিল বলেই স্যারের ‘ক্ষমতা’র কথা উল্লেখ করেছিলেন অধ্যাপক রাজ্জাক, আর স্নেহ করেন বলেই সেটা পাঠককে জানিয়েছিলেন আহমদ ছফা।
পরবর্তীকালে বিনয়ের সঙ্গেই অধ্যাপক রাজ্জাককে স্মরণ ও শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন সলিমুল্লাহ খান। তাঁর সত্যবচন ও সমালোচনাকে অনেকে দুর্বিনীত আচরণ বলে মনে করতে পারেন। তাতে ক্ষতি বৃদ্ধি হচ্ছে না। তবে আমি মনে করি আমাদের মতো গড্ডলে ঠাসা সমাজে স্যারের মতো ‘দুর্বিনীত’ সমালোচকের প্রয়োজন আছে। ওনার কথার চাবুকের চোটে যদি বাংলাদেশের সাহিত্যের দুনিয়ায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় তাতে বরং লাভই হওয়ার কথা। এমন কথা কবি সাখাওয়াত টিপুও বলেছেন এক ফেসবুক পোস্টে। সলিমুল্লাহ খানের গুণমুগ্ধ বলে তাঁকেও নিন্দামন্দের ভাগিদার হতে হয়, আমার মতোই। আমার একটা বিষয় খুব বিস্ময়কর লাগে: ধরুন বিখ্যাত সেতারবাদক রবিশঙ্কর, তাঁকে বহু জায়গায় দেখেছি আদবের সাথে উস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁয়ের নাম স্মরণ করে সংগীত পরিবেশন শুরু করেছেন। রবিশঙ্কর ‘বাবা’ বলে সম্বোধন করতেন আলাউদ্দিন খাঁকে। এতে কি তিনি ছোট হয়ে গেলেন? নিজের শিক্ষক বা গুরুর নাম নিলে, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলে, লোকে দেখি এ দেশে ঠাট্টা করে, ছোট করার জন্য উঠেপড়ে লাগে। ভাবখানা এমন তারা সকল শিক্ষাগ্রহণ করেছেন অলৌকিক হাওয়া থেকে।
সলিমুল্লাহ খান আমাদের সময়ের জাক লাকাঁ। লাকাঁ যেমন প্রতি সপ্তায় সেমিনার করে বক্তৃতা দিতেন নানা বিষয়ে, বছরের পর বছর। স্যারও তেমনি গত কুড়ি বছরের বেশি সময় ধরে বিষয়ভিত্তিক সেমিনারে বক্তৃতা দিয়ে গেছেন। নিয়ে গেছেন বিষয়ের গভীরে। সেখানে কত শত মানুষকে যে দেখেছি। আজ যারা কবিতাচর্চা বা বুদ্ধিচর্চা করেন, তাদের অনেকের কাজেই স্যারের সেসব সেমিনারের প্রভাব লক্ষণীয়, কিন্তু তারা মুখে সেটা স্বীকার করেন না, উল্টো কটূকথা ছড়িয়ে ‘উচিত গুরুদক্ষিণা’ দেওয়ার চেষ্টা করেন।
সলিমুল্লাহ খান বক্তৃতা, টেলিভিশন টক শো ও বিভিন্ন লেখায় সব সময়ই গুরুত্বপূর্ণ লেখক ও চিন্তাবিদদের ভুলত্রুটি নিয়ে কথা বলেন। তাঁর সত্য বলার ধরনের কারণে লোকে চাইলেও তাঁকে এড়িয়ে যেতে পারে না, আবার দীর্ঘদিন ধরে গুরুত্বপূর্ণ লেখক ও চিন্তাবিদদের সম্পর্কে একপ্রকার ধারণা পোষণের কারণে স্যারের কথা মেনেও নিতে পারে না। অনেকে আবার স্যারের মতো করে চিন্তা করতে না পারার যন্ত্রণাতেও ভোগেন। সব মিলিয়ে স্যারের বিরুদ্ধে বিষোদগার শুরু হয়ে যায়। এতে বোঝা যায় এসব মানুষ তিতা সত্যকে বরণ করার চেয়ে পুরোনো বিশ্বাসকেই আঁকড়ে ধরে রাখতে ও আমুদে আক্রমণ করতেই বেশি আগ্রহী। সলিমুল্লাহ খানের কথা ও লেখায় যে মনীষার দেখা পাওয়া যায়, তা দুই বাংলাতেই বিরল। সলিমুল্লাহ খানের মনীষার কান্তি, কাঁটাবিহীন নয়। এটাই তাঁর বৈশিষ্ট্য। স্যারের এই বৈশিষ্ট্যের কারণেই একদল মানুষ আকৃষ্ট হয়, আরেক দল মানুষ শত্রুতে পরিণত হয়।
সলিমুল্লাহ খান আমাদের চমকে দেন, সত্য দিয়ে, তাঁর ভাষ্য দিয়ে। ভাষার প্রতি তাঁর দখল চমকে দেওয়ার মতোই। বাংলা, ইংরেজি, ফরাসি, আরবি, জর্মনসহ আরও বহু ভাষার সঙ্গে পরিচয়ের সুবাদেই তিনি চিন্তার ক্ষেত্রে এতটা সমৃদ্ধ। স্যার মূলত ভাষারই শিক্ষক, অন্তত আমার কাছে। লাকাঁ যেমন বলেন, ভাষা বৈ তিনি আর কিছুরই শিক্ষা দেননি সারা জীবন, স্যারও স্রেফ ভাষাটাই শিখিয়েছেন, শিখিয়ে যাচ্ছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজও এটাই, ভাষা শিক্ষা দেওয়া। লাকাঁর কাছে বিশ্ববিদ্যালয় হলো ভাষা বলয়ের (ডিসকোর্স) বিশ্ব বা মহাবিশ্ব (ইউনিভার্স)। বিশ্ববিদ্যালয়ে নানা বিষয়ের শিক্ষা, নানা ধরনের ডিসকোর্স ব্যবহার করেই দেওয়া হয়।
সলিমুল্লাহ খান শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে প্রকৃত অর্থেই বিশ্ববিদ্যালয়ের বৈশিষ্ট্যকে ধারণ করেন। স্যার এই নগরীতে গত বিশ বছর ধরে মনোবিশ্লেষণ, রাজনীতি, মার্কসবাদ, অর্থনীতি, ইতিহাস, দর্শন, সাহিত্য, চলচ্চিত্র এমন কোনো বিষয় নেই, যা নিয়ে সেমিনার করেননি। এসবের মাধ্যমে তিনি বিচিত্র ডিসকোর্স বা ভাষা বলয়ের সঙ্গেই পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন আমাদের। এ জন্যই সলিমুল্লাহ খান আমার ‘আলমা ম্যাটার’। তাঁর কাছ থেকে যে সামান্য জ্ঞান আমি অর্জন করেছি, তা একজন শিক্ষার্থী বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই অর্জন করেন। লাকাঁ মনে করতেন, শিক্ষাদানের গোড়ায় রয়েছে ‘ইউনিভারসিতাস লিত্তেরারুম’ (Universitas Litterarum) অর্থাৎ পত্র বিশ্ববিদ্যালয়, যেখানে সামগ্রিক রূপে মানবিকবিদ্যার পাঠদান করা হয়। বাংলায় পত্রের অর্থ চিঠি বা লিখিত কাগজ যেমন হয়, তেমনি বৃক্ষ বা গ্রন্থের পাতাও হয়। সলিমুল্লাহ খানের প্রাপ্য হাজার চিঠি গুম করে ফেলা যায়, তাঁকে আক্রমণ করা যায়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনিই আমাদের এই রোঁয়া ওঠা নগরে পত্রপল্লবে ছাওয়া বিদগ্ধ ‘ইউনিভারসিতাস লিত্তেরারুম’।


-20210817145406.jpg)