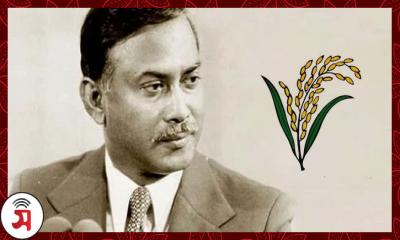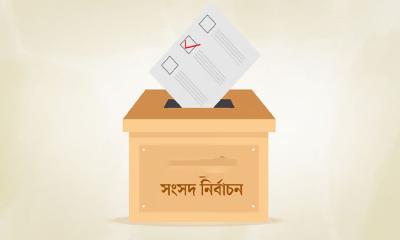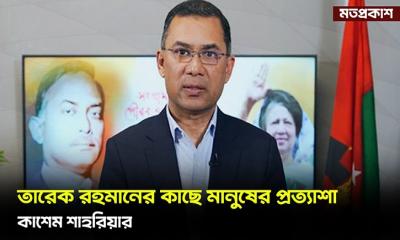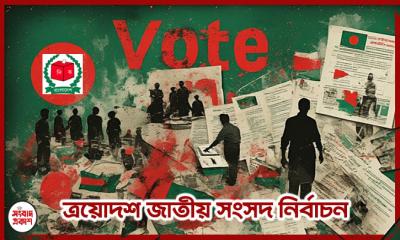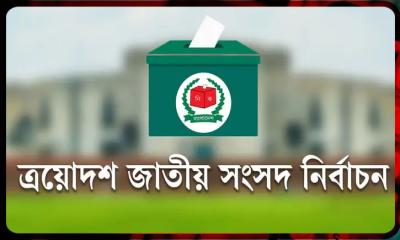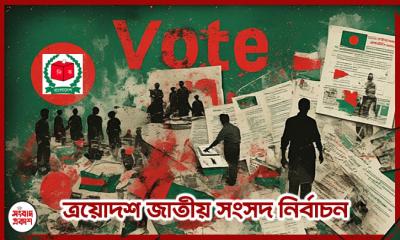বিশ্বব্যাংকের হিসাবে ২০১৭ সালে শ্রীলঙ্কার মাথাপিছু জিডিপি ছিল ৪,০৭৬ ডলার। ৫ বছর ধরে মন্দা, মহামারি ও অস্থিরতায় তা কমলেও এখনো ৩,৬৮২ ডলার। বাংলাদেশের মাথাপিছু জিডিপি ২,০০০ ডলারের কাছাকাছি। ভারতেরও তাই। পাকিস্তান ও নেপালের ১,২০০ ডলারের কম। ভুটান ৩,১২২ এবং মালদ্বীপের মাথাপিছু জিডিপি ৭,৪৫৫ ডলার। তার মানে দক্ষিণ এশিয়ায় মাথাপিছু জিডিপি বিচারে শ্রীলঙ্কার অবস্থান এখনো দ্বিতীয়।
তাহলে বোঝা গেল মাথাপিছু জিডিপি অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার বা অর্থনীতি বিচারের একমাত্র মাপকাঠি না। জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার যদি ধরি!
আইএমএফের পরিসংখ্যান গণনায় ধরলে গত ৯-১০ বছরের গড় প্রবৃদ্ধি বিবেচনায় নিলে লিবিয়া ও গায়ানার প্রবৃদ্ধি সবচেয়ে বেশি, দুই অঙ্কের ওপর। চীন ও বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি প্রায় সমান সমান, সাড়ে ছয়ের মতো। ভারতের ৫.৫, মালদ্বীপ ৫.১, নেপাল ৪.৬, পাকিস্তান ৩.৮, ভুটান ৩.৩, এবং শ্রীলঙ্কা ৩। দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে শ্রীলঙ্কার প্রবৃদ্ধি সবচেয়ে কম। কিন্তু তা শতকরা তিন ভাগ। বিশ্ববিচারে বেশ ভালো বলতে হবে। বিশ্বে অন্তত ১১৬টি দেশ প্রবৃদ্ধির বিচারে শ্রীলঙ্কার নিচে আছে। সেখানে কাতার, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, সৌদি আরব, জ্যাপান, জার্মানি, নরওয়ের মতো সম্পদশালী ও উন্নত দেশগুলো আছে। আবার একেবারে ঋণাত্মক প্রবৃদ্ধি হচ্ছে, তা-ও ১০ বছর ধরে, এমন দেশের সংখ্যা ২২, যেখানে ব্রুনেই, কুয়েত, ইতালির মতো ধনী দেশও আছে। তার মানে প্রবৃদ্ধির হার দিয়েও অর্থনৈতিক অবস্থা যাচাই করা যায় না।
সাধারণভাবে সবাই বলছেন শ্রীলঙ্কার বৈদেশিক ঋণই এর জন্য কাল হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফি বছর চার বিলিয়ন ডলারের ওপর ঋণের কিস্তি শোধ করতে হয়। শ্রীলঙ্কা বৈদেশিক ঋণ এখন জিডিপির ১০১ ভাগ। ভয়ংকর পরিসংখ্যান। কিন্তু শ্রীলঙ্কার এমন অবস্থা একবিংশ শতকের শুরুর দিকেও ছিল। সে সময় ক্রমাগত পাঁচ বছর ধরে তা ১০০-এর ওপর ছিল। ২০০২ সালে তা প্রায় ১০৯ ভাগ ছিল। কোথায়, তখন তো কোনো সংকট হয়নি! সুতরাং বৈদেশিক ঋণ বেশি থাকাটাও বড় কোনো ইস্যু না।
অন্য দেশগুলোর দিকে তাকানো যাক। জাপানের বৈদেশিক ঋণ জিডিপির ২৫৯ ভাগ। শ্রীলঙ্কার ১৫২ ভাগ। যে মালদ্বীপের মাথাপিছু জিডিপি দক্ষিণ এশিয়ায় সবচেয়ে বেশি, সেই মালদ্বীপের বৈদেশিক ঋণ জিডিপির ১৪৬ ভাগ। যে ভুটানের মাথাপিছু আয় শ্রীলঙ্কার কাছাকাছি তার বৈদেশিক ঋণ ১৩১ ভাগ। যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেত্রে তা ১৩৪, ফ্রান্সের ১১৫, যুক্তরাজ্যের ১০২, ভারতের ৯০, চীন ও জার্মানির ৬৮, বাংলাদেশের মাত্র ৩৯। আর সবচেয়ে কম বৈদেশিক ঋণ যাদের, সেই দেশগুলোর অধিকাংশ হয় আফ্রিকার অনুন্নত দেশ বা প্রশান্ত মহাসাগরের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপরাষ্ট্র।
আসলে যে দেশের ভাবমূর্তি ভালো, যে দেশের ওপর অন্যরা ভরসা করতে পারে, যে দেশের অর্থনৈতিক সক্ষমতা আছে বলে অন্যরা মনে করে, তারাই বেশি বৈদেশিক ঋণ পায়। ঋণ পাওয়া, ঋণ নেওয়া এবং সময়মতো সেই ঋণ ফেরত দেওয়া একটা দেশের অর্থনৈতিক সক্ষমতার নজির। আন্তর্জাতিক রীতিনীতির প্রতি শ্রদ্ধাশীলতার নজির। দেশের ভাবমূর্তি ও বিশ্বাসযোগ্যতা উন্নত করার একটা গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। শ্রীলঙ্কার ওপর সেই বিশ্বাসটা বরাবর ছিল। বিশ বছর ধরে খুবই উঁচু মাত্রার বৈদেশিক ঋণ থাকলেও শ্রীলঙ্কা কখনো ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হয়নি। ব্যর্থ হলো এই প্রথমবার।
তাহলে ঘটনাটা কী!
বৈদেশিক ঋণ প্রধানত শোধ করতে হয় মার্কিন ডলারে। কোনো কোনো দেশ ভিন্ন মুদ্রায় লেনদেন করে থাকে। সে ক্ষেত্রে সেই নির্দিষ্ট মুদ্রায় তা পরিশোধ করতে হয়। সুতরাং ঋণ পরিশোধ করতে গেলে কেন্দ্রীয় ব্যাংকে হয় সেই নির্দিষ্ট মুদ্রা, নয় মার্কিন ডলারের মজুত থাকতে হবে। নতুবা নির্দিষ্ট বিনিময় হারে নিজস্ব মুদ্রা দিয়ে মার্কিন ডলার কিনতে হবে এবং তারপর সেই ঋণ শোধ করতে হবে।
নিজ নিজ দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সূত্র সমন্বয় করে জানা যায়, চীনের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ সবচেয়ে ভালো। ৩,২৪৬ বিলিয়ন ডলার। জাপানের ১,৩১১ বিলিয়ন, সুইজারল্যান্ডের ১,০৩৩ বিলিয়ন ডলার। ভারতের ৫৮০ বিলিয়ন, যুক্তরাষ্ট্রের ২৪২ বিলিয়ন, বাংলাদেশের ৩৮.৭৮ বিলিয়ন, পাকিস্তানের ৯.৭১ বিলিয়ন, নেপালের ১০.৪৭ বিলিয়ন, ভূটানের ১.২৪, মালদ্বীপের ০.৭৬ এবং শ্রীলঙ্কার ক্ষেত্রে তা শূন্যের কোঠায়। কিরিবাতি, সোমালিয়া, বুরকিনা ফাসো বা বেনিনের ক্ষেত্রেও তা নিতান্ত কম। কিন্তু এই দেশগুলোর বৈদেশিক ঋণও তেমন নেই।
ঋণ পরিশোধ ছাড়া আমদানির জন্যও বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন হয়। শ্রীলঙ্কা প্রধানত আমদানি করে জ্বালানি, সার, রাসায়নিক দ্রব্য, ভোগ্যপণ্য, নির্মাণসামগ্রী, কাপড়চোপড়, যন্ত্রপাতি, যানবাহন সামগ্রী, খাদ্যদ্রব্য। তবে কৃষি উৎপাদন কমে যাওয়ায় খাদ্যদ্রব্য আমদানি বেড়ে গেছে। শ্রীলঙ্কা প্রায় অর্ধেক পণ্য আমদানি করে চীন ও ভারত থেকে। এরপর আরব আমিরাত, সিঙ্গাপুর, জ্যাপান, মালয়েশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্র থেকে।
অপর দিকে শ্রীলঙ্কা রপ্তানি করে তৈরি পোশাক, চা, দারুচিনি, রাবারের টায়ার, শুকনা ফল, মাছ, হীরা ও রত্ন, ছোট কারখানাজাত পণ্য। অধিকাংশ পণ্য যায় যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, জার্মানি, ভারত, ইতালি, নেদারল্যান্ডস, বেলজিয়াম, চীন, আমিরাত, জাপান, রাশিয়া, বাংলাদেশ ও তুরস্কে। গড়ে বছরে রপ্তানি আয় ২০ বিলিয়ন ডলারের কম। মহামারির কারণে তা আরও ৪-৫ বিলিয়ন কমেছে। কিন্তু আমদানি ২২ বিলিয়ন ডলার। আগে আরও বেশি ছিল। বৈদেশিক মুদ্রার ওপর চাপ কমাতে এক বছর ধরে সরকার কিছু কিছু ভোগ্যপণ্য, কয়েক ধরণের কাপড় ও সার আমদানি গত বছর থেকে নিষিদ্ধ করে আমদানি ব্যয় কিছুটা হলেও কমিয়ে এনেছে।
আমদানি ব্যয় ও রপ্তানি আয়ের মধ্যে ফারাক ৬-৯ বিলিয়ন ডলার। পর্যটন খাতে ২০১৭ বা ২০১৮ সালে যেখানে ৫ বিলিয়ন ডলারের বেশি আয় ছিল, সেখানে ২০২০ সালে তা এক বিলিয়ন ডলারে নেমে এসেছে। দেশে অস্থিতিশীলতা চলতে থাকলে পর্যটক আরও কমে যাবে। ফলে পর্যটন আয়ও কমবে।
প্রবাসীদের পাঠানো রেমিট্যান্স ছিল শ্রীলঙ্কার অন্যতম প্রধান বৈদেশিক মুদ্রার উৎস। গত দশ বছর ধরে তা সাত বিলিয়ন ডলারের ওপরে ছিল। অস্থিতিশীলতার কারণে সেই রেমিট্যান্স প্রবাহে ভাটা পড়েছে। ২০২১ সালে রেমিট্যান্স এসেছে ৫.৫ বিলিয়ন।
যারা অঙ্কে পটু, তাদের কাছে এমন একটা সমীকরণ মেলানো হয়তো খুব কঠিন না। কিন্তু রাজনীতি, বিশেষ করে আন্তর্জাতিক রাজনীতি বা কূটনীতি আরও কিছুটা জটিল। রাজনীতি ও কূটনীতি অঙ্কের মতো না। এখানে অনেক সময় শূন্যের সঙ্গে শূন্য যোগ করেও কিছু ফল পাওয়া যায়। আবার অনেক ক্ষেত্রে সব ঠিক থাকলেও কিছুই ঠিক হয় না। যার বেতন শ্রীলঙ্কায় ৫০ হাজার রুপি, তাঁকে হয়তো জ্বালানির জন্যই এখন ৩০ হাজার রুপি ব্যয় করতে হচ্ছে।
আন্তর্জাতিক বাজারে ডলারের মুদ্রামান উত্থান-পতনেও শ্রীলঙ্কার মতো দেশ প্রভাবিত হয়। মহামারির ঠিক শুরুতে ডলারের মুদ্রামান ৯৬ থাকলেও বর্তমানে তা ১০৬। ডলারের বিপরীতে শ্রীলঙ্কান রুপির বিনিময় হার খুবই ভয়াবহ। মহামারির আগে এক ডলার কিনতে ১৭৫ শ্রীলঙ্কান রুপি লাগত। এখন তার দ্বিগুণ লাগে, ৩৬০ রুপি।
আমাদের অনেকে শ্রীলঙ্কার সংকটের জন্য চীনকে খলনায়ক বলছে। পশ্চিমা সংবাদমাধ্যম অনুসরণ করলে এমন ধারণা তৈরি হতে বাধ্য। শ্রীলঙ্কার যে বৈদেশিক ঋণ তার ১০ ভাগ চীনা ঋণ। এমন ১০ ভাগ ঋণ জাপান থেকেও নিয়েছে। বিশ্বব্যাংক থেকেও নিয়েছে। এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক থেকে এর চেয়ে বেশি ১৩ ভাগ ঋণ নিয়েছে। ৪৭ ভাগ ঋণ বাজার থেকে নেওয়া। ভারতের কাছে ঋণ শতকরা দুই ভাগ। কোথায়, কেউ তো জাপান, বিশ্বব্যাংক বা এশীয় উন্নয়ন ব্যাংককে খলনায়ক হিসেবে চিহ্ণিত করছে না! চীনকে খলনায়ক বলার একটা প্রধান কারণ হলো, হাম্বানটোটা সমুদ্রবন্দর লিজ নিয়ে নেওয়া।
হাম্বানটোটার প্রতি চীনের একটা আগ্রহ কৌশলগত কারণে ছিল। আরও পরিষ্কার করে বললে বলতে হয় সামরিক কৌশলগত স্বার্থ। চীন সে জন্য তা উন্নয়নে সচেষ্ট হয়। এখন তা অর্থনৈতিকভাবে পারঙ্গম করতে লিজ নিয়ে নিয়েছে। আমি মনে করি নিজের স্বার্থেই শ্রীলঙ্কাকে সবল করতে চীন সচেষ্ট হবে। সুতরাং চীনের প্রতি শ্যেন দৃষ্টি দেওয়ার মানে হয় না।
অপর পক্ষে ভারত চাইবে না শ্রীলঙ্কায় চীনের আধিপত্য বাড়ুক। আবার শ্রীলঙ্কায় অস্থিতিশীল পরিস্থিতি চলতে থাকলে তার একটা ধাক্কা ভারতের উপকূলবর্তী জনপদেও লাগবে। ফলে ভারতও শ্রীলঙ্কাকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসবে, এটাই স্বাভাবিক।
শ্রীলঙ্কায় বামপন্থার উত্থানের ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্র এবং তার মিত্ররা সতর্ক। সুতরাং তারা যেনতেন প্রকারে শ্রীলঙ্কাকে স্থিতিশীল রাখায় সচেষ্ট হবে। বামপন্থার ব্যাপারে ভারতের ভেতর মিশ্র প্রতিক্রিয়া আছে। অধিকাংশ পক্ষ বামপন্থার ব্যাপারে শূচিবায়ূগ্রস্ত। তবে বামপন্থী শক্তি যদি দেশে স্থিতিশীলতা আনার রক্ষাকবচ হয়, তবে বামপন্থী একটা সরকার মেনে নিতে তাদের আপত্তি থাকবে না।
শ্রীলঙ্কা তাহলে কোন পথে?
সঠিক উত্তরটা একমাত্র সময়ই বলতে পারবে। তবে এইটুকু বোঝা যাচ্ছে যে পথই হোক, সে পথে উঠতেই শ্রীলঙ্কার আরও সময় লাগবে। ২০ জুলাই নতুন প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন রনিল বিক্রমাসিংহে। নতুন প্রেসিডেন্টের ওপর অনেক কিছু নির্ভর করছে। কারণ তাকে একাধারে দুই বিপরীত শক্তি ভারত ও চীনের মুখোমুখি হতে হবে। অন্যদিকে রাজপথকে সামলাতে হবে। তাকে পশ্চিমা বিশ্বকে আশ্বস্ত করতে হবে, আবার সেনাবাহিনীর মন জুগিয়ে চলতে হবে। তাকে আইএমএফ ও আন্তর্জাতিক সংস্থার কাছে ধর্ণা দিতে হবে, আবার অন্যদিকে রাশিয়া থেকে কম দামে জ্বালানি জোগাড় করতে হবে।
প্রেসিডেন্ট যদি জনপ্রিয় না হন, তার যদি জনসমর্থন না থাকে, তাহলে যেখানেই যে সমঝোতা বা নেগোসিয়েশনে যাবে, বেশি বেশি ছাড় দিয়ে আসতে হবে। আর যদি উল্টোটা হয়, তবে নেগোসিয়েশনের সময় তার মনোবল চাঙা থাকবে। নতুন প্রেসিডেন্টকে যেমন জনগণের আস্থাভাজন হতে হবে, জনগণকেও তেমন একজন আস্থাভাজনকে প্রেসিডেন্ট পদে বসাতে হবে। অর্থাৎ শ্রীলঙ্কার এই সংকট উত্তরণের একধরনের চাবিকাঠি জনগণ নিজেই।
লেখক: আন্তর্জাতিক রাজনীতি বিশ্লেষক ও সাবেক রাষ্ট্রদূত