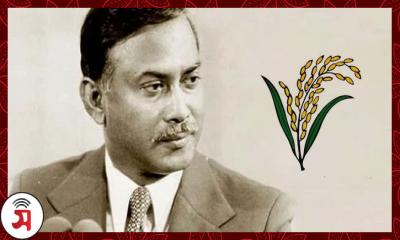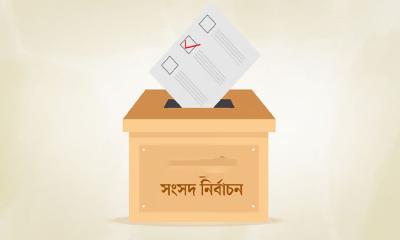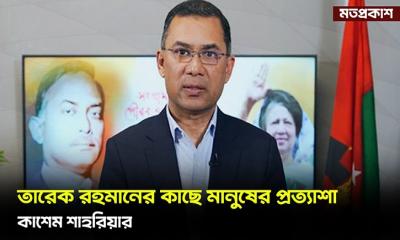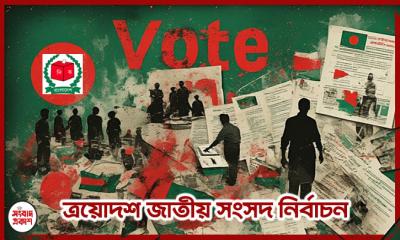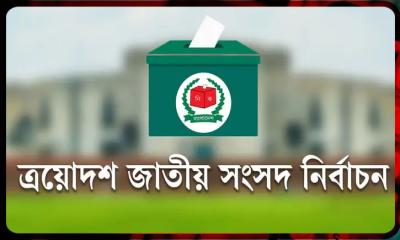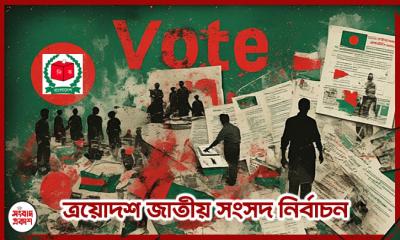১৯৭১ সালের প্রসঙ্গ এলে আমরা আমাদের মুক্তিযুদ্ধকে স্মরণ করি। কেউ কেউ আরও কিছু দূর গিয়ে পশ্চিমবঙ্গের নকশাল আন্দোলনের কথা বলেন। খুব একটা কেউ বলেন না, ওই ১৯৭১ সালেরই এপ্রিলে, শ্রীলঙ্কায় মার্ক্সবাদী বামপন্থীদের একটি দল সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে ক্ষমতা দখলের জন্য সচেষ্ট হয়েছিল। তখনকার বিশ্ব পরিস্থিতি আজকের মতো ছিল না। সেই মার্ক্সবাদীদের সঙ্গে চীনের কিছুটা যোগাযোগ থাকলেও সমাজতান্ত্রিক বিশ্বের তৎকালীন নেতা সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে কোনো যোগাযোগ ছিল না। বরং শ্রীমাভো বন্দরনায়েকের নেতৃত্বে শ্রীলঙ্কায় তখন সোশ্যালিস্ট সরকার থাকায় সোভিয়েত ইউনিয়ন সেই সশস্ত্র সংগ্রামের বিরোধিতা করে তা দমনের জন্য শ্রীলঙ্কাকে সামরিক সহায়তা দেয়। যুগোশ্লাভিয়া, ভারত, পাকিস্তান এবং যুক্তরাজ্য, এমনকি যুক্তরাষ্ট্রও শ্রীলঙ্কাকে সামরিক সাহায্য দিয়েছিল। চীন শেষ দিকে এসে শ্রীলঙ্কাকে কূটনৈতিক সমর্থন জানিয়েছিল। সশস্ত্র বিদ্রোহীদের দল সহায়তা পেয়েছিল কেবল উত্তর কোরিয়া, আলবেনিয়া ও দক্ষিণ ইয়েমেনের। এর বাইরে ইরাকের বাথ পার্টির সমর্থন ছিল। এপ্রিলের দিকে কয়েক সপ্তাহ তারা শ্রীলঙ্কার দক্ষিণ অঞ্চল দখল করে রাখে। দেশের ভেতরে মাওপন্থী কমিউনিস্ট পার্টি বিদ্রোহীদের পক্ষে থাকলেও সোভিয়েতপন্থীরা সরকারকে সমর্থন করে। বিদ্রোহের সামগ্রিক পরিকল্পনা করেন রোহন বিজয়বীর।
কিন্তু বিদ্রোহ শুরুর আগেই বিজয়বীর গ্রেপ্তার হন। বিচারে তার যাবজ্জীবন হয়। আদালতে তিনি বলেছিলেন, আমাদের মৃত্যু হতে পারে, কিন্তু আমাদের বিপ্লবের কোনো মৃত্যু হবে না। ১৯৭৭ সালে তিনি মুক্তি পেয়ে ১৯৮২-তে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে অংশ নেন। ৪ ভাগ ভোট পেয়ে তৃতীয় হন। তাঁর দলের নাম জেভিপি বা জনতা ভিমুক্তি পেরামুনাই।
রোহন বিজয়বীর ১৯৮৭-তে দ্বিতীয়বারের মতো সচেষ্ট হন সশস্ত্র সংগ্রামের জন্য। এবারে বিজয়বীর গ্রেপ্তার এড়াতে চা-বাগানে আত্মগোপনে থাকেন। শ্রীলঙ্কার সশস্ত্র বাহিনী তাঁকে গ্রেপ্তার করে ১৯৮৯-এর অক্টোবরে। ১৩ নভেম্বর তাঁকে বিনা বিচারে গুলি করে হত্যা করা হয়। চে গেভারার মতো।
বিশ্বব্যাপী স্নায়ুযুদ্ধের অবসান হলে জেভিপি নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতিতে ফিরে আসে। সংসদ নির্বাচনে অংশ নিয়ে ১৯৯৪ সালে একটি সিট পায়। ২০০০ সালে ১০টি, ২০০-এ ১৬টি, এবং ২০০৪ সালে শতকরা ৪৫.৬ ভাগ ভোট পেয়ে ৩৯টি আসন পায়। বিদ্রোহী তামিলদের সঙ্গে যে প্রক্রিয়ায় শান্তি সমঝোতা চলছিল, জেভিপি তার বিরোধিতা করে। সে জন্য ২০০৫-এর প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে মাহিন্দা সমর্থন পায়। কিন্তু ২০১০-এ প্রেসিডেন্ট এবং সংসদ নির্বাচনে ইউএনপির সঙ্গে কোয়ালিশন করে ৪টা সিট পায়। ২০১৫-তেও মাহিন্দার বিরোধিতা করে সংসদ নির্বাচনে ৬টি সিট পায়। ২০১৯-এ প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করে তৃতীয় হয়। ২০২০-এ সংসদ নির্বাচনে ভোট কমে। ৩টি আসন নিয়ে চতুর্থ হয় জেভিপি।
রোহন যেমন বলেছিলেন, তাঁর মৃত্যু হলেও বিপ্লবের মৃত্যু হবে না, আন্দোলনের মৃত্যু হবে না, জেভিপি বিভিন্ন চড়াই-উতরাই পার হয়ে এখন সরকারবিরোধী চলমান আন্দোলনের অন্যতম প্রধান সংগঠিত শক্তি। জেভিপির নেতা অনুঢ়া কুমার দেশনায়েক সংসদে আছেন ২০০০ সাল থেকে। ২০১৪ থেকে তিনি জেভিপির প্রধান। ২০০৪ সালে মন্ত্রী ছিলেন। ২০১৯-এর প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে তিনি মাত্র ৩.১৬ ভাগ ভোট পান। কিন্তু এরপরের ঘটনা দ্রুত ঘটেছে। রাজাপক্ষের দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, দুঃশাসন ও অবহেলার বিরুদ্ধে অনুঢ়া শুরু থেকে উচ্চকণ্ঠ। কোভিড মহামারির সময় থেকে তাঁর দল রাজপথকে উত্তপ্ত করতে তৎপর ছিল। সংসদে মাত্র ৩টি আসন থাকলেও অনেকের কাছে অনুঢ়া তাই একটি বিকল্প।

শ্রীলঙ্কা অনিশ্চয়তার মধ্য দিয়ে প্রতিটি মুহূর্ত পার করছে এখন। ২০১৯ সালে দেশটি ৫ বছরের জন্য প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত করেছিল গোতাবায়া রাজাপক্ষেকে। ২০২০ সালে সংসদ নির্বাচনে ৫৯ ভাগ ভোট দিয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে পিপলস ফ্রিডম অ্যালায়েন্সের নেতা মাহিন্দা রাজাপক্ষেকে প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত করেছিল। অর্থনৈতিক সংকট, দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি, নিত্যব্যবহার্য পণ্যের ঘাটতি এই সব মোকাবেলায় ব্যর্থ হয়ে প্রধানমন্ত্রী ২০২২ সালের ৯ মে পদত্যাগ করেন। প্রেসিডেন্ট গোতাবায়া রাজাপক্ষে পদত্যাগ করেন ১৩-১৪ জুলাই। জনরোষ এড়াতে গোতাবায়া দেশ ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়েছেন।
রাজাপক্ষে পরিবারের বড় খুঁটি সেনাবাহিনী। তামিল যোদ্ধাদের হাতে মার খেতে খেতে শ্রীলঙ্কান সেনাবাহিনী যখন পাল্টা মরণ আঘাত দিতে বেপরোয়া হয়ে ওঠে, তখন এই রাজাপক্ষেরা তাদের রাজনৈতিক সমর্থন দিয়েছিল। সেনাবাহিনী তার প্রতিদান দিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী ও প্রেসিডেন্ট–দুই রাজাপক্ষে ভ্রাতা–দুজনকেই বিপদের সময় শ্রীলঙ্কা ত্যাগ করতে নিরাপদ প্যাসেজ দিতে চেয়েছে সেনাবাহিনী।
সিংহল-তামিল বিরোধ এবং গৃহযুদ্ধের কথা শুনলেও জাতি হিসেবে শ্রীলঙ্কানদের নৃশংসতা বা সহিংসতার খুব একটা পরিচয় পাওয়া যায় না। তবে এবারে সেনাবাহিনীর প্যাসেজ সুবিধা না পেলে শ্রীলঙ্কানরা সরকার ও রাষ্ট্রপ্রধানদের নিয়ে রাজপথে হোলি খেলতে পারত। পরিস্থিতি এমনই ভয়াবহ। পরিস্থিতি এখনো ভয়াবহ। উন্নয়নশীল দেশে এমন পরিস্থিতি সামরিক শাসন জারি এবং সামরিক বাহিনীর ক্ষমতা দখলের জন্য আদর্শ পটভূমি। শ্রীলঙ্কার সশস্ত্র বাহিনীর দিকে তাই পর্যবেক্ষক মহলের সতর্ক দৃষ্টি রয়েছে।
শ্রীলঙ্কার সংকট অর্থনৈতিক। কিন্তু শ্রীলঙ্কায় আন্দোলনকারীরা এ জন্য সর্বতোভাবে রাজনৈতিক নেতাদের দায়ী করছে। তাঁদের প্রধান ক্ষোভ রাজাপক্ষে পরিবারের প্রতি। প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী ছাড়াও মন্ত্রিপরিষদে তাঁদের পরিবারের আরও দুজন সদস্য আছে। সরকার ও প্রজাতন্ত্রের আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ পদ তাঁদের পরিবারের বা পরিবারকেন্দ্রিক গোষ্ঠীর দখলে। আন্দোলনকারীদের দ্বিতীয় ক্ষোভ অন্যান্য রাজনৈতিক দল ও পরিবারের প্রতি যাঁরা পর্যায়ক্রমে শ্রীলঙ্কার শাসন ক্ষমতায় ছিলেন।
প্রেসিডেন্ট পদত্যাগ করে দেশ ছেড়ে গেলে সেই শূন্যস্থান পূরণ করা নিয়ে এখন প্রাসাদ রাজনীতি চলছে। সংবিধান রক্ষা, সরকারের ধারাবাহিকতা রক্ষা, সংকট মোকাবেলা–এই সব ছুতানাতায় রাজনৈতিক নেতারা এখন প্রতিনিয়ত নানাবিধ সমীকরণ মেলাতে ব্যস্ত।
এই সব সমীকরণ মেলাতে মাস্টার ৭৩ বছর বয়সের আইনজীবী ও রাজনীতিক রনিল বিক্রমাসিংহে। নিজে এর মধ্যে পাঁচবার শ্রীলঙ্কার প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন। যদিও কোনোবার তিনি তাঁর পাঁচ বছরের মেয়াদ শেষ করতে পারেননি। তবে বারবার দায়িত্ব পাওয়ায়, বলতেই হয় যে তাঁর ভাগ্য সুপ্রসন্ন। ১৯৯৩ সালে তিনি প্রথমবারের মতো প্রধানমন্ত্রী হন যখন তামিল বিদ্রোহীদের হাতে প্রেসিডেন্ট রানাসিংহ প্রেমদাসা নিহত হন এবং তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী দিনগিরি বিজেতুঙ্গা প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব নেন। ২০০১ সালে সংসদ নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে তিনি ১৭তম প্রধানমন্ত্রী হন। এই সময়ে পশ্চিমের সহায়তায় তামিলদের সঙ্গে সমঝোতায় পৌঁছেন এবং যুদ্ধবিরতিতে যান। সমঝোতার একপর্যায়ে উভয় পক্ষ উভয় পক্ষকে যুদ্ধবিরতি চুক্তি ভঙ্গের অভিযোগ আনে। পরিস্থিতি ঘোলাটে হয়। তামিলরা নিজেদের রাষ্ট্র ঘোষণা করে। প্রেসিডেন্ট কুমারাতুঙ্গা তখন বিক্রমাসিংহের সরকার বাতিল করে নতুন নির্বাচন দেন। ২০০৪ থেকে রনিল বিরোধী দলের নেতা থাকেন। ২০০৫ সালে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করে হারেন। ২০১৫-তে তিনি আবার প্রধানমন্ত্রী হন যখন সিরিসেনা প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জেতেন। ৬ মাস পর সংসদ নির্বাচন হলে রনিল নতুন করে প্রধানমন্ত্রী হন। অক্টোবর ২০১৮ সালে তাকে প্রধানমন্ত্রিত্ব থেকে সরানো হলে তিনি আদালতে যান। ডিসেম্বরে পুনরায় প্রধানমন্ত্রিত্ব ফিরে পান। ২০২০-এর সংসদ নির্বাচনে তাঁর দল ইউএনপি গো-হারা হারে। মাত্র ২.১৫ শতাংশ ভোট পায়। কোনো সিট পায়নি। কিন্তু শতকরা দুই ভাগ ভোট পাওয়ায় দলের পক্ষে একটা সিট পায়। সেই সিটের বদৌলতে রনিল সংসদে ঢোকেন। কী ভাগ্য! রাজনীতিটা পাশা খেলার মতো। ১২ মে ২০২২ তাঁকে প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করা হয়। ১৩ জুলাই ২০২২ থেকে তিনি আবার অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট। ভালো। রনিল বিক্রমাসিংহের পোর্টফোলিও তাই খুব ভারী।
কিন্তু তাঁর এই ভার শ্রীলঙ্কার জনগণ আর বহন করতে রাজি কি না, সে এক প্রশ্ন। এখনো মাঠে আন্দোলন, সংকটে অর্থনীতি, স্থবির জনজীবন, অনিশ্চিত শ্রীলঙ্কার ভবিষ্যৎ। অন্যদিকে রাজনীতিকরা সক্রিয় নতুন সরকার গঠনের লড়াইয়ে। শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্ট নির্বাচন হয় জনগণের সরাসরি ভোটের মাধ্যমে। ২০১৯-এ সেই নির্বাচন হয়ে যাওয়ায়, পরবর্তী নির্বাচন হবে ২০২৪-এ। এর মধ্যে প্রেসিডেন্টের শূন্য পদ পূরণ করতে পারে সংসদ।
এই সংসদ গঠিত হয়েছে ২০২০-এর নির্বাচনের ভিত্তিতে। সেখানে সর্বমোট ২২৫টি সিটের মধ্যে মাহিন্দা রাজাপক্ষের নেতৃত্বে ১৭টি দল সমন্বয়ে গঠিত জোট পিপলস ফ্রিডম অ্যালায়েন্সের দখলে ১৪৫টি। সাজিথ প্রেমাদাসার নেতৃত্বাধীন প্রধান বিরোধী দল ইউনাইটেড পিপলস পাওয়ারের দখলে মাত্র ৪৫টি। সুতরাং সংসদ যদি প্রেসিডেন্টকে বেছে নেয়, তবে রাজাপক্ষের নেতৃত্বাধীন জোট থেকেই নতুন প্রেসিডেন্টের নির্বাচিত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। সেই জোটের পক্ষে ইতোমধ্যে দুলাস আলাহাপেরুমা তাঁর অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছেন। আবার জোটের অনেকে রনিল বিক্রমাসিংহেকে এই সংকট মোকাবেলার জন্য অভিজ্ঞ ও উপযুক্ত মনে করছেন।
রনিল বিক্রমাসিংহে সারা জীবন দক্ষিণপন্থী ইউনাইটেড ন্যাশনাল পার্টি করেছেন। এই পার্টি থেকে তিনি প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন, বিরোধী দলীয় নেতার আসনে ছিলেন। কিন্তু ২০১৯ সালে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে পরাজয়ের পর দলের প্রার্থী সাজিথ প্রেমাদাসা ইউএনপি ছেড়ে নিজের দল করেন এবং সেভাবে ২০২০ সালে সংসদ নির্বাচনে অংশ নেন। ইউএনপির অধিকাংশ নেতা-কর্মী সাজিথের সঙ্গে দল ছাড়েন। রনিল একা হয়ে পড়লেও ক্ষমতার আকর্ষণ তাকে ছাড়ে না। ২০২০ থেকে তিনি তাঁর একসময়কার প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী রাজাপক্ষেদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ক্ষমতার কাছাকাছি আসেন। তাঁর ধৈর্য, সহনশীলতা এবং চেয়ারের প্রতি আকর্ষণ তাঁকে আপাতত শ্রীলঙ্কার শীর্ষ পদ অলংকৃত করার সুযোগ দিয়েছে। দেখতে হবে তিনি তা ধরে রাখতে পারেন কি না।

রনিল বিক্রমাসিংহের প্রতিদ্বন্দ্বী অনেক। আপাত বিচারে অন্তত দুজন খুব শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী। একজন আলাহাপেরুমা। বর্তমান ক্ষমতাসীন জোটের প্রতিনিধি। অন্যজন সাজিথ প্রেমাদাসা। তামিলদের হাতে নিহত প্রেসিডেন্ট রানাসিংহে প্রেমদাসার সন্তান সাজিথ বর্তমান সংসদে বিরোধী দলের নেতা, যিনি গত প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে গোতাবায়ার কাছে হারলেও শতকরা ৪২ ভাগ ভোট পেয়েছিলেন। ত্রিমুখী এই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ছোট দলগুলোর একটা ভূমিকা আছে। এগুলোর মধ্যে তামিল ন্যাশনাল অ্যালায়েন্সের ১০, তামিল ন্যাশনাল পিপলস ফ্রন্টের ২, তামিল মাকাল পুলিকালের ১, ইলাম পিপলস ডেমোক্রেটিক পার্টির ২ এবং তামিল পিপলস ন্যাশনাল অ্যালায়েন্সের ১ সিট আছে। দুটি মুসলমানের সংগঠনের আছে ২ সিট, এবং কট্টর বামপন্থী জেভিপি বা ন্যাশনাল পিপলস পাওয়ারের আছে ৩টি সিট।
শ্রীলঙ্কার রাজপথে এখন যে আন্দোলন চলছে, তা সর্বমত ও পথের আন্দোলন। সুতরাং এই আন্দোলনের জের ধরে নির্বাচনের মাধ্যমে সমস্যার সমাধানের উদ্যোগ নেওয়া হলে তা নির্বাচনের চোরা পথে হারিয়ে যাবে। আন্দোলনকারীদের মধ্যে ডানপন্থী বৌদ্ধ ভিক্ষুরা যেমন আছেন, তার চেয়েও বেশি সক্রিয় মাত্রায় আছেন কট্টর বামপন্থীরা।
আন্দোলনকারীদের বড় অংশ মনে করছেন, ট্রাডিশনাল পথে হয়তো শ্রীলঙ্কা সংকটের সমাধান হবে না। রনিল বিক্রমাসিংহে, সাজিথ প্রেমদাসা কিংবা দুলাস আলাহাপেরুমা—প্রত্যেকে মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ। প্রত্যেকে শ্রীলঙ্কার ক্ষমতাকেন্দ্রিক রাজনীতির প্রোডাক্ট। এর বাইরে সামরিক বাহিনীর পূর্বতন প্রধানরা বা বর্তমান প্রধান–কেউই হয়তো অর্থনৈতিক সংকট মোকাবেলা করার জন্য যথেষ্ট না। আর সামরিক শাসন দিয়ে জন-অসন্তোষকে ধামাচাপা দেওয়া স্বল্প মেয়াদে সম্ভব হলেও দীর্ঘ মেয়াদে খুব ঝুঁকিপূর্ণ হবে।
আন্তর্জাতিক রজনীতি বিশেষ করে ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধ নিয়ে পশ্চিমের অতি মাত্রায় ব্যস্ততা শ্রীলঙ্কার ঘটনাপ্রবাহে ভিন্ন একটা মাত্রা নিয়ে এসেছে। নিকট প্রতিবেশী হিসেবে ভারত সতর্কতার সঙ্গে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছে। চীনও তাই। তবে সাধারণভাবে চীনের ঋণ শ্রীলঙ্কার জন্য বোঝা হয়েছে, এমন ধারণা প্রচলিত থাকায় চীন কিছুটা দূরত্ব বজায় রেখে যাচ্ছে। ভারতও সতর্ক, কারণ যতক্ষণ পর্যন্ত না শ্রীলঙ্কায় রাজনৈতিক পরিস্থিতি উত্তপ্ত আছে, ততক্ষণ পর্যন্ত ভারতও প্রকাশ্যে কোনো পক্ষ নিতে চাচ্ছে না। আপাতদৃষ্টে ভারত সাজিথ প্রেমাদাসার সঙ্গে যোগাযোগ রেখে যাচ্ছে। শ্রীলঙ্কার ব্যবসায়ীরা স্থিতিশীলতা চান। তাদের সাধারণ সমর্থন সাজিথ প্রেমদাসার দিকে। রনিল বিক্রমাসিংহে আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর সঙ্গে তাঁর পুরোনো সম্পর্ক ঝালাই করার চেষ্টা চালাচ্ছে, যেন তাদের সহযোগিতায় সে ক্ষমতা পাকাপোক্ত করতে পারে। দুলাসের শক্তি তাঁর দলের সংসদ সদস্যদের আনুগত্য এবং সামরিক বাহিনীর আশীর্বাদ। অপর দিকে অনুঢ়া কুমার দেশনায়েকের নির্ভরতা রাজপথের আন্দোলন।
শ্রীলঙ্কা মোটামুটি আমাদের কাছের দেশ। একেবারে ভারত বা মিয়ানমারের মতো প্রতিবেশী না হলেও বঙ্গোপসাগরের কল্যাণে নিকট প্রতিবেশী বলা যায়।
আমরা বলি, আমরা ঔপনিবেশিক শাসনাধীন ছিলাম ২০০ বছর। ঘটনাক্রমে শ্রীলঙ্কা ১৫০৫ সালে পর্তুগিজদের আগমনের পর থেকে প্রায় ৪৫০ বছর ঔপনিবেশিক শাসনের অধীন ছিল। পর্তুগিজদের পরে ডাচরা আসে, আর ক্যান্ডির উঁচু জঙ্গলে দারুচিনির লোভে মজে থাকে। কিন্তু ইউরোপে যখন ব্রিটিশদের হাতে ডাচরা কোণঠাসা, তখন শ্রীলঙ্কাতেও তার রেপ্লিকা মঞ্চস্থ হয় এবং ডাচদের হটিয়ে দ্বীপটির নতুন অভিভাবক সাজে ব্রিটিশরা। আজকে শ্রীলঙ্কায় চা ও কফির যে চাষ, তা ব্রিটিশদের হাত ধরেই। তবে শুরুটা সহজ ছিল না তাদের জন্য। ব্রিটিশদের হুমকি-ধমকি ক্যান্ডির পাহাড়ের ঢালে বসবাস করা মানুষদের টলাতে পারেনি। বিকল্প হিসেবে ১৮৪০ সালের দিকে ব্রিটিশরা ভারতের তামিলনাড়ু থেকে ধরেবেঁধে তামিল শ্রমিক এনে ফেলে ক্যান্ডির পাহাড়ে। পাঠকদের বুঝতে অসুবিধা হওয়ার কথা না, এই তামিলরাই পরবর্তীকালে শ্রীলঙ্কার জন্য কী পরিমাণ অভিশাপ হয়ে দাঁড়ায়!
ব্রিটিশদের কফি-হানিমুন বেশি দিন টেকেনি। ১৮৭০ সালের দিকে এক ভাইরাস এসে কফি চাষ ধ্বংস করে দেয়। ব্রিটিশরা দমে যায়নি। কফির বদলে তখন তারা চা চাষ শুরু করে। কালো রঙের তামিল শ্রমিকরা তো ছিলই। পাহাড়ের ওপর দিক থেকে ক্রমান্বয়ে নিচের দিকে নামলে চায়ের পর রাবার চাষ হয়। একেবারে নিচে সৈকতের কাছাকাছি নারকেলের চাষ। শ্রীলঙ্কার কৃষিতে এবং রপ্তানিতে এই তিনের ভূমিকা বেশি। রাজাপক্ষে বাধ্যতামূলক অর্গানিক কৃষি চালু করায় কৃষি উৎপাদন কমে গিয়েছিল। রাজাপক্ষেদের অনুপস্থিতিতে শ্রীলঙ্কায় এখন নিশ্চিত ভারতীয় সার ঢুকবে।
প্রশ্ন হলো, সমাধান কী? কিংবা ভিন্নভাবে বললে, ভবিষ্যৎ কী? দুটো প্রশ্নের উত্তর একরকম না। ভবিষ্যৎ আরও কিছুদিন অর্থনৈতিক সংকট, এবং তার চেয়ে বড় রাজনৈতিক সংকট। সংকট মোকাবেলার জন্য প্রয়োজন সময়, যা শ্রীলঙ্কার হাতে আছে খুব কম। জ্বালানির জোগান হলে সরকার কিছুটা বাড়তি জীবন পাবে। এই সময়ের মধ্যে সর্বক্ষেত্রে স্থিতিশীলতা আনতে পারলে শ্রীলঙ্কা পুনরায় তার নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারবে। তবে রাজনৈতিক নেতারা নিজেদের মধ্যে ক্ষমতার লড়াই চালাতে থাকলে এই সুযোগটি হাতছাড়া হবে। তখন কোনো আন্তর্জাতিক সংস্থা বা দ্বিপক্ষীয় সাহায্য আশা করা বৃথা।
রোহন বিজয়বীরের উত্তরসূরিরা আন্দোলন যতই করুক, একেবারে আউট-অব-দ্য-বক্স সমাধান আশা করা খুবই চ্যালেঞ্জিং। সব জায়গাতে দেখেছি জনতার এই সব আন্দোলন একসময় নানা কারণে স্তিমিত হয়ে যায়। শ্রীলঙ্কায় এ ধরনের কারণের ঘাটতি নেই। অনুঢ়া বলেছেন তিনি দাতা সংস্থাগুলোর কাছে তিন বছর সময় চাইবেন। আমি মনে করি তিন বছরে অবশ্যই শ্রীলঙ্কা ঘুরে দাঁড়াতে পারবে, যদি তাকে সুযোগ দেওয়া হয়। কিন্তু আন্তর্জাতিক সংস্থাই হোক, আর দ্বিপক্ষীয় সূত্রই হোক, টাকা যারা ধার দেয় তারা কাবুলিওয়ালাদের চাইতেও অনেক বেশি স্মার্ট। তাদের জন্য অনুঢ়া কোনো ভালো দেনাদার না, তাদের পছন্দ রনিল বিক্রমাসিংহে। তাদের পছন্দ সাজিথ প্রেমাদাসা, দুলাস আলাহাপেরুমা। আর না হয় উর্দি পরা সাহেবরা তো আছেনই।
শ্রীলঙ্কার সংকট, আন্দোলন এবং সম্ভাব্য উত্তরণ–আমাদের রাজনীতিকদের জন্য অতি জরুরি পাঠ্যবইয়ের মতো। দেখা যাক, সম্ভাব্য উত্তরণের যে চিত্রটি আমাদের সামনে আছে, তার কোনটি চিত্রায়িত হয়।
লেখক: আন্তর্জাতিক রাজনীতি বিশ্লেষক ও সাবেক রাষ্ট্রদূত