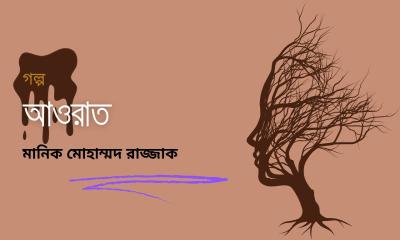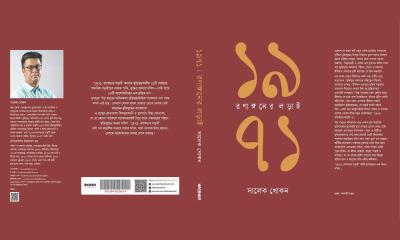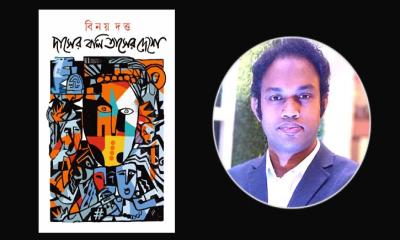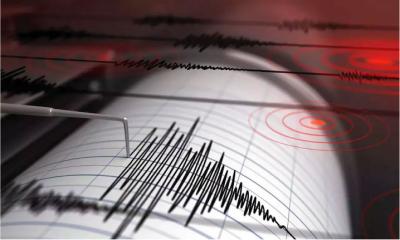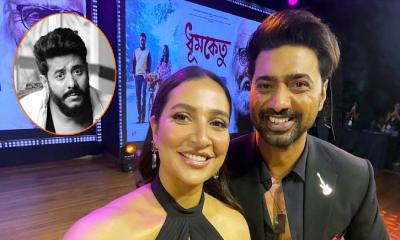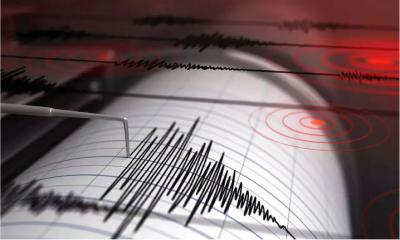বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে ঋতুপর্ণ ঘোষের ‘থার্ড পারসন’ বইতে দারুণভাবে লেখা আছে—‘তবে বঙ্গবন্ধুকে আলাদা লাগে। তিনি বাংলায় বক্তৃতা দেন। রাষ্ট্রপ্রধানরাও বাংলা বলেন বুঝি? তখনো কমপ্লেক্স সেন্টেন্সে ইংরেজি বলতে পারি না। বুঝি রাষ্ট্রপ্রধানদের সঙ্গে কথোপকথন কখনোই বুঝি আর হয়ে উঠবে না আমার। উত্তম-সুচিত্রার ছবিতে দিন কতেক কারও মন নেই। সে জায়গাটা নিয়ে নিয়েছেন মুজিব-ইন্দিরা। যেন তারাই নায়ক-নায়িকা। ইন্দিরা গান্ধীকে দেখলে মনে হয় রাশভারী, দাম্ভিক। তাকে টপকে কি আর বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে কথা বলা যাবে? হয়তো প্রথম বাক্যেই থামিয়ে দেবেন। তারপর একদিন সিনেমার নায়কের থেকেও অনেক বেশি নাটকীয়ভাবে বাড়ির দেয়ালে রক্তের পিচকারি দাগ রেখে চলে যান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। আর, আমার আর কোনো প্রথম রাষ্ট্রনায়কের সঙ্গে বাংলা বলা হয় না এ জীবনের মতো।’
এক ইন্টারভিউয়ে ঋতুপর্ণ ঘোষ বলেছিলেন, “এই শহর না আমায় নিতে পারবে, না ফেলতে পারবে।”
দুই দশকের কর্মজীবনে ১৯টি চলচ্চিত্রের ১২টি পেয়েছে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে জাতীয় পুরস্কার এবং পেয়েছেন বেশ কয়েকটি আন্তর্জাতিক পুরস্কার। চিত্রনাট্যনির্ভর চলচ্চিত্র বলতে যা বোঝায়, তার নির্মিত সব কটিই তাই। শিক্ষকদের শিক্ষক ছিলেন তিনি। লেখক, পরিচালক, অভিনেতা—সব ক্ষেত্রেই তিনি ছিলেন সফল বিতর্কিত নায়ক। বাঙালির মনোজগৎকে সেলুলয়েডে বন্দি করে আন্তর্জাতিক দর্শকের কাছে নতুন করে বাংলা ছবি তিনিই পৌঁছে দিয়েছিলেন। প্রচলিত কিংবা চালু ধ্যানধারণাগুলোকে ভেঙেচুরে নিজের আঙ্গিকে অনন্য এক মাত্রা যোগ করা চিত্রপরিচালকের আরেক নাম হচ্ছে—ঋতুপর্ণ ঘোষ।
পরিচালক হিসেবে ঋতুপর্ণ ঘোষের সবচাইতে বড় যে গুণ তা হচ্ছে, যেকোনো মানুষকে দুর্দান্ত অভিনেতা/অভিনেত্রীতে পরিণত করা। চিরঞ্জিত, প্রসেনজিৎ, বিপাশা বসুরা নাকি অভিনয় পারেন না—এই ভুল তিনি ভাঙিয়ে দিয়েছিলেন প্রচণ্ডভাবে। আজকের যীশু সেনগুপ্ত, কঙ্কণা সেন শর্মা তার বানানো। পাওলি দাম নামটাও নেওয়া যায় এ ক্ষেত্রে। তার নির্মিত যেকোনো চলচ্চিত্রের চরিত্র রূপায়ণকারী নামগুলোর দিকে তাকান, যদি সেই চলচ্চিত্রটি দেখে থাকেন, আপনার চোখে কোনো নায়ক-নায়িকার ছবি ভাসবে না। যেটা ভাসবে তার নাম ‘অভিনেতা-অভিনেত্রী’। এই ছোট পরিসরে ঋতুপর্ণ ঘোষকে ধারণ করা সম্ভব নয়। নব্বই দশকের পর সত্যজিৎ-পরবর্তী পশ্চিমবঙ্গের মধ্যবিত্ত বাঙালিদের হলমুখী করে তবেই ছেড়েছেন। শিল্পের মানদণ্ডে তার চলচ্চিত্রগুলো একেকটা মাইলফলক। তিনি সময়কে সেলুলয়েডে বন্দি করে রেখেছেন। কজন পারে?
ঋতুপর্ণের সিনেমাকে তিন ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। এক, ‘হিরের আংটি’ থেকে শুরু করে ‘শুভ মহরৎ’। যে সময়ের প্রতিটি চলচ্চিত্র দর্শকের ভালোবাসা এবং সমালোচকদের প্রশংসা দুই-ই পেয়েছে। দুই, ‘চোখের বালি’ থেকে ‘সব চরিত্র কাল্পনিক’। যখন তার ছবিতে বলিউডি তারকাদের ঘনঘটা। তিন, ‘আবহমান’ থেকে ‘চিত্রাঙ্গদা’। যেখানে পরিচালক-অভিনেতা হিসেবে তার প্রতিভার বিকাশ ঘটেছে।
রেইনকোট দেখেছেন? ও. হেনরির ছোটগল্প ‘দ্য গিফট অব দ্য ম্যাজাই’ অবলম্বনে নির্মিত এই হিন্দি চলচ্চিত্রটি কোনো এক বৃষ্টির দিনে দেখুন। হারিয়ে যাওয়া ভালোবাসা (প্রেম নয়), অন্তর্দ্বন্দ্ব, মনের টানাপোড়ন, একে অপরের কাছে মিথ্যে ভালো থাকার অভিনয় করা, ধরা পড়ে যাওয়ার গল্প কী যে এক আবেশে জড়িয়ে ধরবে—আহা!
আবহমান—এক পরিচালক ও তার আত্মিক সাথী অভিনেত্রীর গল্প দেখুন। এই চলচ্চিত্রে দীপঙ্কর দে, মমতা শঙ্কর, অনন্যা চট্টোপাধ্যায়, যীশু সেনগুপ্তদের সাবলীল যথার্থ অভিনয় পরতে পরতে এঁকেছেন পরিচালক ঋতুপর্ণ ঘোষ।
চোরাবালি, নৌকাডুবি, চিত্রাঙ্গদা দেখুন। রবীন্দ্রনাথের কী সহজ, অসাধারণ শৈল্পিক উপস্থাপন! মহাভারত যেন শুধু এক ধর্মীয় গ্রন্থ হিসেবে পড়ে না থাকে, সে কথা মাথায় রেখে আজকের জীবনের সাথে মিশিয়ে নির্মাণ করলেন ‘চিত্রাঙ্গদা: দ্য ক্রাউনিং উইশ’ এবং সেটাতে অভিনয় করে নিজের অভিনয় প্রতিভারও জাত চেনালেন দর্শকদের।
‘বাড়িওয়ালি’ ছবিতে কিরণ খেরের মাধ্যমে কী চমৎকার নিঃসঙ্গ একজন মানুষের বাড়িওয়ালি হয়ে ওঠার গল্প উঠে এসেছে, সেটা দেখুন। দহন, ১৯শে এপ্রিল, চোখের বালি ও মেমরিজ ইন মার্চ ছবির নারী চরিত্রগুলো সবার দৃষ্টি কেড়েছে।
ব্যোমকেশ বক্সীর ওপরে বানালেন ‘সত্যান্বেষী’। আগাথা ক্রিস্টির ‘দ্য মিরর ক্র্যাকড ফ্রম টু সাইড’ গল্পকে নিজের মত করে নিয়ে শর্মিলা ঠাকুর, রাখী গুলজার, নন্দিতা দাসদের নিয়ে বানালেন অনন্য এক গোয়েন্দা গল্পের ছবি ‘শুভ মহরৎ’।
‘তিতলি’ ছবিতে মা-মেয়েকে একই ফ্রেমে এনে অপর্ণা-কঙ্কণাকে যেভাবে ব্যবহার করেছেন, তা কি ভোলা যায়! এই ছবির বিখ্যাত একটি গানের কলি এই লিখতে লিখতে মনে পড়ল—
‘মেঘ পিয়নের ব্যাগের ভিতর মন খারাপের দিস্তা
মন খারাপ হলে কুয়াশা হয়, ব্যাকুল হলে তিস্তা…
‘১৯শে এপ্রিল’ চলচ্চিত্রে অপর্ণা সেনের অভিনয়ের মাধ্যমে দুর্দান্তভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন ক্যারিয়ার সচেতন একজন নারীর কষ্টসহিষ্ণু জীবনের উপাখ্যান। স্বামী, ক্যারিয়ার, মেয়েকে নিয়ে গড়া এক নারীর গল্প।
আবার ‘দহন’ চলচ্চিত্রে ঋতুপর্ণা সেনগুপ্তের গৃহবধূর চরিত্রের মাধ্যমে ফুটিয়ে তুললেন এক অপমানিত নারীর আর্তচিৎকার। সমাজ যেখানে মেয়েদের কণ্ঠ দাবিয়ে রাখতে সচেষ্ট সেখানে ইন্দ্রাণী হালদারের চরিত্রের মাধ্যমে দিলেন অন্য এক বার্তা। ঋতুপর্ণা আর ইন্দ্রাণী হালদারের যুগলবন্দীতে দেখালেন প্রকৃত নারীশক্তি, অথবা প্রতিবাদ, কিংবা সমাজকে আবার চিন্তা করতে শেখানো।
‘অসুখ’ সিনেমাটার দেখে এখনো মন খারাপ হয়। আমার বান্ধবীরও পছন্দের সিনেমা। সে সিনেমায় রবি ঠাকুরের আমার একটা প্রিয় কবিতা আছে—
‘পূর্ণ হয়েছে বিচ্ছেদ, যবে ভাবিনু মনে,
একা একা কোথা চলিতেছিলাম নিষ্কারণে ।
শ্রাবণের মেঘ কালো হয়ে নামে বনের শিরে,
খর বিদ্যুৎ রাতের বক্ষ দিতেছে চিরে,
দূর হতে শুনি বারুণী নদীর তরল রব—
মন শুধু বলে, অসম্ভব এ অসম্ভব।’
‘দোসর’ ছবিতে প্রসেনজিৎকে চিরায়ত ইমেজ থেকে বের করে এনে অভিনয়ের কি চমৎকার প্রদর্শন! কঙ্কণার নীরব অভিনয়, অথবা না- অভিনয়। এক আকস্মিক দুর্ঘটনায় একটি পরিবারের কী হতে পারে? স্ত্রী অন্য পুরুষের সঙ্গে হোটেলে রাত কাটাচ্ছে, পুরুষত্বহীন পৌরুষ সেটাকে কিভাবে মেনে নেবে? এই সব জটিল প্রশ্নের উত্তর সহজে বলতে পারাটা একমাত্র ঋতুপর্ণ ঘোষের পক্ষেই সম্ভব।
‘অন্তরমহল’, ‘দহন’, ‘মেমরিজ ইন মার্চ’, ‘১৯শে এপ্রিল’, ‘উৎসব’ কিংবা ‘হিরের আংটি’ আর ‘সানগ্লাস’ চলচ্চিত্রগুলোর তুলনামূলক বিশ্লেষণে কোনটাকে ঠিক কার থেকে ভালো কিংবা খারাপ বলা যায়—তা আমার মাথায় আসে না। আসলে, তার কোন ছবিটি নিয়ে ঠিক পাতার পর পাতা শৈল্পিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক আলোচনা হতে পারে না, বলতে পারেন? চিত্রনাট্য, ডায়ালগ, গান, দৃশ্যায়নে এমন দক্ষ কয়জন? সত্যজিৎ রায়, মৃণাল সেন, ঋত্বিক ঘটকের পর চলচ্চিত্র যে বাংলা সাহিত্যের শেকড় থেকে বিচ্যুত হয়ে গিয়েছিল সেটাকে ফিরিয়ে এনেছেন তিনিই।
‘আরেকটি প্রেমের গল্প’তে অভিনেতা হিসেবে এমনভাবে সমকামীদের মনস্তাত্ত্বিক ব্যাপার ও দুঃখকে উঠিয়ে আনলেন। পরিচালক কৌশিক গাঙ্গুলি এই সিনেমায় ঋতুপর্ণের স্টান্স নিয়ে তাঁকেই ব্যবহার করে কী ছক্কাটাই না মারলেন!
ঋতুপর্ণ ঘোষের প্রায় সব ছবিতে শারীরিক সম্পর্কগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। তিনি রূপক অর্থে নয়, বরং বিনয়ের সঙ্গে যৌনতাকে দেখিয়েছেন। সেই যুগের পরিপ্রেক্ষিতে নিজের মতামত প্রদানে এতটা বোল্ড মানুষও ‘অন্তরমহল’ সিনেমার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন শুধু মধ্যবিত্ত বাঙালি দর্শকের মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর জন্য। কারণ, তাঁর অন্য সিনেমাগুলোতে ‘অ্যাডাল্ট বিষয়বস্তু’র ব্যাপারটা উল্লেখ করা থাকলেও এখানে তা ছিল না, পোস্টারে কোনো ইঙ্গিতও (তাই বলে যৌনদৃশ্য নয়) দেওয়া ছিল না। তিনি যৌনতাকে হাতিয়ার হিসেবে নিয়ে কখনোই নিজের সিনেমার জন্য বাজার ধরতে সচেষ্ট ছিলেন না। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল অনেক উঁচু দরের।
তিনি পারিবারিক ও মানবজীবনের পারস্পরিক সম্পর্কগুলোর মধ্যকার জটিল মনস্তাত্ত্বিক টানাপোড়নকে এতো সহজে ফুটিয়ে তুলিয়েছিলেন যে, যেকোনো শ্রেণির দর্শক তাতে মুগ্ধ হতে বাধ্য। ভালো চলচ্চিত্রের দর্শক হলে, বাংলা চলচ্চিত্রকে ভালোবাসলে— ইংমার বার্গম্যান ও সত্যজিৎ রায়কে আদর্শ হিসেবে মান্য করা ঋতুপর্ণ ঘোষকে এড়িয়ে যাওয়া, না দেখে থাকা, তাঁর আবেদন ও অবদানকে অগ্রাহ্য করা— অসম্ভব একটি কাজ।
শত প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি, হাজারো আলোচনা-সমালোচনা, তর্ক-বিতর্ক, ঘৃণা-ভালোবাসার মায়াজাল পেরিয়ে প্রজন্মের বিরল এক প্রতিভার নাম ঋতুপর্ণ ঘোষ। জন্মদিনে তাঁকে স্মরণ।