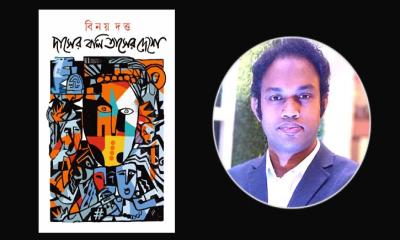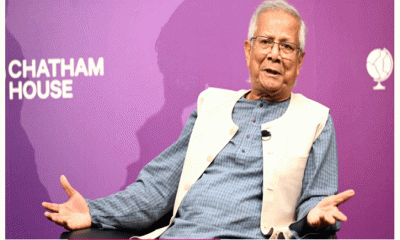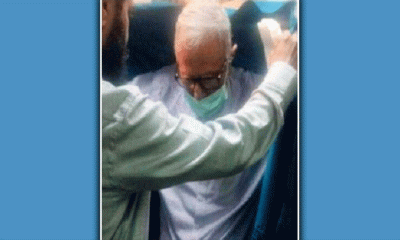রাজনৈতিক চলচ্চিত্র নির্মাণের চেয়ে চলচ্চিত্রকে রাজনৈতিকভাবে নির্মাণের প্রয়াসটাই বেশি চোখে পড়ে মৃণাল সেনের বেলায়। এর কারণ তিনি যে সময়ের ভেতর দিয়ে বেড়ে উঠেছেন, সেই সময়টি ছিল ক্রান্তিকাল, ঔপনিবেশিক শক্তিকে পরাজিত করতে চাওয়া জাতীয়তাবাদী চেতনার উত্থানপর্ব। মৃণাল সেন জন্মেছিলেন ১৯২৩ সালের বাংলাদেশে, ফরিদপুর অঞ্চলে। তাঁর বয়স যখন আট, তখন বঙ্কিমচন্দ্রের ‘বন্দে মাতরম’ গান গেয়ে মিছিলে অংশগ্রহণের দায়ে আটক হন তিনি। পুলিশের জিম্মায় ঘণ্টাখানেক থাকার পর রেহাই পান, নেহাত বয়স কম বলে। রাজনৈতিক দীক্ষা তিনি পেয়েছিলেন আইনজীবী বাবার কাছ থেকে। সে সময়কার বিপ্লবী, স্বাধীনতাসংগ্রামীদের আইনি সহায়তা দিতেন মৃণাল সেনের বাবা দীনেশচন্দ্র সেন।
বয়স সতেরো হলে পড়ালেখার জন্য কিশোর মৃণালকে কলকাতা পাঠিয়ে দেন বাবা-মা। সেখানে প্রথমে মৃণাল সেন নিজেকে আবিষ্কার করেন নাগরিক ভিড়ের ভেতর নিঃসঙ্গ ও শঙ্কিত সত্তা হিসেবে। তবে ধীরে ধীরে কলকাতার সঙ্গেই তার অম্ল-মধুর সম্পর্ক গড়ে ওঠে। স্কটিশ চর্চা কলেজে রসায়ন পড়া মানুষটির ভেতর শহরকেন্দ্রিক যে রসায়ন সৃষ্টি হয়, রাজনীতির জারণে যে রাজনৈতিক অধিকার সচেতনতার স্ফুরণ ঘটে, তারই প্রতিফলন ঘটতে থাকে তাঁর পরবর্তী জীবনে। কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে যুক্ত হওয়া, মার্কসবাদী সাহিত্য পাঠ করা, ভারতের পিপলস থিয়েটার অ্যাসোসিয়েশনের কার্যক্রমে অংশ নেওয়ার মধ্য দিয়ে মৃণাল সেন প্রস্তুত হতে থাকেন।
যদিও প্রথম ছবি ‘রাতভোর’ (১৯৫৬) বানিয়ে সন্তুষ্ট ছিলেন না মৃণাল সেন। ছবিটিকে ‘বিপর্যয়’ বলে সম্বোধন করেছেন নিজেই। এমনকি দ্বিতীয় ‘নীল আকাশের নীচে’ (১৯৫৮) ছবিতেও নিজের কণ্ঠস্বর খোঁজার চেষ্টা করছিলেন মৃণাল। তখনো ঠিক ভঙ্গিটি খুঁজে পাচ্ছিলেন না তিনি। ‘বাইশে শ্রাবণ’ (১৯৬০) ছবিটিতে নিজের বক্তব্যকে ইতিহাস ও রাজনীতির মিশ্রণে উপস্থাপনের দিশা পেতে শুরু করেন মৃণাল সেন। তেতাল্লিশের মন্বন্তরের ভেতর এক দম্পতির করুণ দুর্গতি দেখানোর মধ্য দিয়ে নিষ্ঠুর সময়কে ধরতে চেয়েছেন মৃণাল সেন। তিনি মনে করেন, নিষ্ঠুর সময়কে ধরতে নিষ্ঠুর চলচ্চিত্র প্রয়োজন। এই বোধের উদয় হওয়ার পর থেকেই মৃণাল সেনের নির্মাণ ভিন্ন বাঁক নিতে শুরু করে।
মৃণাল সেনের চতুর্থ ছবি ‘পুনশ্চ’ (১৯৬১)। এই ছবিতে নগরে টিকে থাকার লড়াই এবং সেটা যদি হয় একজন নারীর, তবে তার রূপ কেমন হবে, সেই নিরীক্ষার ভেতর দিয়ে হাঁটতে শুরু করেন মৃণাল সেন। নাগরিক নিষ্ঠুরতার ভেতর এক নারীর টিকে থাকার সংগ্রাম, তার ভালোবাসাকে টিকিয়ে রাখার চেষ্টা ‘পুনশ্চ’ ছবির মূল সুর। মৃণাল সেন এই ছবিতে বাসন্তী নামের এক নারীর গল্প বলেছেন, যে বৃদ্ধ বাবা-মায়ের দায়িত্ব শুধু নয়, বেকার ভাইয়ের সংসারের দায়িত্বটাও নিয়ে নেয় হাসিমুখে। একদিকে সংসার, অন্যদিকে প্রেম। প্রেমটাও আবার পেন্ডুলাম, প্রেমিক সুবোধ ও অফিসের বিপত্নীক বস, দুদিকে দুলছে। দোদুল্যমান শুধু বাসন্তী নয়, প্রেমিক সুবোধও তাই, সে কি বাসন্তীর প্রেম পাবে, কি পাবে না! শহরে থাকবে, না ছেড়ে দূরে চলে যাবে? অফিসের বসও বাসন্তীকে নিয়ে দ্বিধান্বিত। বাসন্তীর ভাই শ্রমিক ইউনিয়ন করতে গিয়ে চাকরি হারিয়ে বেকার। সে কি পুরোনো অফিসে গিয়ে ক্ষমা চাইবে, কি চাইবে না? শহরে মুখ বুজে পড়ে থাকবে, না গ্রামে গিয়ে ছোটখাটো স্কুলের চাকরিটা নিয়ে নেবে? ছবির গোটা দ্বিধা ও দোদুল্যমান অবস্থা মৃণাল সেন যখনই চরিত্রদের মুখে ক্লোজ ধরে অনুবাদ করতে চেয়েছেন, তার বেশির ভাগ সময়েই পেছনে রেখেছেন নগর কলকাতাকে। সেখানকার নিত্যদিনের ব্যস্ততা ও শব্দের নৈরাজ্যকে তিনি রেখেছেন ব্যাকড্রপ হিসেবে। আমার মতে তখনো মৃণাল সেন নাগরিক যান্ত্রিক জীবনকে চরিত্রের ভেতর দিয়ে পুরোপুরি তরজমা করার ব্যাপারে দ্বিধাহীন হয়ে ওঠেননি।
এরই ফাঁকে, ষাটের দশকের গোড়ায়, গোটা পৃথিবীতে আছড়ে পড়ছে ফরাসি নবতরঙ্গের ঢেউ। সেই ঢেউ পশ্চিমবঙ্গেও এসে লাগল। মৃণাল সেন বলছেন, “ফরাসি নবতরঙ্গের প্রভাব এ দেশে অনুভূত হচ্ছে। বাতাসে তখন একধরনের উন্মাদনা। পাগলামি এবং সতেজভাব। আমি পরিবর্তনের জন্য এক অপ্রতিরুদ্ধ তাগাদা অনুভব করতে লাগলাম। মনে হচ্ছিল এটাই শ্রেষ্ঠ সময় খুব সহজে, অর্থপূর্ণভাবে বিদ্যমান বাধাকে ডিঙিয়ে যাওয়া যায়, যে বাধাকে মূলধারার চলচ্চিত্র কদাচিৎ ডিঙোতে চায়।”
মৃণাল সেন সেই বাধা ডিঙানোর মন্ত্র রপ্ত করে বানালেন সপ্তম ছবি ‘আকাশ কুসুম’ (১৯৬৫)। এক আধুনিক তরুণের অবয়বে মৃণাল সেন সেখানে আধুনিকতাকেই হাজির করলেন ‘প্রতারক’ হিসেবে। এখানেও পেছনের দৃশ্যপটে রাখলেন শহর কলকাতাকে। তরুণ চরিত্রটির নাম রাখলেন অজয়, অর্থাৎ আধুনিক সময়কে কবজায় আনা বা এড়িয়ে চলা সম্ভব নয়। অজয় নিরুপায় হয়ে নিজেকে ধনী প্রমাণের চেষ্টায় রত, সে যেকোনো মূল্যে বড়লোক হতে চায়, এখন সেটা ধারদেনায় অনভিজ্ঞ হাতে ব্যবসা করেই হোক, আর বন্ধুর পোশাক ও গাড়ি ধার করেই হোক। একদিকে সে প্রেমিকাকে প্রতারিত করছে মিথ্যা বলে, অন্যদিকে ব্যবসায় নিজেও হচ্ছে প্রতারণার শিকার। প্রতারণার প্রতিবাদ করতে গিয়ে শারীরিক লাঞ্ছনার শিকারও হতে হয় অজয়কে। শহুরে আধুনিক সময়টাই যেন প্রতারণার, গা-জোয়ারির, যে যাকে পারে প্রতারিত করে চলেছে, ঠকিয়ে চলেছে।
‘আকাশ-কুসুমে’র ভেতর দিয়েই মৃণাল সেন শহর কলকাতাকে স্পষ্টভাবে চরিত্রের ভেতর দিয়ে পাঠ করার প্রয়াস পেতে শুরু করেন বলে আমার ধারণা। তিনি এই ছবিটি প্রসঙ্গেই বলছেন, “‘আকাশ-কুসুম’-এর সীমানা না ডিঙিয়েই অর্থাৎ কাহিনির আওতার মধ্যে থেকেই কলকাতা শহরের স্বাভাবিক মুখরতাসহ কলকাতাকে চিত্রায়িত করবার চেষ্টা করেছি। কলকাতার সর্বাঙ্গীন ব্যস্ততা, কলকাতার অস্থিরতা এবং তারই সঙ্গে কলকাতার এক মধ্যবিত্ত যুবক-নায়ক ও তার পরিবেশের অব্যবস্থচিত্ততা-আশা-হতাশা-রুক্ষতা-মধ্যবিত্ততা গোটা ছবিতে জাঁকিয়ে বসিয়ে বাহুল্যবর্জিত বর্ণনে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি—যখন যেমন প্রয়োজন বোধ করেছি তেমনি করে।... নাগরিক জীবনের এই বেপরোয়া মেজাজটিকে বাইরে থেকে টেনে আমাকে আনতে হয়নি। আধুনিক জীবনযাত্রার সর্বস্তরে এর চেহারা আমি দেখেছি এবং ক্যামেরা ও শব্দযন্ত্রের ‘বেপরোয়া’ ব্যবহারে তার যথার্থ রূপ চিত্রিত করবার প্রয়াস পেয়েছি।”
যদিও ‘ভুবন সোম’ (১৯৬৯) ছবিতে শহরের প্রেক্ষাপট ছেড়ে গ্রামীণ পরিবেশে ক্যামেরা বসিয়েছিলেন মৃণাল, তারপরও গোটা শহরকে, শহরের বাবু সংস্কৃতিকে তিনি যেন গ্রামের সহজ-সরল মানবিক সম্পর্কের সামনে নগ্ন করে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলেন। রেলের এক বড় কর্মকর্তা গ্রামে গিয়ে পাখি শিকারে মত্ত হন, সেখানে ফুটে ওঠে তার আগ্রাসী মনোভাব, জবরদস্তিমূলক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, কিন্তু অতি সামান্য, নির্মল এক তরুণীর ভাবনার সামনে সেই কর্মকর্তা যেন নিজেকে পুনঃআবিষ্কার করে। শহরে ফিরে সে পাল্টে ফেলে অনেক সিদ্ধান্ত। অর্থাৎ এই ছবিতে গ্রাম প্রভাবিত করছে শহরকে।
শহরকে পেছনে রেখে চরিত্রদের সংকট তুলে ধরতে ধরতে আদতে শহরের নিষ্ঠুর রূপ তুলে ধরেছেন মৃণাল সেন এসব ছবিতে। কিন্তু তাঁর মতো রাজনীতি সচেতন পরিচালক শুধু শহরে আটকে থাকবেন কেন? শহরের আরও গভীর গ্রন্থিতে গিয়ে নিজের রাজনৈতিক বক্তব্যকে সরাসরি হাজির করতে থাকলেন তিনি। কলকাতা ত্রয়ী হিসেবে পরিচিত ‘ইনটারভিউ’ (১৯৭০), ‘কলকাতা ৭১’ (১৯৭২) ও ‘পদাতিক’ (১৯৭৩)—এই তিন ছবিতে শহর হিসেবে কলকাতা এলো বটে, কিন্তু তার সঙ্গে এলো সাম্রাজ্যবাদ, ঔপনিবেশিক জড়তা, জাতীয়তাবাদের উত্থান, নকশাল বাড়ি আন্দোলন, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, সমাজতন্ত্র, বিপ্লবী আন্দোলনের ভুলত্রুটি নিয়ে পর্যালোচনা প্রভৃতি। গল্পের মোড়কে শিল্পকে উপস্থাপন না করে, শিল্পের মাধ্যমে রাজনীতিকে সরাসরি উপস্থাপন করায় কুণ্ঠা বোধ তো করেনইনি, উল্টো বলেছেন, “আমাকে রাজনৈতিক পুস্তিকা লেখক বললেও আমি লজ্জিত নই। আইজেনস্টাইন, বিখ্যাত রুশ চলচ্চিত্রকার, একবার মার্কসের ‘দাস কাপিতালে’র জন্য একটি দৃশ্য তৈরি করেছিলেন, তো সেটা করার মধ্যে কোনো সমস্যা নেই।”
নিজেকে ‘প্রাইভেট মার্কসিস্ট’ বলা মৃণাল সেন এই কলকাতা ত্রয়ীর পর ‘কোরাস’ (১৯৭৪) ছবিতে আরও তীক্ষ্ণ ও শ্লেষের সঙ্গে রাজনীতিকে উপস্থাপন করলেন: রাজ্যের বেকারত্ব, গণমাধ্যমের বেসাতি, নিষ্পেষিত শ্রেণির উত্থানকে তিনি ব্যঙ্গচিত্রের মাধ্যমে, অনেকটা রূপক আকারে চলচ্চিত্রে নিয়ে এলেন। এবং তিনি তত দিনে রাজনৈতিক বক্তব্য দেওয়ার মধ্য দিয়ে তো বটেই, চলচ্চিত্রের আঙ্গিকের দিক দিয়েও সমসাময়িক বাঙালি চলচ্চিত্রকারদের ভেতর স্বতন্ত্র হয়ে উঠলেন।
‘কোরাসে’র পর মৃণাল সেন যেন শহর, রাজনীতি, সমাজকে ডিঙিয়ে পারিবারিক স্তরে এসে সম্পর্কের রসায়নের ভেতর শহর, রাজনীতি ও সমাজকে আবিষ্কারে ব্রতী হলেন। অন্য রকম করে তিনি যোগাযোগ স্থাপন করতে চাইলেন দর্শকের সঙ্গে। মৃণাল সেন বানালেন ‘একদিন প্রতিদিন’ (১৯৭৯)। তিনি বলছেন, “একদিন প্রতিদিন, ১৯৭৯ সালে তৈরি, চলচ্চিত্রকার হিসেবে আমার ক্যারিয়ারে এক নতুন অধ্যায়, এই অধ্যায় কয়েক বছর যাবৎ চলেছে।” ‘একদিন প্রতিদিন’ ছবিতে চিনু নামের যে মেয়েটি একদিন হঠাৎ করে বাসায় ফিরতে দেরি করল, তার পরিবার ও প্রতিবেশীদের ভেতর দিয়ে মৃণাল সেন প্যান্ডোরার বাক্সের মতো খুলে দেখিয়ে দেন সত্তর লাখ লোকের কলকাতা শহর নারীদের জন্য কতটা অনিরাপদ, এই শহরের সংসারগুলো আদতে একেকটি মর্গ, একে অপরের ওপর স্বার্থপরের মতো নির্ভরশীল, শুধু তাই নয়, সংসারের মানুষগুলো কতটা পুরুষতান্ত্রিক ও নিপীড়নমূলক। সে জন্যই সংলাপের ছুতোয় চিনুর ভাইয়ের মুখ দিয়ে বলিয়ে দেন, “লাথি মারি শালার ভদ্রলোকের মুখে”।
‘একদিন প্রতিদিন’ ছবিতে মৃণাল সেন যেমন বলতে চাইলেন কলকাতা শহরের মধ্যবিত্ত পরিবারগুলো জীবনমৃত অবস্থার ভেতর দিয়ে দিনাতিপাত করে, তাদের নিরাপত্তা বলে কিছু নেই। তেমনি ‘আকালের সন্ধানে’ (১৯৮০) তিনি বললেন, মন্বন্তর চলে গেলেও অভাব থেকে যায়, গরিবের ঘরে চিরকালই মন্বন্তর চলতে থাকে। চলচ্চিত্রের ভেতর চলচ্চিত্র নির্মাণের গল্প বলে এই ছবি। তেতাল্লিশের দুর্ভিক্ষ নিয়ে ছবি বানাতে চলচ্চিত্রের একটি শুটিং ইউনিট এসে হাজির হয় গ্রামে। দারিদ্র্য, চোরাচালান, দুর্ভিক্ষপীড়িত সংসারে নারীর আত্মত্যাগ, পুরুষের আহত পৌরুষ এসবই তাদের ছবির সারবস্তু। তবে ইউনিটের লোকজন ধীরে ধীরে আবিষ্কার করতে থাকে, আশি সালে এসেও সেই একই বস্তু ক্রিয়াশীল, একটু ভিন্ন আঙ্গিকে। তেতাল্লিশ, উনষাট, একাত্তরে যে মানবিক বিপর্যয় নেমে এসেছিল এই বাংলার জনপদে, সেগুলো স্থিরচিত্রের মাধ্যমে দেখিয়ে দেন পরিচালক, আর সেই সঙ্গে বুঝিয়ে দেন বিপর্যয় থেকে উত্তরণ ঘটেনি এখনো। বরং নতুন যোগ হয়েছে—চিন্তার ক্ষেত্রে পশ্চাৎপদতা। এই চিন্তার দৈন্যকে কাজে লাগায় একদল স্বার্থান্বেষী মহল, যারা যেকোনো মানবিক ও প্রাকৃতিক দুর্যোগেই লাভবান হয়, আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়। সবকিছু মিলিয়ে ছবিটি তাই সম্পূর্ণ না করেই গ্রাম ছাড়তে হয় শুটিং ইউনিটকে।
‘আকালের সন্ধানে’র ভেতর শহুরে বাবুদের নিয়ে মৃণাল সেন ফেলেছিলেন গ্রামীণ পটভূমিতে। এর পরের ছবিতেই তিনি আবার ফিরে এলেন রূঢ় শহুরে বাস্তবতায়। বানালেন ‘চালচিত্র’ (১৯৮১), এই ছবিতে তিনি প্রশ্ন করলেন ‘শহরে কত উনুন জ্বলে’, এই প্রশ্নের মধ্য দিয়ে মৃণাল সেন মিশিয়ে দেন মানুষের ক্ষুধা, ক্ষোভ ও ক্ষয়িষ্ণু মূল্যবোধকে। মধ্যবিত্ত বা নিম্নমধ্যবিত্ত খাবারের প্রয়োজনে কি না করে। দীপু নামের এক বেকার যুবক নিজের পরিবারের দুঃখ-দারিদ্র-দুর্দশার ভেতর থেকে সত্যিকারের করুণ রসের গল্প অনুসন্ধান করে, সংবাদপত্রের অফিসে বিক্রির জন্য। এর জন্য সে নিজের মায়ের সঙ্গে প্রতিবেশীদের ঝগড়া বাধিয়ে দিতেও কুণ্ঠা বোধ করে না। অপরদিকে, এক ভুয়া জ্যোতিষী বিদেশিদের কাছে নিজের ছলনা বিক্রি করে। এই জ্যোতিষীর সঙ্গে দীপুর খুব একটা পার্থক্য নেই। দুজনেই বিক্রি করে, একজন নিজের দারিদ্র্য, অন্যজন ছলনা। অপরদিকে, পত্রিকার সম্পাদক পরিবেশ সচেতনতা কিংবা সমাজতান্ত্রিক আদর্শকেও বিক্রির বিষয় বলে মনে করেন। পত্রিকায় লোকে যা ‘খায়’, সেটা ছাপানোই তো বিক্রি। শহরের এই চালচিত্র আদতে বুর্জোয়া ও পেটি বুর্জোয়াদের সামনে আয়না ধরা বৈ কিছু নয়।
‘খারিজ’ (১৯৮২) ছবিটিতেও ‘একদিন প্রতিদিন’ বা ‘চালচিত্রে’র মতো মধ্যবিত্তের সংকট এবং কলকাতা শহরের দারিদ্র্য, অসহায়হীনতা ও নির্ভরশীলতার ভিন্নরূপ হাজির করা হয়েছে। মৃণাল সেন ক্রমাগত যেন রাজনৈতিক স্লোগান থেকে সরে এসে এসব ছবির ভেতর দিয়ে রাজনৈতিক প্রশ্ন উত্থাপন করতে চাইছেন। নারীর নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন, সবকিছু বিক্রি করে দেওয়ার মানসিকতাকে প্রশ্ন করছেন, এমনকি শিশুশ্রম নিয়েও প্রশ্ন ছুড়ে দিচ্ছেন। কার দিকে? রাষ্ট্রের দিকে, শহরের মধ্যবিত্ত শ্রেণির দিকে এবং সর্বোপরি মানুষের বিবেকের দিকে। ‘খারিজ’ ছবিতে পালান নামের যে শিশু ‘কাজের ছেলেটি’ শীতের রাতে উষ্ণতার লোভে বায়ুরুদ্ধ রান্নাঘরে ঘুমোতে গিয়ে মারা গেল, সেই মৃত্যুর দায় কে নেবে? ভৃত্যের এই মৃত্যুর দায় মধ্যবিত্ত প্রভু কি নেবে? নাকি উচ্চমধ্যবিত্ত বাড়িঅলা নেবে, তার বাড়ির নকশার কারণে? নাকি রাষ্ট্র নেবে, একটি শিশুর নিরাপদ ভবিষ্যৎ গড়ে দেওয়ার সামর্থ্য অর্জন করে উঠতে পারেনি বলে? ছবির শেষ দৃশ্যে এক বিরাট প্রশ্নবোধক চিহ্ন রেখে দেন মৃণাল সেন। পালানের আত্মীয়-পরিজন তথা গরিব মানুষেরা যখন বাবুদের বাড়িতে আসে, তখন বাবু দাঁড়িয়েছিলেন সিঁড়ির ওপরে, আর নিচের ধাপে দাঁড়িয়ে থাকা পালানের বাবা যখন বলে, বাবু চলি, তখন মনে হতে পারে ক্ষমাই পরম ধর্ম, তবে তাতেই কি সব অন্যায় ও বৈষম্য খারিজ হয়ে যায়?
এরপর মৃণাল সেন আমাদের বলেন এক অন্ধকারের গল্প, যামিনীর গল্প, ‘খন্দহর’ (১৯৮৩) চলচ্চিত্রে। ‘চালচিত্রে’র মতো এই ছবিতেও অন্যের ‘গল্প’ বিক্রি করে দেওয়ার প্রবণতা দেখা যায়। আমরা দেখি দারিদ্র্যপীড়িত, প্রতারিত ও সামাজিক বিধিবিধানে আটকে পড়া এক গ্রামীণ নারীর অবয়ব শেষ পর্যন্ত ঠাঁই পায় ব্যস্ত শহরের এক স্টুডিওর দেয়ালে। যেন সেটি বিজ্ঞাপন হয়ে ঝুলে আছে সেখানে। একজন চিত্রগ্রাহকের কালিয়াতিটাই সেখানে মূখ্য, কিন্তু চিত্রগ্রাহক সুভাষের সঙ্গে সেই যামিনীর যে মানবিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল তা যেন শহরে এসে কর্পূরের মতো উড়ে যায়। সে কেবলই ছবি হয়ে ঝুলে থাকে ফ্রেমের ভেতর। শহরে ফিরে এসে শহুরে বাবুরা গ্রামে সামাজিক নানা বেড়াজালে আটকে থাকা মানুষদের ভুলে যায়, ভুলে যাওয়াটাই স্বাভাবিক। শহরের আবহাওয়াটাই ও রকম, সবকিছু ভুলিয়ে দেয়, মানুষকে করে তোলে বিস্মৃতপরায়ণ। মৃণাল সেন এই ছবিতেও মধ্যবিত্ত শহুরে বাবুদের সমালোচনা জারি রেখেছেন।
তবে এই ছবির পর মধ্যবিত্তের গণ্ডি থেকে বেরিয়ে মৃণাল সেন চোখ রাখলেন সর্বহারা শ্রেণির ওপর। শুধু তা-ই নয়, তিনি রূপকের সহায়তায় ফিরে গেলেন ‘হক’ অর্থাৎ অধিকার কার সেই রাজনৈতিক বা দার্শনিক প্রশ্নে। আমার কাছে মনে হয় রাজনীতি সচেতন, মার্কসবাদী মৃণাল সেনের সবচেয়ে পরিণত কাজ ‘জেনেসিস’ (১৯৮৬), এই ছবিটি তাঁর চিন্তার পরাকাষ্ঠা ছুঁয়েছে ঠিকঠাক। এই চলচ্চিত্রে দেখা যায় এক চাষা ও এক তাঁতিকে, তারা ক্ষরা ও দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ে প্রাণে বাঁচার জন্য ঘুরতে ঘুরতে এক ঊষরভূমিতে এসে হাজির হয়। এরা দুজনে দুজনের সহায় হয়ে ওঠে। চাষা মাটি থেকে কিছু ফলানোর চেষ্টা করে, বহুদূর থেকে পানি বহন করে আনে, আর তাঁতি বস্ত্রখণ্ড তৈরি করে। উলের তৈরি পণ্য কিনে নিয়ে যায় এক বেনিয়া, বদলে তাদের দেয় জীবনধারণের জন্য সামান্য দানাপানি আর তেল। শ্রম দিয়ে যে পণ্য বানায় তাতে তারই হক বেশি, কিন্তু আমরা দেখি বাজারে অধিক মুনাফায় সেই পণ্য বিক্রি করে ব্যবসায়ী। বিষয়টি চাষা ও তাঁতির কাছে ধরা পড়ে যায়। বেকে বসে তারা। এরই মধ্যে এই দুজনের ভেতর আরেক সর্বহারা এসে হাজির হয়—এক নারী। তো এই তিন প্রাণী মিলে শুষ্ক জমিনে ফসল ফলায়। কঠিন পরিশ্রমের ফল পায় তারা। তারই ভেতর নারী-প্রকৃতিতেও দুই পুরুষ আবির্ভূত হয় কৃষক রূপে। ফলবতী হয় নারী। মাটির মতোই। প্রশ্ন ওঠে, তবে অনাগত শিশুটি কার? নারীটি বুঝিয়ে দেয়, মাটি তার, ফলের অধিকারও তারই। এই উত্তর যেন সেই ব্যবসায়ীকে উদ্দেশ্য করেই রচিত। যিনি উল বুনে বস্ত্রখণ্ড বানায়, সেই বস্ত্রের ওপর যেমন অধিকার থাকে তারই বেশি, ব্যবসায়ীর কম; তেমনি যার গর্ভে সন্তান রক্তেমাংসে বেড়ে ওঠে, সেই সন্তান জননীরই বেশি, বীজপবনকারীর কম।
জননী মানে যেমন জন্মদাত্রী, ঠিক তেমনি ‘জেনেসিস’ শব্দটিও সম্পৃক্ত জন্ম বা উৎপত্তির সঙ্গে। যিনি জন্ম দেন, অধিকার তারই বেশি। ‘জেনেসিস’ ছবির ভেতর দিয়ে মৃণাল সেন যে রাজনৈতিক অর্থনীতি ও দার্শনিক প্রতীতির ভেতর দিয়ে নতুন ধরনের জন্মতত্ত্ব হাজির করেন, তা এককথায় অপূর্ব। যদিও সবশেষে দেখা যায় বেনিয়া লোকটিই জয়ী হয়, শঠতা দিয়ে, তারপরও মৃণাল সেনের চিন্তাশীল চলচ্চিত্রটি ক্রিয়াশীল থাকে দর্শকের চিত্তে।
ছবিটি নিয়ে উৎপল দত্তের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য, তিনি বলছেন, “সত্যিই ভারতের সর্বহারা যদি সব ফিউদাল ঐতিহ্যের ভার ছুড়ে দিতে পারতো, মাথা উঁচু করতে পারতো বিশুদ্ধ প্রোলেতারীয় চিন্তার আলোকে তবে ইতিহাসের পথ হত মসৃণ। কিন্তু তা হবার নয়। উৎপাদনী সম্পর্কের মধ্যে যেখানে জোতদার-জমিদার-ভূমিদাস-বন্ডেড লেবার সব বিরাজ করছে সেখানে সর্বহারার চিন্তায় পশ্চাৎপদ সব ধ্যান-ধারণা থাকবে না, তাতো হয় না। তাই ‘জেনেসিস’ ছবির গোড়ায় যে দুই পুরুষকে আমরা দেখেছিলাম যৌথ শ্রমে ঐক্যবদ্ধ, ছবির শেষে দেখি তারা যুক্তিহীন ঘৃণায় পরস্পরকে আঘাত করছে। আর সেই সুযোগে ঢুকে আসে কোম্পানির বাহিনী। শ্রমিকশ্রেণির অনৈক্যের সুযোগ ব্যতীত কবে কোথায় আক্রমণ চালাতে পেরেছে শোষক? মেশিনের তাণ্ডবে ছবি শেষ হয়।”
সর্বহারা, সামন্ত প্রভু, বেনিয়া, এদের ছেড়ে মৃণাল সেন প্রত্যাবর্তন করলেন মধ্যবিত্ত পরিবারে। বানালেন ‘একদিন আচানক’ (১৯৮৯)। এক বৃষ্টিবাদলার দিন, কলকাতা বেনোজলে তলিয়ে একাকার, রাস্তায় মানুষ নাজেহাল, ঠিক সে রকম এক দিনে ইতিহাসের এক অধ্যাপক বাসা থেকে বেরিয়ে আর ফিরে এলেন না। প্রথমে তার সম্পর্কে ধারণা করা হলো, তিনি শেষ বয়সে হয়তো প্রেমের টানে পুরোনো সংসারের মায়া ত্যাগ করেছেন। কিন্তু পরে দেখা গেল, না, ঘটনা সে রকম নয়। এমনটা হতে পারে তিনি জীবনসায়াহ্নে এসে প্রত্যাশা আর প্রাপ্তির হিসাব মেলাতে পারেননি, হতাশাগ্রস্ত হয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেছেন। আবার দুর্ঘটনার নগরীতে কোনো বিপদেও পড়তে পারেন, তবে সে রকম হলে থানা-পুলিশ থেকে খবর আসত। বয়স্ক মানুষটা যেন কর্পূরের মতো উবে গেলেন। কোথায় গেলেন তা আর জানা যায় না। তার এই অন্তর্ধানকে কেন্দ্র করেই মধ্যবিত্ত পরিবারটিতে উঁকি দিয়ে যায় নানাবিধ কঠিন সত্য। স্ত্রী ভাবে স্বামী শেষ বয়সে হয়তো কমবয়সী প্রেমিকার কাছে চলে গেছেন। বড় মেয়ে ভাবে বাবা হয়তো সংসার নিয়ে হতাশ তাই তাদের ছেড়ে দূরে চলে গেছেন। তিনি হয়তো আর দশটা মানুষের মতোই সাধারণ ছিলেন। ছেলে ভাবে, যেখানেই যাক না কেন, ব্যাংকের জমানো টাকাপয়সার কী হবে, সেগুলো কবে তোলা যাবে। তাদের কথা কি কখনো ভেবেছেন বাবা? ছোট মেয়ে ভাবে অহংকারী বলেই হয়তো বাবা তাদের পরিত্যাগ করেছেন। কিন্তু অধ্যাপক বাবার কথা আমরা সরাসরি শুনতে পারি না। স্ত্রীর উদ্ধৃতির ভেতর দিয়ে জানতে পারি, গৃহত্যাগী হওয়ার আগে একদিন তিনি বলেছিলেন, সবচেয়ে বড় দুঃখ কি জানো, মানুষের জীবন একটাই। অর্থাৎ হতে পারে, “এই জীবন লইয়া কী করিব” বোধ থেকে হয়তো তিনি কোনো নির্বাণ লাভ করেছিলেন। তা নিয়েও আমরা নিশ্চিত নই। তবে অধ্যাপকের সংসারত্যাগী হওয়ার পেছনে একধরনের অভিমান, অপ্রাপ্তির বেদনা এবং সর্বোপরী নাস্তিবাদ কাজ করতে পারে। ছবিটি মুক্তির পর ডেরেক মেলকমের মতো চিত্র সমালোচক প্রশ্ন তুলেছিলেন, এই চলচ্চিত্র কি আত্মজৈবনিক? প্রত্যুত্তরে মৃণাল সেন যদিও ঠাট্টা করে বলেছিলেন, এই কাহিনি আপনাদেরও। কিন্তু পরে ঠিকই এক সাক্ষাৎকারে মৃণাল সেন আক্ষেপ করে বলেছিলেন: আবার যদি শুরু থেকে শুরু করতে পারতাম! যত খ্যাতিই আসুক না কেন, নিজের সীমাবদ্ধতা নিয়ে সচেতন মানুষ মাঝেমধ্যে মুষড়ে পড়েন বটে। হতে পারে ইতিহাসের অধ্যাপক আদতে মৃণাল সেন। তবে এটুকু বলা যায়, মৃণাল সেনের এই আত্মানুসন্ধানের অভিযাত্রা একেবারেই ভিন্ন। তিনি সেই ষাট কিংবা সত্তর দশকের মৃণাল সেন আর নেই।
পরবর্তী ‘অন্তরীণ’ (১৯৯৩) ও ‘আমার ভুবন’ (২০০২) ছবিতেও মৃণাল সেন রাজনীতি নয়, মানবিক সম্পর্কের ক্যালাইডোস্কোপ তৈরি করতে চেয়েছেন। ‘অন্তরীণে’ অচেনা নারী-পুরুষের পূর্বপরিচয়হীন সম্পর্কের অভিঘাত রচনা করেছেন মৃণাল। ‘আমার ভুবনে’ও তাই, তবে ওখানে ত্রিভুজ আছে। এই ছবিটি শুরুই হয় গুলির শব্দ দিয়ে, দরিদ্র মানুষের উপস্থিতি দিয়ে। এরপর লিখে দেওয়া হয়: পৃথিবী ভাঙছে, পুড়ছে, ছিন্নভিন্ন হচ্ছে, তবু মানুষ বেঁচেবর্তে থাকে, মমত্বে, ভালোবাসায়, সহমর্মিতায়। মৃণাল সেন শেষের এই ছবিটি দিয়ে যেন বলতে চাইলেন দুনিয়ায় শ্রেণিসংগ্রাম আছে, যুদ্ধ-বিগ্রহ আছে, নিচুতা-শঠতা আছে, কিন্তু সে সকল কিছু ছাপিয়ে ভালোবাসা, মমতা, সহমর্মিতা অর্থাৎ মানবিক গুণাবলিও আছে। ওটাই মানুষের মূল পুঁজি। নয়তো মানবসভ্যতা পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে যেত।
মৃণাল সেন বলছেন, “যখন আমি পেছন ফিরে তাকাই, তখন অভিজ্ঞতা ও নিরীক্ষা, ব্যর্থতা ও ত্রুটি এবং সাফল্যের আলোকে বুঝতে পারি, আমি আমার মাধ্যমকে, নিজেকে বোঝার চেষ্টা করেছি। আমি নিরন্তর পরিবর্তনের ভেতর দিয়ে গিয়েছি। নিজের সিদ্ধান্তকে বারবার বদলেছি। সেটাই করে চলেছি। এমনকি এখনো।”
মৃণাল সেন পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণ করেছেন ২৮টি। এই ছবিগুলো দেখলে প্রকৃত অর্থেই মনে হয় মৃণাল সেন বারবার নিজেকে ভেঙেছেন, নতুন কিছু গড়ার জন্য। তিনি সত্যকে উপস্থাপন করতে চাননি, কিন্তু সত্যকে ধরার চেষ্টা করেছেন, আর সে কারণেই তাঁর ছবিতে নিরন্তর পরিবর্তনের ছাপ পাওয়া যায়। মৃণাল সেনের চিরপ্রস্থান ঘটে ২০১৮ সালের ৩০ ডিসেম্বর। ২০২৩ তাঁর জন্মশতবর্ষ পূরণের বর্ষ। ভারত উপমহাদেশের শুধু নয়, গোটা চলচ্চিত্র বিশ্বেই মৃণাল সেন এক গুরুত্বপূর্ণ চিন্তাবিদ। তাঁকে সশ্রদ্ধ সালাম।
দোহাই
১. মৃণাল সেন, মোন্তাজ: লাইফ, পলিটিকস, সিনেমা, (ক্যালকাটা: সিগাল বুকস, ২০১৮)
২. জন ডব্লিউ হুড, চেজিং দ্য ট্রুথ: দ্য ফিল্মস অব মৃণাল সেন, (ক্যালকাটা: সিগাল বুকস, ১৯৯৩)
৩. সোমা এ. চ্যাটার্জি, মৃণাল সেন: দ্য সারভাইবর, (নিউ দিল্লি: রুপা অ্যান্ড কোং, ২০০৩)
৪. বিভাস মুখোপাধ্যায় (সম্পাদিত), চলচ্চিত্র চর্চা (প্রসঙ্গ মৃণাল: বিশ্লেষণ মূল্যায়ন অন্বেষণ), (কলকাতা: ২০১৬)
৫. বিভাস মুখোপাধ্যায় (সম্পাদিত), চলচ্চিত্র চর্চা (প্রসঙ্গ: মৃণাল সেন: চলচ্চিত্র সমালোচনা), (কলকাতা: ২০১৭)


-20230513162529.jpg)