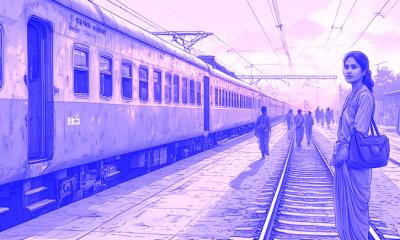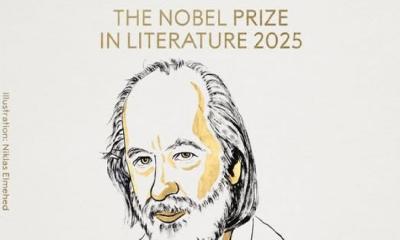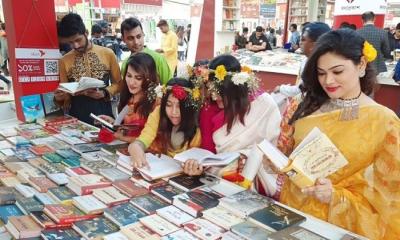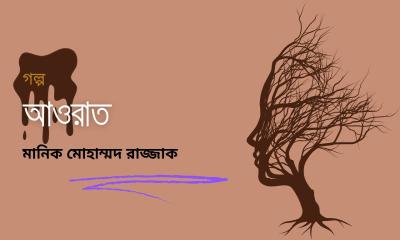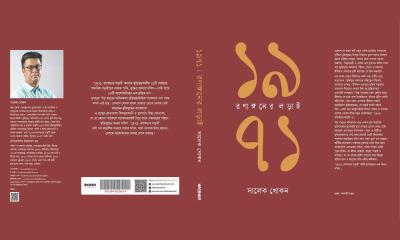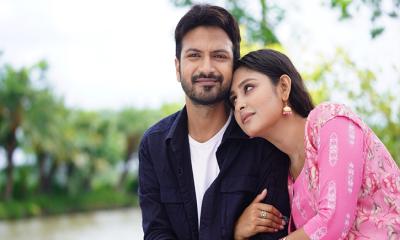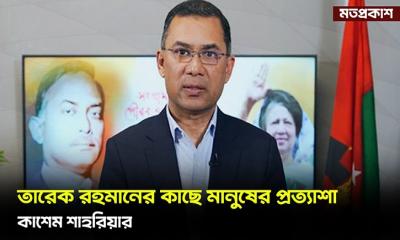যদি বলা হয় ‘আমার সোনার বাংলা’র পর বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি-গাওয়া গান কোনটি, তাহলে আমি মোটামুটি নিশ্চিত, তোমরা দুটো গানের কথা বলবে, ‘আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো’ কিংবা ‘এসো হে বৈশাখ’। তবে আমার কেন জানি মনে হয়, ইদানীং দেশজুড়ে একুশে ফেব্রুয়ারির প্রভাতফেরির চর্চায় বেশ খানিকটা ভাটা পড়াতে ‘এসো হে বৈশাখ’ গানটিই সম্ভবত সেই স্থান দখল করবে। কারণ, তোমরা জানো, রবীন্দ্রনাথের এই গানটি গাওয়া ছাড়া বাংলা নববর্ষ বরণের কথা আমরা কল্পনাই করতে পারি না। আর যত দিন যাচ্ছে, বাংলাদেশের সর্বত্র; শহরে-বন্দরে, গ্রামে-গঞ্জে, অফিসে-আদালতে-বিদ্যালয়ে সব জায়গায় সবাই মিলে এই গান গেয়ে বাংলা বছরের প্রথম দিন তথা পয়লা বৈশাখকে বরণ করে নেওয়ার চল বেড়েই চলেছে। আমার আজকের ‘শিল্পের সিন্দুক’ পর্বে আমি তাই এই গান সম্পর্কেই কিছু কথা তোমাদের শোনাতে চাই, ছোট্ট বন্ধুরা।
আগেই বলেছি গানটি আমাদের প্রিয় কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা। তবে গানটি তিনি ঠিক পয়লা বৈশাখকে নিয়েই যে লিখেছেন, তা কিন্তু নয়, এটি সামগ্রিকভাবে বাংলা বছরের প্রথম মাস বৈশাখকে ঘিরেই লেখা। তোমরা জানো, রবীন্দ্রনাথ নিজেও জন্মেছিলেন এই বৈশাখ মাসেই, পঁচিশে বৈশাখে। তাই এই মাসটির প্রতি তাঁর ছিল এক বিশেষ দুর্বলতা, যে কারণে বৈশাখ নিয়ে তিনি শুধু এই গানটিই নয়, আরও বেশ কয়েকটি গান রচনা করেছিলেন, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য, ‘তোমার বৈশাখে ছিল প্রখর রৌদ্রজ্বালা’,‘বৈশাখ হে মৌনী তাপস’, ‘ঐ বুঝি কালবৈশাখী’, ‘বৈশাখের এই ভোরের হাওয়া’ ইত্যাদি। তবে এই গানটিকে কেউ কেউ কবিতা হিসেবেও দেখে থাকেন, কেননা আদিতে এর একটি নামও ছিল, ‘বৈশাখ আবাহন’, গানের ক্ষেত্রে সচরাচর যা থাকে না। শান্তিনিকেতনে বসেই এটি তিনি রচনা করেছিলেন ১৩৩৩ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন তথা ১৯২৭ সালের মার্চ মাসে। বস্তুত ১৯৬৭ সালে ‘ছায়ানট’ কর্তৃক আয়োজিত রমনার বটমূলের প্রথম বর্ষবরণ অনুষ্ঠানের মূল গান হিসেবে এই গানটি গাওয়ার পর থেকেই ধীরে ধীরে এটিই হয়ে ওঠে পয়লা বৈশাখ তথা নতুন বছরকে বরণ করে নেওয়ার অনিবার্য ও অপরিহার্য এক সর্বজনীন সংগীত। তা ছাড়া এই গানের বাণীর মধ্যেও এমন এক আবেগ, আবেদন ও অঙ্গীকার রয়েছে যে তা সবাইকে সমানভাবে স্পর্শ করে, একধরনের উল্লাস ও উদ্দীপনার জন্ম দেয় শ্রোতা ও গায়ক উভয়ের মনে। এর আর-একটি কারণ সম্ভবত এর সহজ সাবলীল সুরের কাঠামো, যা কিনা রচিত হয়েছিল জনপ্রিয় রাগ ইমনকল্যাণ ও প্রচলিত তাল কাহারবার ছন্দ-লয়কে আশ্রয় করে।
‘ছায়ানট’-এর কথা যদি উঠলই তাহলে বলি, শুধু এই গানটিকে জনপ্রিয় করার পেছনেই নয়, সামগ্রিকভাবেই বাংলা নববর্ষ বরণের যে উদার ও সুন্দর সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে বাংলাদেশে, তার পেছনেও রমনার বটমূলে ‘ছায়ানট’ আয়োজিত এই অনিন্দ্যসুন্দর অনুষ্ঠানটির ভূমিকা বিশাল। তোমরা জেনে অবাক হবে, সেই যে ১৯৬৭ সালের পয়লা বৈশাখে তারা এই অনন্য অনুষ্ঠানটির সূচনা করেছিল, তারপর গত ৫৫ বছরে কেবল ১৯৭১ সাল আর এই সাম্প্রতিককালের করোনা মহামারির দুটো বছর বাদ দিলে একবারের জন্যও তা বন্ধ থাকেনি। যত ঝড়-ঝাপটা, বাধা-বিপত্তিই আসুক না কেন, তারা তা উপেক্ষা ও অতিক্রম করে এই অনুষ্ঠান চালিয়ে গেছে বছরের পর বছর। এমনকি ২০০১ সালে এই অনুষ্ঠানে ধর্মীয় মৌলবাদী ও জঙ্গিগোষ্ঠীর নৃশংস, বীভৎস বোমা হামলার পরেও তারা ভয় পেয়ে পিছিয়ে আসেনি এর আয়োজন থেকে। আর এভাবেই বাংলা বর্ষবরণ তথা পয়লা বৈশাখ উদ্যাপনের আয়োজনটি ক্রমে হয়ে উঠেছে আমাদের দেশের সবচেয়ে বড় মিলনমেলা– জাতি-ধর্ম-বর্ণ-গোত্রনির্বিশেষে একমাত্র সত্যিকার সেক্যুলার, অসাম্প্রদায়িক ও সর্বজনীন উৎসব; যেখানে হিন্দু-মুসলিম-বৌদ্ধ-খ্রিষ্টান-পাহাড়ি জনগোষ্ঠী, ধনী-গরিব, নারী-পুরুষ,নবীন-প্রবীণ সবাই কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে একসঙ্গে আনন্দ ও মিলনের গান গাইতে পারে।
তো আমাদের এই অপরূপ পয়লা বৈশাখ উদ্যাপনের উৎসবটি এক নতুন মাত্রা পায় আরও একটি চমৎকার সাংস্কৃতিক সংঘটনার সুবাদে, যার নাম ‘মঙ্গল শোভাযাত্রা’। ১৯৮৫ সালে প্রথমবারের মতো যশোরের ‘চারুপীঠ’ শিল্প বিদ্যালয়ের উদ্যোগে, সর্বস্তরের সংস্কৃতিকর্মীদের অংশগ্রহণে পয়লা বৈশাখের সকালে একটি বর্ণিল আনন্দ শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়েছিল। পরে ১৯৮৯ সালের বাংলা নববর্ষের প্রথম সকালে ঢাকা চারুকলা ইনস্টিটিউটের শিক্ষার্থীরা ‘মঙ্গল শোভাযাত্রা’ নাম দিয়ে আরও বড় আকারে চমৎকার, বর্ণাঢ্য একটি মিছিল বার করে তাদের ক্যাম্পাস থেকে। এই শোভাযাত্রায় তারা গ্রামবাংলার নানান লোকজ মোটিফ যেমন লক্ষ্মীপ্যাঁচা, পাখি, মাছ, হাতি, বাঘ, সাপ, কুমির জাতীয় প্রাণীর প্রতিমূর্তি; নানাবিধ রঙিন মুখোশ; কুলা, হাতপাখা, লাঙল; বিচিত্র নকশার আলপনা, সরাচিত্র ইত্যাদি বহন করে যাবতীয় অমঙ্গল ও অশুভের বিনাশ কামনা আর কল্যাণ ও সুন্দরের বিজয় চেয়ে পুরো ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ করে। এটি দ্রুতই সর্বস্তরের মানুষের মনোযোগ আকর্ষণ করে এবং দিন দিন তা খুবই জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। প্রতিবছর এতে যুক্ত হয় নতুন নতুন নকশা ও প্রতীক, ক্রমেই তা আকারে বিশাল এবং রঙে ও রেখায় অত্যন্ত আকর্ষণীয় একটি সাংস্কৃতিক ঘটনা হয়ে ওঠে বাংলা বর্ষবরণের। তার জনপ্রিয়তা ও সুনাম দেশের সীমানা ছাড়িয়ে বিদেশের মাটি ও প্রচারমাধ্যমেও ছড়িয়ে পড়তে থাকে। এবং এভাবেই একদিন, আরও নির্দিষ্ট করে বলতে গেলে ২০১৬ সালের নভেম্বর মাসে, জাতিসংঘের শিক্ষা ও সংস্কৃতিবিষয়ক প্রতিষ্ঠান ‘ইউনেসকো’র কাছ থেকে আমাদের এই ‘মঙ্গল শোভাযাত্রা’ বিশ্বের উল্লেখযোগ্য একটি অস্পর্শসম্ভব (Intangible) সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের স্বীকৃতি লাভ করে।
সবশেষে বলি, পৃথিবীতে খুব কম দেশ, জাতি কিংবা সংস্কৃতিরই পয়লা বৈশাখ বা বাংলা বর্ষবরণ অনুষ্ঠানের মতো এ রকম গর্ব করার মতো সুন্দর, সর্বজনীন ও মহৎ একটি উৎসব রয়েছে। এই উৎসবটি বাঙালি ও স্বাধীন, সার্বভৌম বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে আমাদের যতটা আপ্লুত ও আনন্দিত, ঐক্যবদ্ধ ও উজ্জীবিত করে; যতটা আমাদের ইতিহাস, ঐতিহ্য, মাটি ও শিকড়ের কাছাকাছি নিয়ে যায়; আমাদের ভাষা, শিল্প ও সংস্কৃতিকে চিনতে, বুঝতে ও ভালোবাসতে শেখায়, তেমনটি আর কোনো কিছুতেই দেখি না। তাই তোমাদের কাছে আমার একান্ত অনুরোধ, কোনো কুৎসা কিংবা অপপ্রচারেই বিভ্রান্ত হয়ে তোমরা আমাদের এই পরম গর্বের ধন, আমাদের এই হাতের লক্ষ্মীকে যেন কখনো পায়ে ঠেলতে যেয়ো না। বরং সর্বদা সচেষ্ট থেকো এই অনুষ্ঠান, এই উৎসব ও এই সংগীতের যে মর্মবাণী তাকে হৃদয়ে ধারণ করতে, তাকে তোমাদের মননে ও চেতনায় লালন করতে। আমি এই কথাটি বলেই আমার এই লেখার ইতি টানছি এখানে। তবে তার আগে পুরো এই গান কিংবা কবিতাটিকে লেখার নিচে উদ্ধৃত করে দিচ্ছি, এই প্রত্যাশায় যে তোমরা সেটি মন দিয়ে পাঠ করবে পুনরায়, তার কথাগুলো বোঝার চেষ্টা করবে সাধ্যমতো, এবং তোমাদের কাজে ও কর্মে, জীবনে ও যাপনে তার প্রয়োগ ও প্রতিফলন ঘটাবে যতটা সম্ভব। বাংলা নতুন বছর ১৪৩০-এর শুভলগ্নে তাই প্রার্থনা: তোমাদের সবার প্রাত্যহিক জীবন থেকে আজ, এই মুহূর্তেই ‘মুছে যাক গ্লানি, ঘুচে যাক জরা’ এবং এই বিশুদ্ধ বৈশাখের প্রখর রৌদ্রতাপ ও সূর্যকিরণের অপূর্ব ‘অগ্নিস্নানে শুচি হোক ধরা।’
বৈশাখ আবাহন
এসো, এসো, এসো হে বৈশাখ।
তাপসনিশ্বাসবায়ে মুমূর্ষুরে দাও উড়ায়ে,
বৎসরের আবর্জনা দূর হয়ে যাক॥
যাক পুরাতন স্মৃতি, যাক ভুলে-যাওয়া গীতি,
অশ্রুবাষ্প সুদূরে মিলাক॥
মুছে যাক গ্লানি, ঘুচে যাক জরা,
অগ্নিস্নানে শুচি হোক ধরা।
রসের আবেশরাশি শুষ্ক করি দাও আসি,
আনো আনো আনো তব প্রলয়ের শাঁখ।
মায়ার কুজ্ঝটিজাল যাক দূরে যাক॥