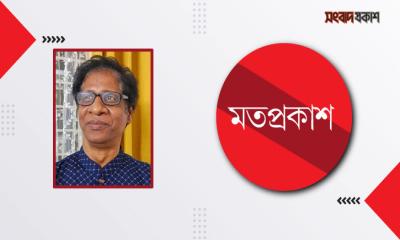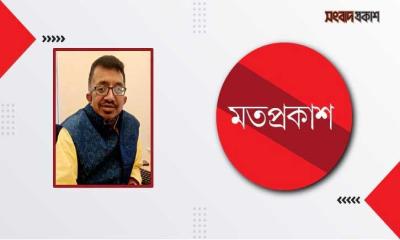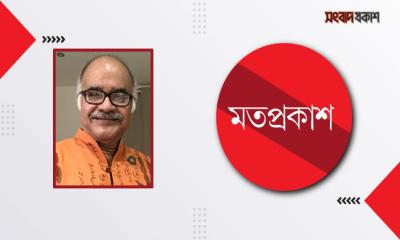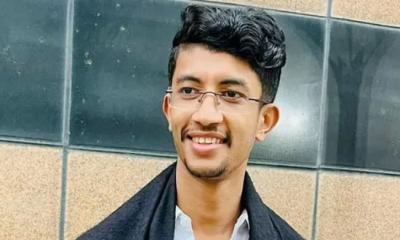রাজনীতি মানুষের নাগরিক অধিকার। প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক, সচেতন ও সুস্থ নাগরিক রাজনীতি করবেন, এটাই স্বাভাবিক। বিভিন্ন ইস্যুতে আন্দোলন-সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হলে একটি শক্তিশালী প্ল্যাটফর্ম দরকার। রাজনৈতিক সংগঠন সেই শক্তিশালী প্ল্যাটফর্মগুলোর মধ্যে অন্যতম। আর এই রাজনীতির একটি প্রধান অঙ্গ ছাত্র রাজনীতি। একটি অভিন্ন উদ্দেশ্য ও আদর্শে লালিত একদল ছাত্র যখন কোনো আন্দোলনে নেতৃত্ব দেয়, তখন শাসকশ্রেণি পর্যন্ত বিষয়টিকে আমলে নিতে বাধ্য হয়। অন্য সাধারণ পেশাজীবী সংগঠনগুলোর দাবি অগ্রাহ্য করে, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে দিয়ে পিটিয়ে এসব সংগঠনের নেতাদের ছত্রভঙ্গ করা যায় সহজে।
কিন্তু আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী দিয়ে ছাত্রদের আন্দোলন দমানো যায় না। বিশেষ করে রাজনৈতিকভাবে ছাত্ররা অনেক বেশি সুসংগঠিত থাকেন, তাই তাদের সংকল্প থেকে হটানো সম্ভব হয় না। ছাত্ররাজনীতি বন্ধ হলে তারা বিভিন্ন জাতীয় ইস্যুতে হয়তো সংগঠিত হবে, কিন্তু সুসংগঠিত হওয়ার মনোবল তাদের থাকবে না। ফলে সহজেই তাদের ছত্রভঙ্গ করা যাবে। এছাড়া যেকোনো ছাত্রকে জঙ্গি-সন্ত্রাসী অপবাদ দিয়ে স্বার্থান্বেষী মহল হয়রানি করার সুযোগ নিতে পারবে।
বছর কয়েক আগে, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) শিক্ষার্থী আবরার হত্যাকাণ্ডের পর একটি মহল থেকে ছাত্ররাজনীতি বন্ধের দাবি তুলেছিল। ওই মহলের পাশাপাশি বুয়েট শিক্ষার্থীরাও তাদের ক্যাম্পাসে ছাত্ররাজনীতি বন্ধের দাবি জানিয়ে আসছিলেন। তাদের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে ২০১৯ সালের ১১ অক্টোবর বুয়েটে ছাত্ররাজনীতি বন্ধের ঘোষণা দিয়েছিলেন তৎকালীন ভিসি সাইফুল ইসলাম। যারা ছাত্ররাজনীতির বিপক্ষে বলছেন, তাদের দাবি হলো—শিক্ষার্থীরা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে জ্ঞান অর্জন করবেন, জাতীয় রাজনীতির লেজুড়বৃত্তি করবেন। শিক্ষার্থীরা রাজনৈতিক দলগুলোর লেজুড় সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত হওয়ায় তাদের মধ্যে আধিপত্য বিস্তারের প্রতিযোগিতা শুরু হবে। আর এই প্রতিযোগিতা একসময় প্রতিহিংসায় রূপ নেবে।
রাজনীতিবিমুখ এই মহলটির মতে, ১৯৯০-এর স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনের পর ছাত্ররাজনীতির প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে। এখন শিক্ষার্থীরা যে রাজনীতি করছেন, তা কেবল চাঁদাবাজি-টেন্ডারবাজি ও র্যাগিংয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। ছাত্ররাজনীতি জাতীয় জীবনে কোনো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারছে না। উপরন্তু সাধারণ শিক্ষার্থীদের মত-প্রকাশ ও অধিকার আদায়ে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াচ্ছে। শিক্ষার্থীরা কোনো যৌক্তিক আন্দোলন-সংগ্রামে নামলে ক্ষমতাসীন দলের ছাত্রসংগঠনের নেতাকর্মীরা সেখানে বাধা হয়ে দাঁড়ান। সাধারণ শিক্ষার্থীদের সঙ্গে তারা একাত্মতা পোষণ না করে উল্টো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেন। চালান হামলাও। এছাড়া, তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে তারা ক্যাম্পাসে কথা-কাটাকাটি থেকে শুরু করে হত্যাকাণ্ড পর্যন্ত চালান।
ছাত্র রাজনীতিবিরোধী মহলটির মতে, ছাত্রনেতারা চাঁদাবাজি-টেন্ডারবাজিতেও অপ্রতিরোধ্য। সম্প্রতি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের কাছ থেকে বিপুল অংকের চাঁদা দাবির ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই গত ৫ অক্টোবর বুয়েটে ছাত্রলীগ নেতারা বিশ্ববিদ্যালয়টির শিক্ষার্থী আবরারকে পিটিয়ে হত্যা করে। এর পরপরই ছাত্ররাজনীতি বন্ধের দাবিতে বিশেষ মহলটি সোচ্চার হয়ে উঠেছে।
এদিকে, রাজনীতি সচেতন মহলের মতে, ছাত্ররাজনীতি বন্ধের দাবি সম্পূর্ণ অযৌক্তিক-অনভিপ্রেত-অপরিণামদর্শী। ছাত্ররাজনীতি বন্ধের দাবিকে তারা গোষ্ঠীবিশেষের ষড়যন্ত্র হিসেবেই দেখছেন। এই পক্ষের মতে, ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন, ৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান, ৯০ সালের স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলন, ২০১৮ সালের নিরাপদ সড়ক আন্দোলন ও কোটা সংস্কার আন্দোলনে চালকের ভূমিকায় ছিলেন ছাত্ররাই। তারাই জাতির প্রতিটি ক্রান্তিলগ্নে ত্রাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন। তাদের আন্দোলনের সুফল ভোগ করছে পুরো জাতি। অথচ সেই ত্রাণকর্তাদের আন্দোলন-সংগ্রামের ফলভোগীরাই এখন ছাত্ররাজনীতি বন্ধের দাবি তুলছেন। এই দাবির মধ্যে জাতিকে রাজনৈতিক নেতৃত্বশূন্য করে দেওয়ার নীলনকশা দেখছেন সচেতন মহল। তাদের মতে, একটি আদর্শ রাষ্ট্রের একজন সুনাগরিকের অন্যতম প্রধান গুণ হচ্ছে—রাজনীতি সচেতনতা। রাজনৈতিক জ্ঞানশূন্য একজন নাগরিক যেমন তার অধিকার আদায়ে সফল হতে পারেন না, তেমনি বুঝতে পারেন না দেশ-জাতির প্রতি তার দায়-দায়িত্ব সম্পর্কেও।
ছাত্রজীবন হলো জীবনের ভিত্তি গড়ার সময়। এই সময়েই প্রত্যেক নাগরিক নিজেকে পরবর্তী জীবনের জন্য গড়ে তোলেন। এ কারণেই শিক্ষার্থীদেরই বলা হয়, আগামী দিনের কর্ণধার। অথচ এই কর্ণধারদের জীবনের প্রস্তুতিপর্বেই রাজনীতিবিমুখ করে রাখার দাবি তোলা হচ্ছে। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্ররাজনীতি বন্ধের দাবি যেখানে তোলা হচ্ছে, সেখানে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় ছাত্র-রাজনীতির যৌক্তিকতা কতটুকু? এই প্রশ্নের উত্তর এক কথায় দেওয়া সম্ভব নয়। কারণ প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সঙ্গে কেবল জ্ঞানার্জনের সম্পর্ক যুক্ত নয়, এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে মালিকপক্ষের ব্যবসায়িক মনোবৃত্তি, রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের অপচেষ্টাও। ফলে যারা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন, তারা শিক্ষার্থীদের জ্ঞানার্জনের পথ সুগম করার চেয়ে নিজেদের অর্থ উপার্জন ও সমাজে প্রভাব-প্রতিপত্তি অর্জনের চেষ্টা করেন বেশি। এমনকি কোনো কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যানসহ একাধিক সদস্যের বিরুদ্ধে কোটি কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগও উঠেছে। এসব বিষয় বিবেচনায় বেশ কিছু কারণে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-রাজনীতি জরুরি বলে মনে করি। কারণগুলো হলো—
১। ট্রাস্টি-ভিসি-প্রোভিসির স্বেচ্ছাচারিতা বন্ধে
২। অতিরিক্ত অর্থ আদায় বন্ধে
৩। অর্থ-আত্মসাৎ ও অনিয়ম-দুর্নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে
৪। দেশের ভবিষ্যৎ কর্ণধার হিসেবে গড়ে উঠতে
৫। মুক্তিযুদ্ধ-দেশের স্বাধীনতাবিরোধী কর্মকাণ্ড বন্ধে
অধিকাংশ প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগপ্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতার অভাব আছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যানসহ সদস্যদের পছন্দের লোকজনকে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেওয়ার অভিযোগ আছে। অনাত্মীয় শিক্ষকদের বছরের পর বছর খণ্ডকালীন শিক্ষক হিসেবে খাটানো হয়। মাসিক ভিত্তিতে বেতন-ভাতা না দিয়ে সেমিস্টারভিত্তিক সম্মানী দেওয়া হয়। স্থায়ী শিক্ষকরা যেখানে একেক সেমিস্টারে তিন-চারটি কোর্স পান, সেখানে ট্রাস্টি বোর্ডের অনাত্মীয় খণ্ডকালীন শিক্ষকরা পান মাত্র একটি কোর্স। চার মাস মেয়াদি সেমিস্টার শেষে টাকা পান মাত্র ৩০ হাজার থেকে ৪০ হাজার টাকা। খুব কম পরিমাণ শিক্ষক আছেন, যারা একেক সেমিস্টারে ৫০/৫২ হাজার টাকা পান। চার মাস মেয়াদি একেকটি সেমিস্টারের জন্য যিনি ৪০ হাজার টাকা সম্মানী পান, তার মাসিক আয় যা দাঁড়ায় তা দিয়ে বাসা ভাড়া দেওয়া দূরে থাক, আসা-যাওয়ার পরিবহণ ভাড়াও হয় না। তবু তারা শিক্ষকতার মতো মহান পেশায় দিনের পর দিন খেটে যান। চাকরি হারানোর ভয়ে ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যানসহ সদস্য কিংবা ভিসি, কিংবা ডিন কিংবা বিভাগীয় চেয়ারম্যানের ভয়ে মুখ খুলতে সাহস পান না। বছরের পর বছর স্বেচ্ছাশ্রম দিয়েও চাকরি স্থায়ীকরণের দাবি জানাতে পারেন না, পাছে খণ্ডকালীন চাকরিটাও যদি চলে যায়! আর এরই সুযোগে ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্যরা এতই উদগ্র ও উগ্র হয়ে ওঠেন যে, তারা ধরাকে সারা জ্ঞান করেন। মালিক পক্ষের এ ধরনের স্বেচ্ছাচারিতা বন্ধেও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-রাজনীতি জরুরি। ছাত্র-রাজনীতি শুরু হলে ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান, বা সদস্য, ভিসি, প্রো-ভিসি, ডিন বা বিভাগীয় চেয়ারম্যানরা শিক্ষকদের ওপর অন্যায় আচরণ করতে পারবেন না। কারণ, তখন স্থায়ী শিক্ষক-খণ্ডকালীন শিক্ষকদের ওপর বৈষম্য দেখা দিলে, সাধারণত দ্বিতীয় পক্ষ অসন্তোষ প্রকাশ করবে। সেই অসন্তোষের আঁচ-প্রভাব গিয়ে পড়বে পাঠদানের ওপর। তখন রাজনীতি সচেতন ছাত্ররা এই অনিয়ম-স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবেন। কর্তৃপক্ষকে বাধ্য করবেন জবাবদিহিতায়।
একথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে, দেশে বিভিন্ন সময়ে মানুষের অধিকার আদায়ের সংগ্রামে মাঠে নেমেছে ছাত্রসমাজ। অন্যান্য পেশাজীবী সংগঠন কেবল যেখানে নিজেদের স্বার্থ দেখে, যেখানে এক পেশার ব্যক্তিরা অন্য পেশাজীবীদের প্রতিপক্ষের কাতারে দাঁড় করিয়েও দেয়; সেখানে ছাত্রসমাজ কখনোই কেবল নিজেদের সুবিধা আদায়ের চিন্তা করে না। তারা যখন আন্দোলনে নামে, তখন জাতীয় স্বার্থকেই প্রাধান্য দেয়। সেখানে কারও প্রতি তাদের পক্ষপাত থাকে না। তারা কেবল একটি ন্যায্য দাবি আদায়ের লক্ষ্যে অবিচল থাকে। তাদের সেই অটল অবস্থা সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার প্রভাবশালীদের জন্য বেশ অস্বস্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।
বিভিন্ন প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় দেখা যায়, আসন-সংখ্যার চেয়ে বেশি শিক্ষার্থী ভর্তি করানো হয়। পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে ইউজিসি নির্ধারিত ফি’র চেয়ে বেশি অর্থ আদায় করা হয়। এছাড়া, নিয়মিত বেতন-ফি দিয়ে ক্লাস করাসহ পরীক্ষা থেকে নতুন বিপাকে পড়তে হয় শিক্ষার্থীদের। তারা অনার্স-মাস্টার্সের সনদ সংগ্রহ করতে গেলে তাদের কাছ থেকে ৮ থেকে ১২ হাজার টাকা পর্যন্ত আদায় করা হয়। প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় ছাত্র-রাজনীতি না থাকায় শিক্ষার্থীরা অভিন্ন স্বার্থে ঐক্যবদ্ধ হতে পারে না। তারা থাকে পরস্পরের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন। ফলে এসব অর্থ আদায়ের বিরুদ্ধে জোরালো প্রতিবাদ জানানোর সাহস ও ইচ্ছা; কোনোটাই তাদের থাকে না। কিন্তু প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় যদি ছাত্র-রাজনীতি সক্রিয় থাকে, তাহলে তাদের কাছ থেকে অতিরিক্ত অর্থ আদায়ের সাহসই করবে না কর্তৃপক্ষ।
বিভিন্ন প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়কে ট্রাস্টিরা অন্যান্য সাধারণ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মতো বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে পর্যবসিত করে ফেলেন। শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে নিয়মিত ফি’র বাইরেও অতিরিক্ত অর্থ আদায় করে, সেই টাকা তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়নে ব্যয় করেন না। গবেষণা কিংবা শিক্ষকদের বেতন-সম্মানীতেও ব্যয় করেন না। সেই সব টাকার বেশিরভাগই আত্মসাতের অভিযোগ ওঠে বিভিন্ন প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রাস্টিদের বিরুদ্ধে। এসবই করার সুযোগ পান তারা ছাত্র-রাজনীতির অনুপস্থিতির কারণে। এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-রাজনীতি সক্রিয় থাকলে ট্রাস্টিরা কখনোই অর্থ আত্মসাতের মতো জঘন্য কর্মে জড়িত হওয়ার সাহস পেতেন না। ফলে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে অনিয়ম-দুর্নীতিমুক্ত রাখতে হলেও ছাত্র-রাজনীতির প্রয়োজন। কারণ বিভিন্ন ইস্যুতে আন্দোলন-সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হলে একটি শক্তিশালী প্ল্যাটফর্ম দরকার। রাজনৈতিক সংগঠন সেই শক্তিশালী প্ল্যাটফর্মগুলোর মধ্যে অন্যতম। একটি অভিন্ন উদ্দেশ্য ও আদর্শে লালিত একদল ছাত্র যখন কোনো আন্দোলনে নেতৃত্ব দেয়, তখন শাসকশ্রেণি পর্যন্ত বিষয়টিকে আমলে নিতে বাধ্য হয়। অন্য সাধারণ পেশাজীবী সংগঠনগুলোর দাবি অগ্রাহ্য করে, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে দিয়ে পিটিয়ে এসব সংগঠনের নেতাদের ছত্রভঙ্গ করা যায় সহজে। কিন্তু আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী দিয়ে ছাত্রদের আন্দোলন দমানো যায় না। বিশেষ করে রাজনৈতিকভাবে ছাত্ররা অনেক বেশি সুসংগঠিত থাকেন, তাই তাদের সংকল্প থেকে হটানো সম্ভব হয় না। যেখানে খোদ শাসক শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্র-রাজনীতির কারণে অনিয়ম-দুঃশাসনে ভয় পায়, সেখানে একেকটি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রাস্টিরা এমনিতেই দুর্নীতি করার সাহস পাবেন না।
ছাত্র জীবনে ছাত্ররাজনীতি বিমুখ হলে একজন নাগরিক তার জীবনের প্রস্তুতি-পর্বে সংবিধান প্রদত্ত অধিকার বঞ্চিত হবেন। এরপর রাজনীতিবিযুক্ত হয়েই ছাত্রজীবন পার করে বাকি জীবনে রাজনীতির আদর্শ পাঠ নিতেই পারবেন না। কারণ ছাত্রজীবন শেষে সাধারণত কর্মজীবনে প্রবেশ করে মানুষ। কর্মজীবনে কেউ যদি সরকারি চাকরিজীবী হন, তাহলে তার পক্ষে প্রকাশ্যে দলীয় রাজনীতি করা ভয়ানক হয়ে উঠবে। কারণ, রাজনীতি করলে তিনি তখন দলের অন্ধ সমর্থক বা কর্মী উঠবেন। তিনি যখন যে রাজনৈতিক দল ক্ষমতায় থাকবে, সে দলের নেতা-মন্ত্রীর অধীনে কাজ করবেন। প্রতিটি ক্ষমতাবান রাজনৈতিক দলের মন্ত্রীকেই তিনি ‘ইয়েস স্যার’ বলতে বাধ্য হবেন। রাজনৈতিকভাবে সম্পূর্ণ প্রতিপক্ষ দলের মন্ত্রীর কথায়ও সচিবকে ‘ইয়েস স্যারই’ বলতে হবে। কখনোই মন্ত্রীর সঙ্গে ভিন্নমত পোষণ করতে পারবেন না। এছাড়া রাজনীনিবিযুক্ত অবস্থায় ছাত্রজীবন পার করে আসা একজন আমলার পক্ষে বোঝাও সম্ভব নয়—কোন সিদ্ধান্ত রাজনৈতিক কারণে নেওয়া উচিত, কোন সিদ্ধান্ত প্রশাসনিক প্রয়োজনে। ফলে দেশের ভবিষ্যৎ কর্ণধার হয়ে গড়ে ওঠার জন্যও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজনীতি প্রয়োজন। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা রাজনীতির সুযোগ পেয়ে নিজেদের রাজনৈতিক জ্ঞানসমৃদ্ধ করে গড়ে তোলার সুযোগ পান। অথচ প্রাইভেটকে বঞ্চিত করে রাখা হয়। এটা এক ধরনের অপরাজনীতি ও বৈষম্যও। ফলে এই বৈষম্য-অপকৌশল দূর করতেও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-রাজনীতি চালু করা জরুরি। তাহলে রাজনৈতিক সচেতনতার দিক থেকে প্রাইভেট-পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মধ্যে কোনো পার্থক্য কিংবা বৈষম্য থাকবে না।
ছাত্র-রাজনীতি-শূন্যতার সুযোগে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে মুক্তিযুদ্ধ-দেশের স্বাধীনতার প্রতি সম্মানবোধ জাগে না অনেকেরই। বরং অভিযোগ রয়েছে—বিভিন্ন জঙ্গিবাদী সংগঠন এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকে পড়ে শিক্ষার্থীদের ‘জেহাদি’ কর্মকাণ্ডে প্ররোচিত করে। যেসব শিক্ষার্থী জঙ্গিবাদী কর্মকাণ্ড-উগ্রপন্থায় জড়িয়ে পড়ে, তাদের কাছে মুক্তিযুদ্ধ-দেশের স্বাধীনতা-বঙ্গবন্ধু কোনো সম্মানের বিষয় হয়ে ওঠে না। দেশপ্রেমও তাদের কাছে তুচ্ছ বিষয়। কিন্তু প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় রাজনীতি চালু থাকলে কোনো উগ্রবাদী সংগঠন, ওই সব বিশ্ববিদ্যালয়ে জঙ্গি কর্মকাণ্ড চালানোর সাহস পাবে না। উগ্রপন্থীদের সামনে তখন দেশপ্রেমী রাজনীতি সচেতন ছাত্ররা বাধার পাহাড় হয়ে দাঁড়াবে।
ছাত্ররাজনীতি বন্ধ হলে শিক্ষার্থীরা কোনো অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত হবে না, তারা সবাই পূর্ণ সময় পড়ালেখায় ব্যস্ত থাকবে— সম্ভবত এমন ধারণার বশবর্তী হয়ে প্রাইভেটে বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্ররাজনীতি বন্ধের দাবি তোলা হচ্ছে। কিন্তু একবারও কি ভেবে দেখা হয়েছে—ঔষধিগুণের কথা ভেবে সারা বাড়িতে নিমগাছ লাগিয়ে রাখলে সেই গাছ থেকে বৈশাখ মাসে আম আশা করা যাবে না। নিমগাছে কখনো আম হয়? একজন নাগরিক তার জীবনের প্রস্তুতিপর্বের পুরোটা সময় রাজনীতিবিমুখ অবস্থায় কাটালে কোন সময় রাজনীতির পাঠ নেবেন? অবশ্যই বর্তমানে অনেক আমলাকে দেখা যায়, চাকরিজীবনের পুরো সময় যখন যে দল ক্ষমতায় এসেছে, তখন সে দলের মন্ত্রী-নেতাকে ‘ইয়েস স্যার-ইয়েস স্যার’ বলতে বলতে মুখে ফেনা তুলে ফেলেন। আর চাকরি জীবন শেষে কোনো একটি দলে ভিড়ে গিয়ে প্রতিপক্ষ দলকে তুলোধুনোও করছেন। কিছুদিন পর ক্ষমতার পালাবদল হলে তিনিও পাল্লা দিয়ে ডিগবাজি খাচ্ছেন। সবসময়ই ক্ষমতাসীন দলের রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত থাকছেন। অর্থাৎ চাকরি জীবনে যেমন ক্ষমতাসীনদের চরণধূলি নেন, চাকরি জীবন শেষে রাজনীতি করতে এসেও সেই লোভ সামলাতে পারেন না। ছাত্রজীবন শেষ হওয়া মাত্রই ক্ষমতাসীন দলের সঙ্গে পেয়ে ধন্য হয়েছেন, বারবার ক্ষমতার পটপরিবর্তন হলেও প্রশাসনের কেন্দ্রবিন্দুতে তো তারাই ছিলেন। তারা নিজেদের স্বার্থে ক্ষমতাসীন দলের রাজনীতিবিদদের ব্যবহার করেছেন। আবার সময়-সুযোগ বুঝে সেনাসমর্থিত অরাজনৈতিক সরকারের শাসন আমলে রাজনীতিবিদদের বিরুদ্ধে সেমিনার-সিম্পোজিয়ামে বক্তব্যও দিয়েছেন।
এ কথা সুবিদিত—সভ্য দুনিয়ার বড় চালিশকাশক্তি রাজনীতি। রাজনীতিশূন্য সমাজ বর্বরতার জন্ম দেয়। ষড়যন্ত্রকারীরা চিরকালই সমাজ-রাষ্ট্রকে বিরাজনীতিকীকরণের দিকেই ঠেলে দেয়। বাংলাদেশেও ওয়ান-ইলেভেনের সময়ের সেনাসমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কর্মকাণ্ড স্মরণ করলে উল্লিখিত বক্তব্যের প্রমাণ মিলবে। ওই সময় বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ অসংখ্য রাজনৈতিক নেতার বিরুদ্ধে ফখরুদ্দিন-মঈনুদ্দিনরা মামলা দিয়েছিলেন। একের পর এক মামলায় শীর্ষ রাজনৈতিক নেতাদের কাবু করার হীন চেষ্টা করা হয়েছিল। এমনকি বড় বড় রাজনৈতিক নেতৃত্বের বিরুদ্ধে দুর্নীতি-ক্ষমতার অপব্যবহারের অলীক অভিযোগ এনে তাদের মাসের পর মাস কারাবন্দী করেও রাখা হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে রাজনৈতিক সরকারের আমলে শেখ হাসিনাসহ বেশিরভাগ নেতার বিরুদ্ধে দায়ের করার মামলাই মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে।
ছাত্র রাজনীতির বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ—তারা ক্যাম্পাসে র্যাগিং-হত্যাকাণ্ড-চাঁদাবাজি-টেন্ডারবাজিতে জড়িত থাকে। কিন্তু এটা শতভাগ সত্য নয়। পুলিশ, শিক্ষক, মন্ত্রী ও সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা-বিচারপতিদের বিরুদ্ধে দুর্নীতি-হত্যাকাণ্ড-চাঁদাবাজির অভিযোগ প্রায়ই ওঠে। এসব গুরুতর অভিযোগের মধ্যে কোনো কোনো অভিযোগ প্রমাণিতও হয়েছে। যেমন নারায়ণগঞ্জের সেভেন মার্ডার ও চট্টগ্রামের দশ ট্রাক অস্ত্র মামলার আসামিদের মধ্যে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরাও রয়েছেন। শিক্ষকদের বিরুদ্ধেও ধর্ষণ-স্বজনপ্রীতিসহ প্রশ্ন ফাঁসের অভিযোগ ওঠে। সেসব অভিযোগে তাদের শাস্তিও হয়েছে। এছাড়া, ব্যবসায়ীরা সিন্ডিকেট করে নিত্যপণ্যের মূল্য বাড়িয়ে জনভোগান্তিরও সৃষ্টি করেন। এসব গুরুতর অভিযোগের কারণে কখনো কখনো কেবল সংশ্লিষ্ট অভিযুক্ত ব্যক্তিরই শাস্তি হয়। কোনোভাবেই ব্যবসা বন্ধের দাবি ওঠে না, বিচারপতি-শিক্ষক-মন্ত্রীর পদ বিলুপ্তির দাবি কেউ জানায় না, হত্যাকাণ্ড ও অস্ত্র মামলায় জড়িত থাকার অপরাধে কোনো আইনশৃঙ্খলা বাহিনীও বিলুপ্ত ঘোষণা করা হয় না। কারণ, একটি রাষ্ট্র কেবল কতিপয় তথাকথিত মেধাবী-আদর্শবান নাগরিকের সমষ্টি নয়, বহু পেশা-শ্রেণী-ধর্ম-বিশ্বাস-স্বভাব-বৈশিষ্ট্যধারীরও আশ্রয়। কোনো একক ব্যক্তি বা একাধিক ব্যক্তির অপরাধের দায় পুরো শ্রেণী বা সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীর ওপর চাপানো যায় না। তাতে সমাজের জন্য কোনো মঙ্গলবার্তা বয়ে আসে না। বরং অন্যান্য শাখায়ও অমঙ্গলের ছায়া ঘনিয়ে আসে।
প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়কে ছাত্ররাজনীতিশূন্য করার আগে ভেবে দেখা দরকার—মাথাব্যথা হলে মাথা কেটে ফেলা হয় না। কারণ নির্ণয় করতে হয়। নির্বাচন করতে হয় উপযুক্ত ওষুধ। তবেই মাথাব্যথা সারে। এখন দেখতে হবে, প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্ররাজনীতি বন্ধ হলে কারা লাভবান হবেন? লাভবান হবে তারা—যারা ছাত্ররাজনীতির কারণে সমাজে স্বেচ্ছাচারিতা চালাতে পারেন না।
অন্যায়-অবিচার-অনিয়ম দেখলে ছাত্রসমাজ যাদের টুঁটি চেপে ধরে, তারা ছাত্ররাজনীতির বিরুদ্ধেই কথা বলবেন। ছাত্রসমাজ যেমন বায়ান্নের ভাষা আন্দোলন-ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান, নব্বইয়ের স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনে ভূমিকা রেখেছে, তেমনি হালের কোটা সংস্কার ও নিরাপদ সড়ক আন্দোলনেও চালকের ভূমিকায় ছিল। এসব আন্দোলনে সমাজের প্রভাবশালীদের ভিত কেঁপে উঠেছিল। ভাষা আন্দোলন, গণঅভ্যুত্থান, গণআন্দোলনের মতো, সড়কে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে কর্তৃপক্ষকে তৎপর হতে বাধ্য করেছে হালের নিরাপদ সড়ক আন্দোলন। লাইনসেন্সবিহীন চালক দিয়ে রাস্তায় গাড়ি নামানোর পথে বাধার মুখে পড়েছিলেন পরিবহন মালিকরা। একইসঙ্গে ফিটনেসবিহীন গাড়ি রাস্তায় নামানোর সাহস পাননি কেউই। এছাড়া চাকরিক্ষেত্রে সাম্প্রতিক কোটা সংস্কার আন্দোলনও সরকারকে এ বিষয়ে বিবেচনা করতে বাধ্য করেছিল।
কেউ কেউ বলবেন—ওই আন্দোলনে সাধারণ ছাত্রসমাজ ছিল, ছাত্ররাজনীতির কেউ ছিলেন না। আপাত দৃষ্টিতে, সেই দাবি ঠিক। কিন্তু গভীরতর বিবেচনায় দেখলে স্পষ্ট হবে, সেখানেও ছাত্ররাজনীতি কার্যকর ছিল। সেখানেও সাধারণ ছাত্রদের পেছনে অভিভাবকের ভূমিকায় ছিল ছাত্ররাজনীতির নেতৃত্ব।
ছাত্ররাজনীতিতে যদি কোনো ত্রুটি থেকেই থাকে, তাহলে প্রয়োজনীয় সংস্কার করা দরকার। ছাত্রসংগঠনের নেতাদের পাঠ্যবইয়ের পাশাপাশি রাজনীতি-রাজনৈতিক ইতিহাস ও মানবিক বিষয়ের পাঠ দেওয়া প্রয়োজন। প্রতিটি দিনকে সুনির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে ভাগ করা দরকার। এই সময়ের মধ্যে তাদের ক্লাস, আহার, নিদ্রা, পাঠ্যবইয়ের বাইরে ইতিহাস- সাহিত্য-রাজনীতি-রাজনৈতিক ইতিহাস, সংগীত, চিত্রকলা, চলচ্চিত্র, দর্শন পাঠ, খেলাধুলা, সংসদীয় বিতর্ক প্রতিযোগিতা থাকা উচিত। একটি রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ কর্ণধাররা ছাত্রজীবনেই রাজনীতির আদর্শিক পাঠ নেবেন। সঙ্গে রাষ্ট্রপরিচালনার ক্ষেত্রে সেসব বিষয় জানা দরকার, সেসবেরও পাঠ নেবেন। আর এসবের সঙ্গে অবশ্যই সুবচন-সুভাষণ ও সম্প্রতির চর্চাও করবেন। প্রতিদ্বন্দ্বী সংগঠনের সঙ্গে তাদের বিরোধ থাকবে আদর্শিক-বুদ্ধিবৃত্তিক-কৌশলগত। কোনোভাবেই সেই বিরোধ সংঘর্ষে রূপ নিতে পারবে না। আর এই বিষয়গুলো প্রতিমাসে অন্তত একবার তদারকি করবেন মূল সংগঠনের ছাত্রবিষয়ক সম্পাদক। তিনি মাসে একবার ছাত্র সংগঠনটির শীর্ষনেতাদের সঙ্গে মতবিনিময় করবেন। তাদের সংস্কৃতিচর্চা, মানবিক বিষয়ের পাঠ, সংসদীয় বিতর্ক বিষয়ে অগ্রগতি দেখবেন, মূল্যায়ন করবেন। এই মূল্যায়নের মাধ্যমে কেবল তাদের মেধার মূল্যায়ন হবে না, নেতৃত্বের জন্য তারা কতটা যোগ্য হয়ে উঠছেন, তারও মূল্যায়ন করা হবে।
সংগঠনের শীর্ষ নেতৃত্বে আসার জন্য চাঁদাবাজি-টেন্ডারবাজি-অস্ত্রচালনার পারদর্শিতা নয়, ইতিহাস-রাজনীতি-মানবিক বিষয়ে কতটা ঋদ্ধ, তার মূল্যায়ন করতে হবে। একইসঙ্গে সুবচন-সুভাষণ ও সম্প্রীতির চর্চায় নিজদলের নেতাকর্মীর বৃত্ত ছাড়িয়ে অন্য সংগঠন ও সাধারণ শিক্ষার্থীদের মাঝেও গ্রহণযোগ্য অবস্থা তৈরি করতে হবে। এছাড়া ছাত্র সংগঠনগুলোর নিয়মিত কাউন্সিল করতে হবে। কাউন্সিলে যাদের মনোনয়ন দেওয়া হবে, তাদের যোগ্যতা হিসেবে দেখতে হবে, পরমত-সহিষ্ণুতা, পরোপকার, সম্প্রীতি, ছাত্রসমাজ ও জনগণের ভাষা বোঝার দক্ষতা, নেতৃত্বের গুণাবলি, ছাত্রসমাজে জনপ্রিয়তা, রাজনৈতিক ইতিহাসচেতনা, মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ লালন, দেশপ্রেম, পাঠাভ্যাস, পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ, সুবচন, সুভাষণ, সুকুরমারবৃত্তি, সুরুচি ও রাষ্ট্রপরিচালনা সংক্রান্ত অন্তত প্রাথমিক জ্ঞান আছে কি না। যে ছাত্রনেতার মধ্যে উল্লিখিত গুণাবলির ঘাটতি থাকবে, তাকে ছাত্রসংগঠনের শীর্ষ পদে নির্বাচনে অযোগ্য ঘোষণা করতে হবে।
উল্লিখিত বিষয়গুলো এড়িয়ে যদি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধ করা হয়, তাহলে একসময় দেশে মেধাবী রাজনীতিকের নেতৃত্বশূন্যতা তৈরি হবে। শুরু হবে রাজনীতির দুর্বৃত্তায়ন। দেশকে বিরাজনীতিকীকরণের দিকে ঠেলে দেওয়া হবে। এতে ঘটবে অশুভ শক্তির উত্থান। সেই অশুভ শক্তি সমাজকে ঠেলে দেবে গাঢ় অন্ধকারের দিকে।
এ কথা মনে রাখা জরুরি—রাজনীতিবিদরা কেবল তথাকথিত সুশীল সমাজের নেতা নন। তাদের ভোট দিয়ে যারা নির্বাচিত করেন, তাদের মধ্যে সরকারের দুর্নীতিবাজ আমলা থেকে শুরু করে অসৎ ব্যবসায়ী, উগ্র ছাত্র, চরিত্রহীন শিক্ষকও থাকেন। আবার শ্রমিক-কৃষক থেকে শুরু করে কামার-কুমার, হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিষ্টান-মুসলমান; ফর্সা-কালো-তামাটে—সব শ্রেণী-পেশা-ধর্ম-বর্ণের নাগরিকও রাজনীতিবিদদের সঙ্গে উঠবস করেন। তাদের সুখ-দুঃখের কথা বলেন। উৎসবে-পার্বণে পরস্পরের খোঁজ নেন। কিন্তু যেসব অবসরপ্রাপ্ত আমলা কিংবা ব্যবসায়ী পেশীশক্তি-অর্থের জোরে মনোনয়ন বাগিয়ে নিয়ে জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত হন, তাদের সঙ্গে সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখের ভাবনা বিনিময় দূরে থাকুক, কালেভদ্রে দেখাসাক্ষাৎও হয় না। রাজনীতিবিদরা যতই খারাপ হন, জনতার কান্না তাদের চোখকে আর্দ্র করবেই। তারা মাটির টানে মানুষের কাছে ফিরবেনই। কিন্তু সারাজীবন রাজনীতিবিযুক্ত থেকে যে ব্যবসায়ী ও অবসরে যাওয়ার পর যে আমলা অর্থের জোরে জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত হবেন, তিনি যতই ভালো হন, পত্রিকায় বিবৃতি কিংবা কালো গ্লাসযুক্ত গাড়িতে চড়ে হাত নাড়ানোর বাইরে কিছুই করবেন না।
একথা ভুলে গেলে চলবে না—রাজনীতির কাজ রাজনীতিবিদকে করতে দিতে হবে। এদেশের বুকে যেন বারবার অনির্বাচিত ও অরাজনৈতিক শক্তি ক্ষমতায় আরোহণ করতে না পারে, তার জন্য আরও গণমুখী-কল্যাণকামী রাজনীতি চর্চা জরুরি। আর রাজনীতির আদর্শ পাঠ নেওয়া ও জনমুখী-কল্যাণকামী রাজনীতিচর্চার উপযুক্ত সময়ই ছাত্রজীবন। মনে রাখতে হবে, দেশে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়ে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা বেশি। এ কারণে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধ না করে পদ্ধতি ও গুণগত সংস্কার করা প্রয়োজন। সেই কাজটি করার সুবর্ণ সময় এখনই। দেরি করলে অপরাজনীতির রাহু এসে ছাত্ররাজনীতির সুকুমারবৃত্তিকে গ্রাস করে ফেলবে। সুতরাং সময় থাকতেই এগুলো বিবেচনায় আনা উচিত।
লেখক : কবি-প্রাবন্ধিক-সাংবাদিক।