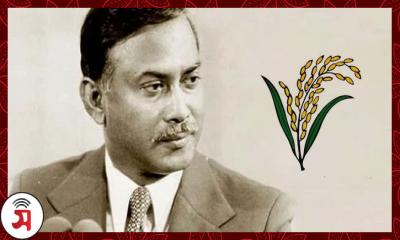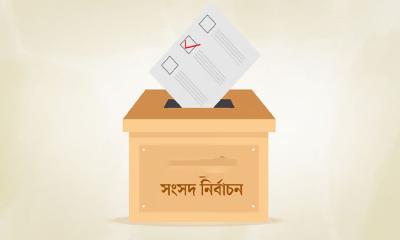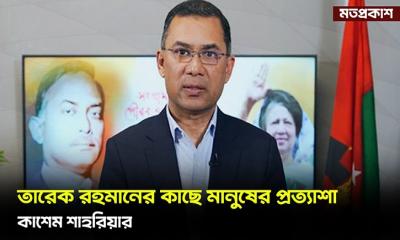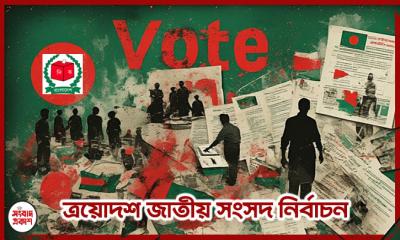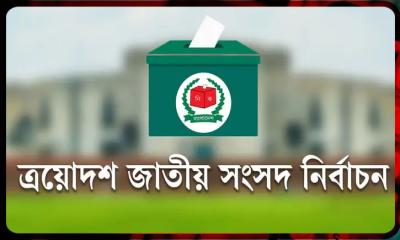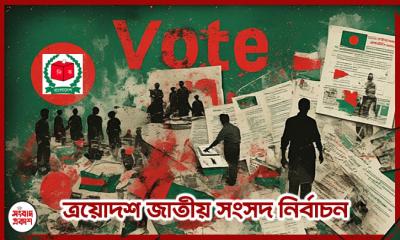বাঙালি সমাজে একটা সময়ে বলা হতো, ‘মেয়েরা লেখাপড়া শিখলে বিধবা হয়; রাঁড় হয়।’ সংস্কার এতটা নৃশংস ছিল যে শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন, ‘ভারতের কিছু অঞ্চলে, বিশেষত রাজপুত দিগের মধ্যে, সূতিকাগারে কন্যা হত্যা করার প্রথা প্রচলিত ছিল।’ ‘ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর আঁতুড় ঘরেই মুখে বিষ দেওয়া’ হতো। এ ছাড়া মর্যাদা রক্ষার খাতিরে অভিজাত হিন্দু পরিবারের মেয়েদের মধ্যে পর্দা প্রথা তো বরাবর ছিলই। স্ত্রীশিক্ষা প্রচলনের পর জমিদার বাবুরা বাড়িতে বাড়িতে লোক পাঠিয়ে মেয়েদের স্কুলে যেতে নিষেধ করতেন। তারা বলতেন ‘যে মেয়ে পাঠাবে তাকে একঘরে করব।’ সেই কালকে অতিক্রম করে শিক্ষা ও অন্যান্য ক্ষেত্রে নারী এখন যে উজ্জ্বল ভূমিকায় আবির্ভূত, তার পেছনে রয়েছে দুই শতাব্দীর দীর্ঘ ইতিহাস। তবু নারী যে এখনো সব ক্ষেত্রে মুক্ত হতে পেরেছেন, সে কথা বলা যায় না। আসলে, সমাজের সার্বিক মুক্তি ছাড়া নারী মুক্ত হবেন কীভাবে। সে কারণে জীবনানন্দের সঙ্গে আমাদেরও স্বর মিলিয়ে বলতে হয়, ‘সুচেতনা, এই পথে আলো জ্বেলে, এ পথেই পৃথিবীর ক্রম মুক্তি হবে; / সে অনেক শতাব্দীর মনীষীর কাজ।’
নবযুগের বাংলায়, উনিশ শতকে স্ত্রীশিক্ষা নিয়ে চিন্তা ও মনীষার প্রথম আলো জ্বেলেছিলেন রামমোহন রায়। রামমোহন এব্যাপারে যে খুব বেশি অগ্রসর হতে পেরেছিলেন, তা নয়। তবে এ সময় থেকে প্রধানত কলকাতা শহরে খ্রিষ্টান মিশনারিদের উদ্যোগে প্রথম স্ত্রীশিক্ষার সূচনা হয়। ১৮২১ সালে Mary Anne Cooke, যিনি ‘মিস কুক’ নামে পরিচিত, ইংল্যান্ড থেকে স্ত্রীশিক্ষার উদ্দেশ্যে কলকাতায় এসে ‘আটটি বালিকা-বিদ্যালয়’ স্থাপন করেন। তার মধ্যে ‘শ্যামবাজার স্কুল’ বিশেষ কারণে উল্লেখযোগ্য। ‘এই অঞ্চলের একজন মুসলিম মহিলা প্রায় ১৮টি বালিকা নিয়ে’ স্কুলটি শুরু করেন। ‘তাঁর অসীম উৎসাহের জন্য বালিকার সংখ্যা বেড়ে পরে ৪৫ জন হয়।’
এ দেশীয়দের মধ্যে স্ত্রীশিক্ষার ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য আওয়াজ তুলেছিলেন ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠী। ১৮৪০-এর দিকে তারা এটিকে একটি সামাজিক আন্দোলনে পরিণত করেন। ইয়ংবেঙ্গলের উদ্যোগে নারী শিক্ষা বিষয়ে প্রবন্ধ রচনা করে ‘প্রথম পুরস্কার পান মধুসূদন দত্ত এবং দ্বিতীয় পুরস্কার পান ভূদেব মুখোপাধ্যায়’।
উনিশ শতকের চতুর্থ দশকে অক্ষয়কুমার দত্ত ‘বিদ্যাদর্শন’ পত্রিকায় নারীশিক্ষা বিষয়ে লেখেন, ‘... আমরা একান্তরূপে অনুরোধ করিতেছি দয়াশীল মহাশয়েরা ঐক্যবাক্যে একত্র হইয়া এতদ্দেশীয় স্ত্রীবিদ্যার উন্নতি নিমিত্ত একটি সভা স্থাপন করুন, এবং দৃঢ়রূপে তৎ সমাজের কার্যবিষয় মনোযোগী হউন।’
এভাবে বিভিন্ন তৎপরতার মধ্যে ‘১৮৪৭ সালে বারাসাতে একটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশে সম্ভ্রান্ত বাঙালির উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত প্রথম বালিকা-বিদ্যালয় এইটি।’ যাঁরা এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, তাদের অনেক ‘লাঞ্ছনা-নিগ্রহ’ সহ্য করতে হয়েছিল। সংস্কারও তো ছিল, মেয়েরা লেখাপড়া শিখলে জাত যায়। এর প্রতিফলনও দেখা গিয়েছিল। একবার ‘একজন সম্ভ্রান্ত ইংরাজ কর্মচারী সস্ত্রীক বারাসাতের বালিকা বিদ্যালয় পরিদর্শনার্থ আসিয়া একটি দুগ্ধপোষ্য বালিকার চিবুকে হাত দিয়া আদর করাতে জাতিনাশ আশঙ্কা করিয়া বারাসাতবাসীগণ ঘোটমঙ্গল বসাইয়াছিলেন।’ তখন বারাসাত একটি ব্রাহ্মণ প্রভাবিত এলাকা।
নারীশিক্ষার ব্যাপারে এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের সূচনা হয় ১৮৪৯ সালে। স্ত্রীশিক্ষার যে পরম্পরা ক্রমশ বর্ধিত হয়েছে, এটিই ছিল তার সূচনাবিন্দু। শিক্ষা সংসদের সভাপতি ড্রিংকওয়াটার বেথুন ছিলেন এই পর্বের উদ্যোক্তা। বেথুনের (১৮০১-১৮৫১) উদ্যোগে ওই বছর প্রতিষ্ঠিত হয় ‘ক্যালকাটা ফিমেল স্কুল’, পরে ১৮৫১ সালে বেথুন সাহেবের মৃত্যুর পর স্কুলের নাম হয় ‘বেথুন স্কুল’। এ সময় কলকাতার হিন্দু সমাজে স্ত্রীশিক্ষার প্রচলন নিয়ে ‘মহা আন্দোলন’ উপস্থিত হয়। সেই পরিস্থিতির ভেতর বাংলার কবি মদনমোহন তর্কালঙ্কার শুধু স্ত্রীশিক্ষার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেননি; বেথুন সাহেবের নবগঠিত বিদ্যালয়ে প্রথমেই তাঁর দুই কন্যা ভুবনবালা ও কুন্দমালাকে ভর্তি করে দিলেন। সেদিনের আবহে এটি একটি দুঃসাহসী ঘটনা। বিদ্যাসাগর প্রথম থেকে হয়ে উঠেছেন বেথুন সাহেবের আন্তরিক সহযোগী। ‘স্কুল প্রতিষ্ঠার পরেই বেথুন সাহেব বিদ্যাসাগরকে স্কুল পরিচালনার দায়িত্ব নিয়ে তার অবৈতনিক সম্পাদক রূপে কাজ করার অনুরোধ করেন। বিদ্যাসাগর সাগ্রহে এই দায়িত্ব গ্রহণ করেন; ১৮৫০ সালের ডিসেম্বর থেকে। বেথুন সাহেবের সহযোগী হিসেবে তর্কালঙ্কার ও বিদ্যাসাগর, দুই বন্ধুর দ্বৈরথ এগিয়ে যেতে থাকে।
স্কুলে ছাত্রীদের আনা-নেওয়ার জন্য একটা ঘোড়ার গাড়ির ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সেটা নিয়েও কথা উঠেছিল; কারণ মেয়েদের গাড়ির গাড়োয়ান তো হবেন পুরুষ লোক। বিদ্যাসাগর গাড়ির পাশে মহানির্বাণতত্ত্বের একটি শ্লোক খোদাই করে দেন, ‘কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযন্ততঃ’ অর্থাৎ ‘পুত্রের মত কন্যাকেও যত্ন করে পালন করতে ও শিক্ষা দিতে হবে।’ বিদ্যাসাগর বুঝেছিলেন, ‘শাস্ত্রের দোহাই না দিলে এদেশের লোককে কিছুই বোঝানো যাবে না।’ এরপরও ‘রাস্তায় মেয়েদের স্কুলের গাড়ির দিকে লোকে হাঁ করে তাকিয়ে থেকেছে, স্কুলের গাড়ির বালিকাদের উদ্দেশে বিস্তর অভদ্র শব্দ উচ্চারণ করতে লোকের মুখ আটকায়নি। লোকজন বলাবলি করেছে এইবার কলির কাল বাকি যা ছিল হইয়া গেল।’
স্ত্রীশিক্ষা প্রচলন হওয়ার পর পক্ষে বিপক্ষে পত্রপত্রিকায় বাদ-প্রতিবাদ চলেছে। ইয়ংবেঙ্গল, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮১৭-১৯০৫) ব্রাহ্ম সমাজ (১৮২৮) ও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা (১৮৪৩), এমনকি শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতদের একটি অংশও ‘স্ত্রীশিক্ষার পক্ষে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন।’ ১৮৫৭-৫৮ সালে মাত্র ৬/৭ মাসের মধ্যে বিদ্যাসাগর হুগলী, বর্ধমান, মেদিনীপুর ও নদীয়ায় ৩৫টি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এ সময় একটি অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার জন্ম হলো। ১৮৫৮ সালের জুন মাস পর্যন্ত স্কুলের শিক্ষকদের বেতন বাবদ প্রায় সাড়ে তিন হাজার টাকা পাওনা হলো। বাংলা সরকার ভারত সরকারকে তখন অর্থ সাহায্যের জন্য সুপারিশ করলে গভর্নমেন্ট এই অর্থ দিতে স্বীকৃত হন নাই। ‘ভারত সরকার তখন সিপাহী বিদ্রোহের দুশ্চিন্তায় কাতর।’ কাজেই এ বিষয়ে তাদের কোনো মনোযোগ ছিল না। বিদ্যাসাগর এতে হতাশ হননি। তাঁর ‘চরিত্রের বৈশিষ্ট এই যে জীবনের অধিকাংশ কাজই তিনি প্রচণ্ড জিদের বশবর্তী হয়ে আরম্ভ করতেন এবং চূড়ান্ত ফলাফল না দেখা পর্যন্ত ছাড়তেন না।’ বালিকা বিদ্যালয়গুলো পরিচালনার জন্য তিনি একটি ‘নারী ভাণ্ডার’ খুললেন। সেখানে অনেক রাজা-জমিদার ও উচ্চপদস্থ ইংরেজ নিয়মিত চাঁদা দিতেন।
১৮৬৬-তে মিস মেরি কার্পেন্টার ইংল্যান্ড থেকে কলকাতায় এলেন স্ত্রীশিক্ষার আগ্রহ নিয়ে। স্ত্রীশিক্ষার সূত্রে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে কার্পেন্টারের পরিচয় ও কাজের সম্পর্ক তৈরি হলো।
মিস কার্পেন্টার বেথুন স্কুলের পাশে একটি নর্মাল স্কুল স্থাপনের চেষ্টা করলে বিদ্যাসাগর এ বিষয়ে আপত্তি করেছিলেন। কিন্তু বাংলা গভর্নমেন্ট কার্পেন্টারের প্রস্তাব অনুযায়ী অগ্রসর হলে ‘বিদ্যাসাগর এই প্রস্তাবে সম্মত না হইয়া’ ১৮৬৯ সালের জানুয়ারি মাসে পদত্যাগ করেন। ‘বিদ্যাসাগরের কথাই সত্য হলো। তিন বছর না যেতেই পরবর্তী ছোট লাট জর্জ ক্যাম্পবেল বেথুন বিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট নর্মাল স্কুলটি তুলে দেবার আদেশ দিলেন।’ এই ঘটনা থেকে বোঝা যায়, স্ত্রীশিক্ষা নিয়ে বিদ্যাসাগরের ভাবনা ও বিচক্ষণতা কতটা গভীর ছিল।
একটু খেয়াল করলে দেখা যাবে, ‘উনিশ শতকে সমাজ-সংস্কারের প্রধান কথাই ছিল নারীমুক্তি, আধুনিক অর্থে নয়, তখন নারীশিক্ষা, নারীর অধিকার এবং নারী প্রগতির দিকেই মনীষীদের দৃষ্টি পড়েছিল!’ নিঃসঙ্গ পথিকের মতো বিদ্যাসাগরও বিপৎসংকুল সেই পথে হেঁটে গেছেন।
লেখক : সাংস্কৃতিক কর্মী।