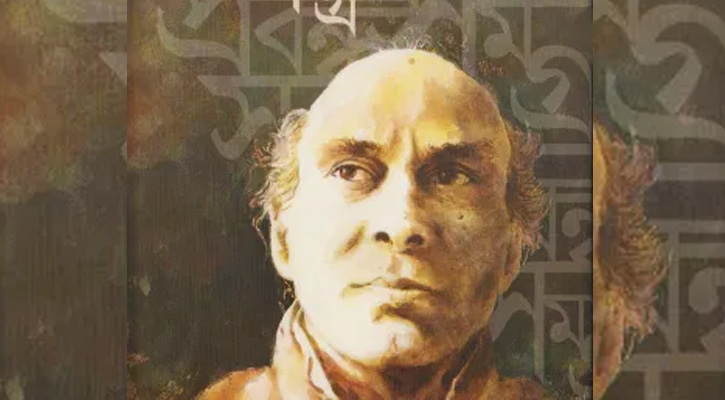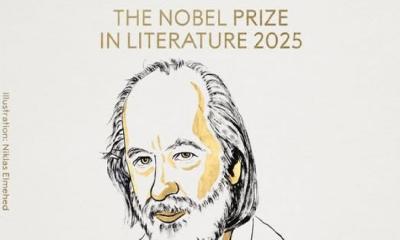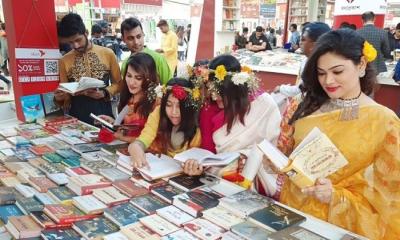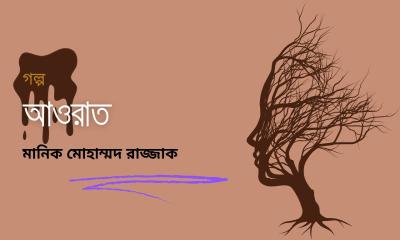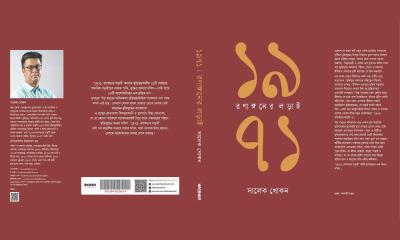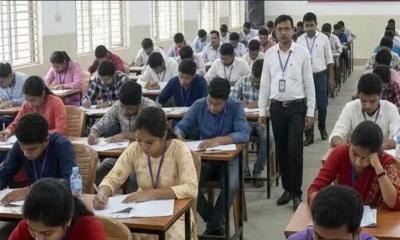হামিদ কায়সারের খুব চমৎকার লেখা আছে, রশীদ করীমের প্রয়াণের দিনটা নিয়ে। হামিদ কায়সার ছাড়া আর কোনো লোক রশীদ করীম নিয়ে ডেডিকেটেড লেখার আগ্রহ বোধ করেননি। আনিসুজ্জামানের একটা চমৎকার বক্তৃতা ছিল, নাজমা জেসমিন স্মারক বক্তৃতায়, রশীদ করীমের উপন্যাস নিয়ে। হামিদ কায়সারের লেখাটা অবশ্য কিছুটা মন খারাপেরও। কেমন জানি এলোমেলো করে দেয় সব কিছু। যেমন হামিদ কায়সার যখনই রশীদ করীমের বাসায় যেতেন, নাস্তায় ডালপুরি খাওয়াতেন। মৃত্যুর পর যখন তিনি সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যে প্রেস রিলিজ লিখছেন, তখন তাকে রশীদ করীমের মেয়ে নাবিলা মোরশেদ ডালপুরি এনে দিতে দিতে বললেন, ‘আজ বাবা নেই ডালপুরি তো আছে, আপনি তো রাত থেকেই না খেয়ে আছেন।’ হামিদ কায়সার সেই ডালপুরি আর খেতে পারেননি। নাবিলা মোরশেদ যখন তাকে ফোন দিলেন মাঝরাতে, তখন তিনি ঘুম থেকে উঠেই ফেসবুকে কিছু একটা আপডেট দিয়ে বেরিয়ে গেলেন, যানবাহন কিছু নেই, অনেকটা রাস্তা দৌড়ে তিনি নাবিস্কো মোড় থেকে রিকশা পান। যেয়ে দেখেন হাতে গোনা কয়েকজন আত্মীয় স্বজন। বেলা বাড়ল, লেখক সাহিত্যিক কয়েকজন ছাড়া তেমন কেউ আসেইনি, মিডিয়াও এসেছে অনেক পরে, বাংলা একাডেমির সাড়াশব্দ নাই। মিরপুর বুদ্ধিজীবী কবরস্থানে একটা জায়গায় মোটামুটি অপরিচিতভাবেই হলো তাঁর শেষ যাত্রা।
ব্যাপারটা খুবই মন খারাপের। ঢাকা শহরে যদি আপনি বৃদ্ধ হন, অসুস্থ হয়ে বাসা থেকে বের হতে না পারেন বছরের পর বছর, স্ত্রী ছাড়া আর কেউ থাকবে না আপনার পাশে। আপনার সামাজিক জীবন চলে যাবে চার দেয়ালে। আপনি যা যা পছন্দ করতেন তা মাথা থেকে ভ্যানিশ হয়ে যাবে। যেমন জীবনের শেষ দিকে এক ইন্টারভিউতে রশীদ করীম বলেছিলেন, ‘বয়স যখন গুনে দেখি ৮৬, ভেবে আমার নিজেরই মাথা ঘুরে। এত বয়স বেঁচেই থাকলাম।’ ক্রিকেট যিনি ভালোবাসতেন তিনি শোনেননি বাংলাদেশের ক্রিকেটের এই অগ্রগতি অবনতি। শেষ বয়সে পড়তেও পারতেন না কিছু, রবীন্দ্র সংগীত শুনতেন। তার স্ত্রী টেলিভিশন রিমোর্ট নিয়ে খুঁজে বের করতেন, কোথায় হয় রবীন্দ্রনাথের গান। আর না পেলে লং প্লেয়ারটাই ভরসা। কে এল সায়গল, পংকজ কুমার মল্লিক, কানন বালা, ওস্তাদ আমির খান এসবেই কাটতো সময়। দরিদ্র অবস্থায় তিনি মারা যাননি, বড় বড় মানুষেরা তাঁকে দেখতেও যাননি। নীরবে তিলে তিলে চলে গেছেন ২০১১ সালের এইদিনে বাংলাদেশের অন্যতম সেরা উপন্যাসিক রশীদ করীম।
রশীদ করীম, আপনাকে পড়তে আমার ভালো লাগে সবসময়। ইদানীং পড়া হয় না। আগে পড়তাম, তারপর ইচ্ছে করেই বইগুলো হাতছাড়া করেছি, যেন আপনাকে পড়তে না হয়। তবুও আপনার কথা মনে পড়ে। এই নগরে আজকাল নতুন নতুন বই এর দোকানে আপনার বইয়ের উপস্থিতি চিত্তকে আনন্দ দেয়। ইচ্ছে করেই বই হাতে নিয়ে পাতা উল্টাই। আপনার অজনপ্রিয় উপন্যাসও আমার ভালো লাগে, যেমন ধরুন প্রসন্ন পাষাণ। মাঝেমধ্যে ভারতের পত্রিকায় কলকাতা মোহামেডানের খবর দেখি, আপনার কথা মনে পড়ে। কয়েক বছর আগে জামাল ভুঁইয়া খেললো মোহামেডানে, মনে হলো রশীদ করীমকেই ট্রিবিউট দিচ্ছে। ট্রেনে কোথাও গেলে খাবার কিনলে ওনার উপন্যাসের এক সিনের কথা মনে পড়ে যায়। কিশোরদের খেলাধুলা দেখলে উত্তম পুরুষের নায়কের ফুটবল খেলার কথা মনে পড়ে। সৈয়দ মুশতাক আলী ট্রফি ভারতে হয় ঘরোয়া লিগ হিসাবে, আমার মনে পড়ে সৈয়দ মুশতাক আলী নিয়ে কি উচ্ছ্বাস ছিল। গ্যারি কুপারের পুরাতন সব সিনেমা দেখেছি রশীদ করীমের জন্য। এইভাবে কতকিছুতে রশীদ করীম জড়িয়ে আছেন। ওনার লেখার আরেকটা জিনিস আমার সব চাইতে প্রিয়, তা হলো দোদুল্যমানতা। কোথাও রশীদ করীম স্থির রাখেন না কাউকে। মানুষের মতামত যে কিভাবে ক্ষমতার পালাবদলের সাথে সাথে আমূল পাল্টে যায় তা লেখায় ফিরে ফিরে আসে বারবার। তাঁর লেখা দেখলে কে বুঝবে ওনার পিতা-মাতা কেউ বাংলাতে তেমন কথা বলতেন না। বড় বড় মানুষদের সাথে ছিল আপনার ওঠাবসা, স্নেহ পেয়েছেন বরেণ্য সব মানুষদের। তারপরেও আপনি নিজেকে খুবই সাধারণ ভাবতেন। করীম আজকালের আধুনিক মানুষদের চেয়েও বেশী আধুনিক, সেই কবে থেকেই ক্রিকেট সিনেমা মিউজিক নিয়ে কথা বলতে লিখতে ভালোবাসতেন।
এখনকার লোকজন রশীদ করীম পড়ে না, আমি বিস্মিত হই। ভারত পাকিস্তান সমর্থন করা না করা নিয়ে আলোচনা এসব আপনি কবেই লিখেছেন। মাঝেমধ্যে জীবনটাকে তুচ্ছ মনে হয়, রশীদ করীমের একটা উপন্যাসের চরিত্র হয়েও তো বেঁচে থাকতে পারতাম। তরুণ লেখকদের লেখা তিনি পছন্দ করতেন। দাওয়াত খাইয়ে প্রশংসা করতেন। সেই মনপ্রাণ উজাড় করে আড্ডা মারার দিন শেষ। এক সময় আমার প্রোফাইলে ছিল আপনার লাল গেঞ্জি গায়ে ছবি। মানুষ চিনতো না। না চিনুক। অত চিনেই কী হবে? তাঁর একটা স্মৃতিকথা আছে, মেয়ের জন্য আইসক্রিম কিনতে গিয়ে এক পথশিশুকে আইসক্রিম কিনে দিবে কিনা, তারপর সে মেয়েটার কতটুকু দায়িত্ব তিনি নিতে প্রস্তুত এরকম একটা ব্যাপার। লেখাটা এত ভালো লেগেছিল। এরকম একটা লেখা লিখতে পারলেই ধন্য ভাবতাম। কিংবা হিন্দু আইডি কার্ড দিয়ে দেশভাগের পর ভারতে কিছুদিন থাকার গল্প; এসব কেউ বলেনি। একজন একবার আমাকে বলেছিল, ‘তোমার লেখায় একটা, রশীদ করীমের মতো সাবলীলতা আছে’, প্রশংসা শুনে বাকরুদ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। যাই হোক বাংলাদেশে রশীদ করীম পাঠ বাড়ুক। ওনার মেয়ে নাবিলা মোরশেদও আমার এক লেখা পড়ে বলেছিল, ‘তোমার মতো তরুণ, রশীদ করীমকে নিয়ে এভাবে লিখতে পারে কখনো ভাবিনি।’ ভাবা হয় না অনেক কিছুই, দেশভাগের পর কলকাতা মোহামেডানের এক বিশাল তারকা খেলোয়াড়, ঢাকায় কেরানির চাকরি করবে এসব কে কবে ভেবেছিল? এসব গল্পই বলতেন রশীদ করীম।