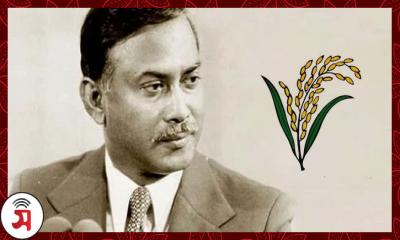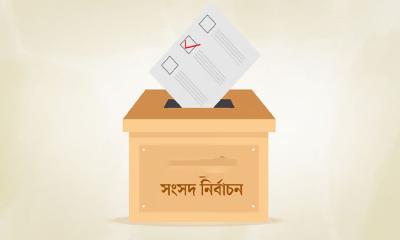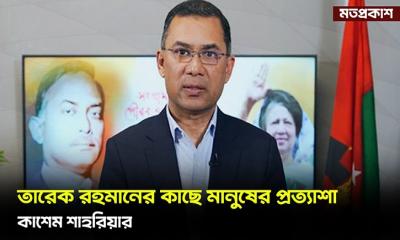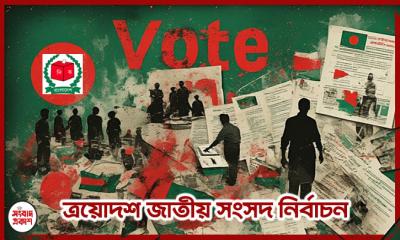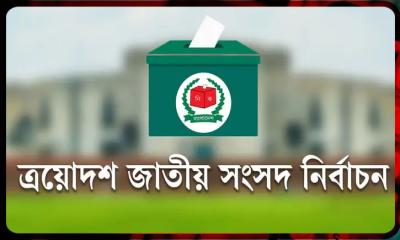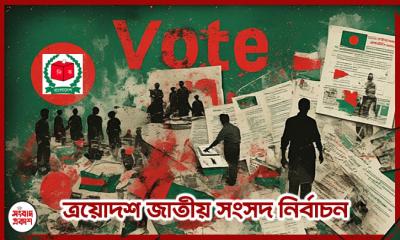দুয়ারে কড়া নাড়ছে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন। বাংলাদেশের এবারের নির্বাচনের গুরুত্ব অন্যবারের তুলনায় বেশি। ভূরাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির বিভিন্নতার কারণে এই নির্বাচন বাংলাদেশের ইলেকশন কমিশনের জন্য বড় এক চ্যালেঞ্জ। আমাদের অভ্যন্তরীণ রাজনীতির মাঠে একটা দ্বান্দ্বিক পরিস্থিতি যে বিরাজমান, তা কমবেশি সবাই জানেন। এই পরিস্থিতির মধ্যেও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক রাজনৈতিক দল ও প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। পুরোদমে চলছে ইলেকশন ক্যাম্পেইন। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকমহল বিরাজমান পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করছেন যার যার মতো করে। তবে সাধারণ মানুষের প্রত্যাশা একটি গ্রহণযোগ্য নির্বাচন।
গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রাইমারি হচ্ছে ইলেকশান। এই সত্যটি মাথায় রেখেই আমাদের ভোটের তাৎপর্য অনুধাবন করতে হবে। গণতন্ত্রের প্রথম ও শেষ কথা হচ্ছে জনগণ। শাসক ও শাসিতের মধ্যে কল্যাণপ্রসূ সেতুবন্ধন রচনা করতে গণতন্ত্রের মতো কার্যকর শাসন পদ্ধতি আধুনিক বিশ্বে আর নেই।
গণতন্ত্রের ধারণা মোটেও নবীন নয়। সভ্যতা বিকশিতরূপ লাভ করবার আগেও এক ধরনের গণতন্ত্র ছিলো। তবে, সেই সময়ের মানুষ; একে যে গণতন্ত্র বলে বা বলা যায় , সেটা হয়তো জানতো না। যিশুখ্রিষ্টের জন্মের কমপক্ষে চার শ বছর আগে ক্লিয়ান নামে একজন সমাজ চিন্তাবিদ এমন এক শাসন ব্যবস্থার কথা বলেছিলেন, যা আধুনিক গণতন্ত্রের সঙ্গে মিলে যায়। ১৮৬৩ সালের ১৯ নভেম্বর গেটিসবার্গে গৃহযুদ্ধে নিহত সৈনিকদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে আমেরিকার ষোড়শ প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিঙ্কনের দেওয়া ভাষণের অংশবিশেষ গণতন্ত্রের সর্বোৎকৃষ্ট সংজ্ঞা হিসাবে বিবেচিত হয়ে থাকে। তিনি সেদিন যা বলেছিলেন, তার বাংলা করলে এই দাঁড়ায়; (সৈনিকদের) এই মৃত্যু বৃথা যাবে না, ঈশ্বরের অধীন এই জাতির স্বাধীনতার নব জন্ম হবে। (এখানে) সরকারকে হতে হবে এমন; যা হবে জনগণের, জনগণের দ্বারা এবং জনগণের জন্য। ক্লিয়ানও একই কথা বলেছিলেন বহুশত বর্ষ আগে। ক্লিয়ান বলেছিলেন, শাসনব্যবস্থা হবে জনগণের এবং জনগণের দ্বারা।
তত্ত্ব আর তার বাস্তব প্রয়োগ—এই দুইয়ের মধ্যে বিস্তর ব্যবধান। এই বাস্তবতায় গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় মানুষের সবচেয়ে বেশি কল্যাণ কীভাবে নিশ্চিত করা যায়, এ নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। তবে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের সমর্থন যিনি বা যারা পাবেন, তিনি বা তারাই দেশের শাসনভার লাভ করবেন; এই প্রশ্নে গণতান্ত্রিক সমাজে কোনো মতভেদ নেই। কিন্তু মতের বিভিন্নতা রয়েছে; নির্ভেজাল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিশ্চিত করা যায় কেমন করে—এই প্রশ্নে। ওয়েস্টমিনস্টার ডেমোক্রেসির দেশ যুক্তরাজ্যে এবং সংসদীয় গণতন্ত্রের দেশগুলোতে মেজরিটি নিরূপণ করা তুলনামূলকভাবে সহজ। এইসব দেশে উপস্থিত ভোটার সাধারণের মধ্যে যিনি সবচেয়ে বেশি ভোট পান, তিনিই জয়যুক্ত হন। দেশের মোট ভোটারের কত শতাংশ ভোট তিনি পেলেন, সেটা বিচার্য নয়। এই ব্যবস্থাটিকে আবার অনেক দেশেই যথার্থ বলে মনে করা হয় না। অন্যদিকে, কেবল একটি নির্বাচিত পার্লামেন্টের পক্ষে জনগণের সুরক্ষা দেওয়া সম্ভব নয়, এমনটিও মনে করে অনেক দেশ। এই দৃষ্টিকোণ থেকেই অনেক দেশে প্রেসিডেন্সিয়াল ফর্ম অব গভর্মেন্ট বহাল রয়েছে। গণতন্ত্রকে তথা জনগণের সর্বাধিক কল্যাণ নিশ্চিত করার জন্য ক্ষমতার ভারসাম্য রক্ষার বিষয়টিকে জরুরি মনে করা হয়ে থাকে উভয়বিধ গণতন্ত্রে। ওয়েস্টমিনস্টার গণতন্ত্রের দেশগুলোতেও দ্বিকক্ষবিশিষ্ট পার্লামেন্টের মাধ্যমে চেক এন্ড ব্যালেন্স নিশ্চিত করা হয়। ব্রাজিল ও তুরস্কের মতো আরও কোনো কোনো দেশে কমপক্ষে ৫০ শতাংশ ভোট না পেলে, কোনো প্রার্থীকে নির্বাচিত বলে ঘোষণা করা হয় না। সেক্ষেত্রে সেকেন্ড রাউন্ড ভোটের আয়োজন করা হয়। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে নির্বাচনব্যবস্থাটি আরও জটিল। সে দেশে পপুলার ভোটের পাশাপাশি ইলেকটোরাল কলেজ পদ্ধতি চালু রয়েছে। এই পদ্ধতিটিকেই আমেরিকার আইনপ্রণেতারা সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটারের ম্যান্ডেট নিরূপণ করার উৎকৃষ্ট পদ্ধতি বলে বিশ্বাস করেন। কমিউনিস্ট দেশগুলোতেও একধরনের গণতন্ত্র রয়েছে বলে ওইসব দেশের নীতিনির্ধারকেরা দাবি করে থাকেন। আকারেপ্রকারে এটাকে তারা শোসিতের গণতন্ত্র বলে ব্যাখ্যা করেন।
প্রায়োগিক ক্ষেত্রে পদ্ধতিগত এতসব বিভিন্নতার অভিলক্ষ্য কিন্তু একটাই। আর সেটা হলো দেশের জনসাধারণের কল্যাণ সাধন।
বাংলাদেশে ১৯৭২ সালে প্রণিত শাসনতন্ত্রে সংসদীয় গণতন্ত্রের বিধান করা হলেও মাঝখানে দেশে রাষ্ট্রপতি সরকার ব্যবস্থা চালু হয়েছিল। তখন পার্লামেন্টকে বানানো হয়েছিলো রাবার স্ট্যাম্প। পার্লামেন্টের একমাত্র কাজ ছিলো রাষ্ট্রপতির সিদ্ধান্তকে সিলমোহর দিয়ে পাকাপোক্ত করা। ১৯৯০ সালে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের বিজয়ের পরে দেশে আবারও চালু হয় সংসদীয় গণতন্ত্র। নব্বইয়ের পরে বাংলাদেশে জাতীয় সংসদের ৭টি নির্বাচন হয়েছে। এর মধ্যে ছয়টি পার্লামেন্ট পূর্ণ মেয়াদ কাজ করেছে। ১৯৯৬ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারির ভোটে গঠিত পার্লামেন্ট ছিলো স্বল্পজীবী। বাকি যে ছয়টি পার্লামেন্ট পূর্ণ মেয়াদে কাজ করছে, তাও জনগণের প্রত্যাশা পূরণ করতে পেরেছে কিনা, তা তর্কাতীত নয়।
সংসদীয় গণতন্ত্রে পার্লামেন্ট ঠিকমতো কাজ করবে বা করতে পারবে কিনা, তা বহুলাংশে নির্ভর করে প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিক সাধারণের ভোটাধিকার প্রয়োগের প্যাটার্নের ওপর। সত্য বটে, নাগরিক সাধারণের একটা অংশ কোনো না কোনো রাজনৈতিক দলের কর্মী-সমর্থক। এই শ্রেণির অনেকেই নিজেদের এতটাই বুদ্ধিমান মনে করেন যে, শেষ বিচারে তাদের নিজেদের কোনো পছন্দই অবশিষ্ট থাকে না। ভোট দেওয়ার সময় তারা প্রার্থী দেখেন না, মার্কা দেখেন।
পক্ষান্তরে যারা কোনো রাজনৈতিক দলের সক্রিয় কর্মী-সমর্থক নন, তারা পরিবার পরিজন নিয়ে শান্তিপূর্ণ জীবনযাপনের নিশ্চয়তা চান। নাগরিক হিসাবে প্রাপ্য অধিকারগুলো বুঝে পেতে চান, অত্যাচারিত না হওয়ার গ্যারান্টি চান, নির্ভয় জীবন চান। সুশিক্ষা, সুবিচার, সুচিকিৎসা সব মিলিয়ে তারা চান সুশাসন।
এই শ্রেণিটিই কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ। এরা হলেন সাইলেন্ট মেজরিটি। এরা সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং সরল। এরা খুব সহজেই বিভ্রান্ত হন। এরা হুজুগে মাতেন এবং আখেরে ক্ষতির বোঝা বহন করেন।
এই সাইলেন্ট মেজরিটির সত্যিকারের যে চাওয়া; তা কোনো একটি দলের কাছ থেকে চেয়ে নেওয়ার জিনিস নয়। অসীম ক্ষমতা পেলে তার সসীম ব্যবহার করেন ; এমন ঔদার্যের দৃষ্টান্ত বিশ্বের রাজনৈতিক ইতিহাসে নেই বললেই চলে।
তাহলে অসীম ক্ষমতাই হচ্ছে মন্দ শাসনের মূল কারণ। নির্বাচনে সাইলেন্ট মেজরিটি তাদের অভিজ্ঞতা ও বিচারবোধকে কাজে লাগাতে ব্যর্থ হলে সংসদীয় গণতন্ত্রের কাঙ্ক্ষিত সুফল পাওয়া অনেক সময় কঠিন হয়ে পড়ে। সংসদীয় গণতন্ত্রে ক্ষমতার মাত্রা নির্ধারিত হয় পার্লামেন্ট দ্বারা। পার্লামেন্টে কোনো একটি মার্কা নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেলে অথবা নির্বাচিত পার্লামেন্টারিয়ানদের যুক্তি-তর্কের সক্ষমতার অভাব ঘটলে ব্রুট বা নির্দয় মেজরিটির উত্থান ঘটে। ব্রুট মেজরিটি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পার্লামেন্টকে রাবারস্ট্যাম্পে রূপান্তরিত করে। এমতাবস্থায় সাইলেন্ট মেজরিটি যদি অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে বিবেক খাটিয়ে প্রার্থীর যোগ্যতা বিচার করে ভোট দেন, তাহলেই কেবল একটি ভারসাম্যপূর্ণ পার্লামেন্ট আশা করা যায়, যেখানে থাকবে সাদাকে সাদা, কালোকে কালো বলবার মতো সাহসী ও যোগ্য পার্লামেন্টারিয়ানগণ।
বাংলাদেশের মতো একটি উন্নয়ন ও কল্যাণমুখী রাষ্ট্রের জন্য অব্যাহত সুশাসন ও গণতান্ত্রিক ধারাবাহিকতা অপরিহার্য।। জনসাধারণের সচেতন অংশগ্রহণ ছাড়া অপরিহার্যতার এই দাবি পূরণ হওয়া কঠিন। নানান সীমাবদ্ধতা আছে। তা থাকলেও তা অতিক্রম করতে হবে। মানুষ যাতে নির্বিঘ্নে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেন, তা নিশ্চিত করতে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদেরও দায়- দায়িত্ব রয়েছে। নির্বাচনের সুনির্দিষ্ট আইন-বিধিমালা আছে। সেই আইনের প্রতি প্রত্যেক ক্যান্ডিডেট এবং সমর্থকদের অবশ্যই শ্রদ্ধাশীল থাকতে হবে পূর্বাপর। ইলেকশান কমিশন ও প্রশাসন তাদের ক্ষমতা বলে প্রার্থী ও ভোটারসাধারণের কর্তব্য পালন করে দিতে পারবে না। বস্তুত যেখানে যার যতটুকু দায়িত্ব; ঠিক ততটুকু তাকেই পালন করতে হবে। তবেই জাতি পেতে পারে ফ্রি এন্ড ফেয়ার নির্বাচনের মাধ্যমে একটি কল্যাণপ্রসূ, শক্তিশালি ও কার্যকর পার্লামেন্ট।
আর, এটাই আজকের প্রত্যাশা।
লেখক : জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক ও কথাসাহিত্যিক