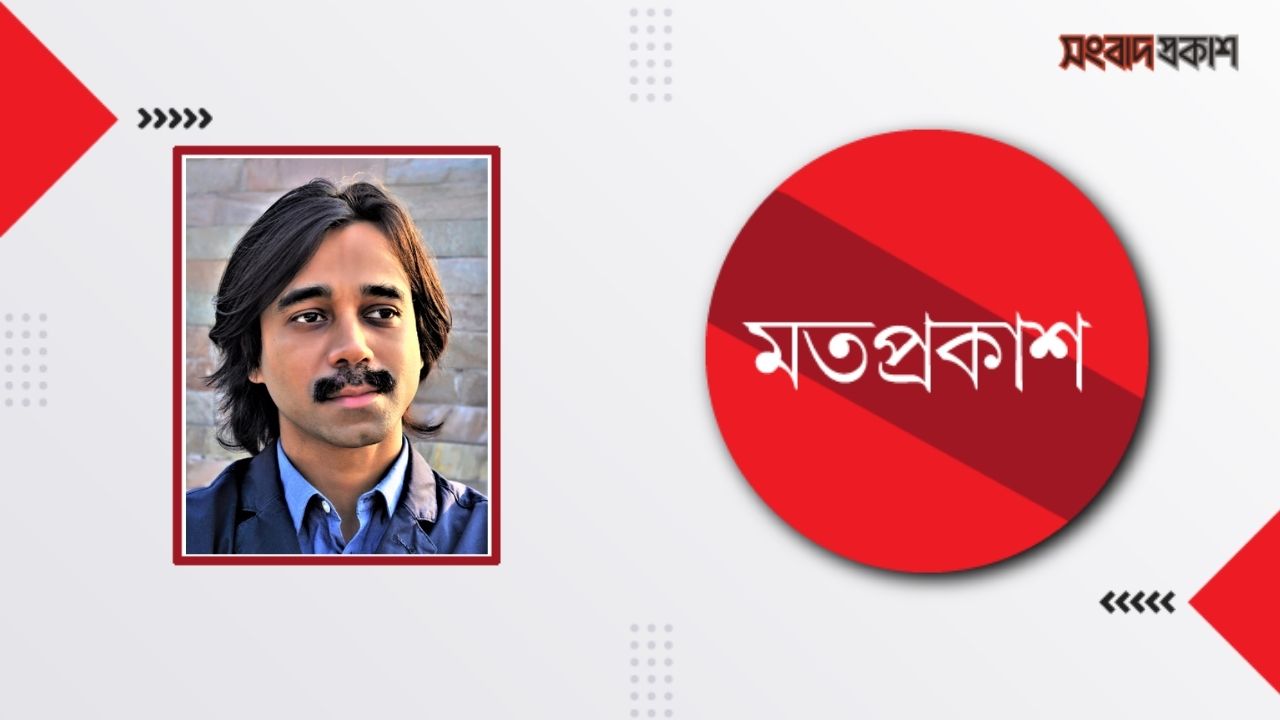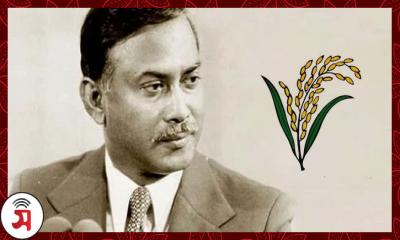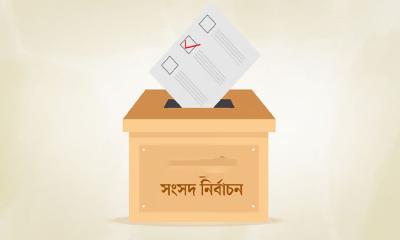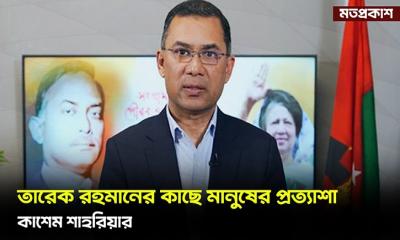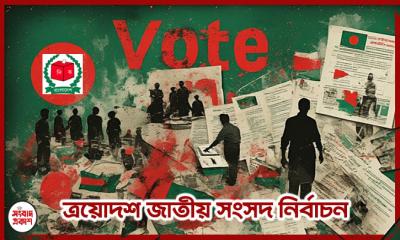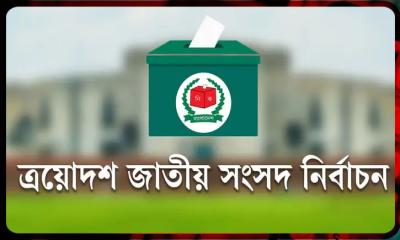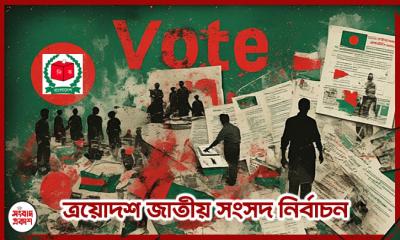দর্শকের জন্য নাটক-চলচ্চিত্র দেখার যত সহজ সুযোগই তৈরি করা হোক না কেন, বা যত আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করেই তা নির্মিত হোক না কেন, যদি নির্মাণশৈলী ও বক্তব্যে নতুনত্ব আর চিন্তার গভীরতা না থাকে তাহলে সেই নাটক-চলচ্চিত্র মানুষের মনে চিন্তাশীলতা তৈরির ক্ষেত্রে কোনো ভূমিকা রাখবে না। দর্শককে ভাবতে আগ্রহী না করে কেবল বিনোদনে বিভোর করে রাখার অর্থ তার চিন্তার সক্রিয়তা নষ্ট করা, এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক বাস্তবতার জটিল দিকগুলি অনুধাবনের জন্য তাকে অনুপ্রাণিত না করা। যে ক্ষমতাশালী শ্রেণি বা গোষ্ঠী নিজের ক্ষমতা এবং বিত্ত টিকিয়ে রাখতে উন্মুখ, তারা তাদের সুবিধা নিশ্চিত করবে এমন ধারণার প্রতিই গণমানুষের মনে আকর্ষণ আর বিশ্বাস তৈরি করতে চায়। নতুন আর প্রথাবিরোধী চিন্তা সমাজে সৃষ্টি হওয়ার মাধ্যমে সামাজিক পরিবর্তনের জন্য জনগণ জেগে উঠুক, এমন পরিস্থিতি সুবিধাভোগী গোষ্ঠী কখনোই চাইবে না। তাই প্রয়োজন হয় মানুষকে বিনোদনে বুঁদ করে রাখা। কারণ কেবল হালকা বিনোদন গ্রহণে অভ্যস্ত মানুষের মধ্যে চিন্তাঋদ্ধতা এবং সমাজ সচেতনতা তৈরি হবে না।
সাম্প্রতিক সময়ে ওটিটি (ওভার দ্য টপ) প্ল্যাটফর্ম বা ভিডিও স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্ম নিয়ে বাংলাদেশে অনেক আলোচনা এবং উচ্ছ্বাস দেখতে পাচ্ছি আমরা। নেটফ্লিক্স, আমাজন প্রাইম ভিডিওর মতো আন্তর্জাতিক ওটিটি প্ল্যাটফর্মের বিষয়বস্তু নিয়ে কথা হচ্ছে, বাংলাদেশের কোনো ভিডিও স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্ম যাত্রা শুরু করার পর জাতীয় দৈনিকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে সেই সংবাদ প্রকাশ করা হচ্ছে। বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে কোন কোন ওয়েব সিরিজ দেখা যাবে তার প্রচার চলছে সংবাদপত্রে আর সোশাল মিডিয়ায়। করোনা মহামারির কারণে বিভিন্ন সিনেমা হল বন্ধ থাকার এবং অনলাইনে দীর্ঘসময় কাটানোর এই সময়ে দিন দিন বাড়ছে ওটিটি প্ল্যাটফর্মে সিরিজ আর চলচ্চিত্র দেখার প্রবণতা। চলচ্চিত্রের বিদ্যমান বিতরণ এবং প্রদর্শন ব্যবস্থার মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন প্রেক্ষাগৃহে কম বা মাঝারি বাজেটের একটি চলচ্চিত্র দেখানোর সুযোগ পাওয়া সহজ নয়। তাই অনেক নির্মাতাই এখন ওটিটি প্ল্যাটফর্মের জন্য নাটক-চলচ্চিত্র নির্মাণে আগ্রহী হবেন। বাড়ির আরামদায়ক পরিবেশে যে কোনো সময় ছবি দেখা সহজ হয়েছে ওটিটি প্ল্যাটফর্মের কারণে। যদিও প্রেক্ষাগৃহে বড় পর্দায় চলচ্চিত্র দেখার যে ভিন্ন অভিজ্ঞতা, ভিডিও স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে মোবাইল ফোনে বা ল্যাপটপে চলচ্চিত্র দেখে সেই অভিজ্ঞতা অর্জন অসম্ভব।
ধারণা করা যায়, অনলাইন যোগাযোগের গুরুত্ব ক্রমশ বাড়তে থাকা সময়ে নাটক-চলচ্চিত্র দেখার জন্য ওটিটি প্ল্যাটফর্মের উপর মানুষের নির্ভরতা বাড়বে। ওটিটি প্ল্যাটফর্মে প্রদর্শিত ওয়েব সিরিজ আর চলচ্চিত্রের বিষয়বস্তু এবং নির্মাণশৈলী কেমন, এবং দর্শকের মনে এমন উপাদানের কী প্রভাব পড়ছে এই প্রশ্নসমূহ নিয়ে তাই চিন্তা করা দরকার। নেটফ্লিক্স, হৈচৈ, আড্ডা টাইমস প্রভৃতি স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্মের গ্রাহক হয়েছেন আমাদের দেশের অনেক দর্শক। সম্প্রতি চালু হওয়া আরেকটি স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্ম ‘চরকি’ পেয়েছে ব্যাপক প্রচার। আমরা দেখতে পাই যে বিশ্ব চলচ্চিত্রের ইতিহাসে যারা খ্যাতনামা পরিচালক হিসেবে স্থান করে নিয়েছেন, তাদের অল্প কয়েকজনের কয়েকটি মাত্র ছবিই এই সব ওটিটি প্ল্যাটফর্মে দেখা যায়। আকিরা কুরোশাওয়া, ভিত্তোরিও ডি সিকা, জঁ-ল্যুক গদার, টমাস গ্যেতিরেজ আলিয়া, গ্লবার রোশা, আলা রেনে, জিল্লো পন্টেকর্ভো, রেইনার ভেরনার ফাসবিন্ডার, আন্দজে ভাইদা, মাইকেলঅ্যাঞ্জেলো আনতোনিওনি, ইয়াসুজিরো ওজু প্রমুখ চলচ্চিত্র ইতিহাসে সাড়া জাগানো চলচ্চিত্রকার এবং এমন আরও অনেক খ্যাতনামা পরিচালকের বেশির ভাগ ছবির সাথে তো দর্শকদের পরিচয় করিয়ে দেয়ার উদ্যোগ ওটিটি প্ল্যাটফর্মে নেয়া হচ্ছে না। বাংলা চলচ্চিত্রের খ্যাতিমান পরিচালক যেমন সত্যজিৎ রায়, ঋত্বিক ঘটক, মৃণাল সেন, বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত, জহির রায়হান, আলমগীর কবিরের গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন ছবি সম্পর্কে দর্শক-মনে আগ্রহ তৈরির উদ্যোগও কি বিভিন্ন ওটিটি প্ল্যাটফর্মে গ্রহণ করা হয়েছে?
চিন্তাশীল চলচ্চিত্রের আন্তর্জাতিক পরিসরে ভারতীয় ছবি মর্যাদার আসন পেয়েছিল সত্যজিৎ রায়ের ছবির মাধ্যমে। সত্যজিৎ রায়ের বিভিন্ন চলচ্চিত্র নিয়ে এখন আমাদের সমাজে কথা বলা হয় না বললেই চলে। কিন্তু সত্যজিৎ রায়ের চারটি গল্প অবলম্বনে তৈরি একটি নেটফ্লিক্স সিরিজ, যার নামও দেয়া হয়েছে ‘রায়’ তা নিয়ে কিন্তু চলছে বিস্তর আলোচনা কারণ সোশাল মিডিয়ায় এই সিরিজের ব্যাপক প্রচার দর্শকরা দেখেছেন। এই সিরিজের চারটি পর্বের তিনটিতেই (ফরগেট মি নট, বহুরূপী, স্পটলাইট) ব্যবহার করা হয়েছে থ্রিলারধর্মী কাহিনির উত্তেজনা, নারী চরিত্রের আকর্ষণীয় উপস্থাপন, চাকচিক্যপূর্ণ দৃশ্য, অতি-নাটকীয়তা, কখনো অগভীর কৌতুক, আর সাদামাটা সংলাপ যা এই সময়ের আরও বিভিন্ন ওয়েব সিরিজ আর চলচ্চিত্রে নিয়মিত দেখা যায়। যারা সত্যজিৎ রায়ের কোনো চলচ্চিত্র দেখেননি বা তার লেখা পড়েননি, এই সিরিজের তিনটি পর্ব দেখার মাধ্যমে সত্যজিৎ রায়ের চলচ্চিত্র আর লেখায় থাকা পরিমিতি বোধ, বাহুল্যবিহীন রূপ, সূক্ষ্ম শৈল্পিক বোধ, আর নান্দনিক সৌন্দর্য সম্পর্কে তারা কোনো ধারণা পাবেন না। থ্রিলারধর্মী কাহিনির উত্তেজনা আর চাকচিক্য দেখার যে অভ্যাস বহু দর্শকের মধ্যে গত বেশ কয়েক বছর ধরে তৈরি করা হয়েছে, এই নির্মাতারা সেই অভ্যাস বাধাগ্রস্ত করতে চাননি তা বোঝা যায়। তাই, একটি পর্ব ছাড়া (হাঙ্গামা হ্যায় কিয়ো বারপা) অন্যগুলিতে সত্যজিতের কাজের ধরন প্রাধান্য পায়নি। কোনো পরিচালক তার পছন্দমতো কাজ করতেই পারেন। কিন্তু যে সিরিজে সত্যজিতের দর্শন এবং নির্মাণপদ্ধতি গুরুত্ব দেয়া হয়নি সেই সিরিজের নামকরণ সত্যজিৎ রায়ের নামে করার ফলে অনেক দর্শকের মনে সত্যজিতের চলচ্চিত্র আর লেখা সম্পর্কে ভুল ধারণা তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।
মূলধারার চলচ্চিত্রে থ্রিলার এবং অ্যাকশনধর্মী কাহিনির আধিক্য দেখি আমরা। ওটিটি প্ল্যাটফর্মেও এমন কাহিনি দেখা যাচ্ছে প্রায়ই। সম্প্রতি বাংলাদেশের তিনজন নির্মাতার তৈরি তিনটি ওয়েব সিরিজ ― মহানগর, মরীচিকা, আর লেডিস অ্যান্ড জেন্টলমেন ― দেখানো শুরু হয়েছে তিনটি ওটিটি প্ল্যাটফর্মে। মুক্তিলাভের আগেই যথেষ্ট প্রচার পেয়েছে এই তিন ওয়েব সিরিজ। সিরিজগুলিতে অভিনয় করেছেন বিভিন্ন জনপ্রিয় অভিনেতা-অভিনেত্রী। এই প্রতিটি সিরিজেই দেখানো হয়েছে পুলিশ সদস্যদের যারা কিভাবে গাড়ি দুর্ঘটনায় একজন প্রাণ হারিয়েছে, বা কিভাবে একজন নারীকে পীড়ন করা হয়েছে, বা কে খুন করেছে সেই রহস্য সমাধানের চেষ্টা করছেন। প্রায়ই দেখা যায়, পুলিশ সদস্যরা সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের ধরার জন্য ধাওয়া করছেন আর যাদের ধাওয়া করা হচ্ছে তারা প্রাণপণে ছুটছেন। এমন দৃশ্য অজস্রবার দেখা গিয়েছে এবং অহরহ দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন বাংলা-হিন্দি-ইংরেজি সিরিজ আর চলচ্চিত্রে।
যথারীতি এই সিরিজগুলিতে দেখা যায় প্রভাবশালীদের যারা অন্যায় ধামাচাপা দেয়ার চেষ্টা করছেন। তাদের কেউ রাজনৈতিক দলের সাথে ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি, কেউ যুবনেতা, কেউ কোনো প্রতিষ্ঠানের প্রধান। দেখানো হয় সুইমিং পুলের পাশে জাঁকজমকপূর্ণ পার্টি যেখানে মদের গ্লাস হাতে নিয়ে ফূর্তি করছে বিত্তশালীরা। কোনো সিরিজে অপরাধের সাথে যুক্ত ব্যক্তি ধরা পড়ে, আর কোথাও অপরাধী প্রকৃতঅর্থেই ‘ফিল্মি স্টাইল’-এ হেলিকপ্টারে বসে ‘আমার বিনাশ নাই’ এই কথা চিৎকার করে বলে পুলিশের সামনে দিয়ে স্বচ্ছন্দে পালিয়ে যায়। কোথাও নারী নিগ্রহের দায়ে অভিযুক্ত ব্যক্তি নিজেই খুন হয়ে যায়। আর যে খুনি এক সময় কেবল তার চোখের দৃষ্টি দেখেই পুলিশের গোয়েন্দা অফিসার বুঝে যায় সেই আসলে খুন করেছে।
অপরাধ উদঘাটনের জন্য পুলিশের তৎপরতা দেখানোর মাধ্যমে তৈরি করা উত্তেজনা, আকর্ষণীয় পোশাকে বিভিন্ন নারী-চরিত্রের উপস্থিতি যা নারীর প্রথাবিরোধী শক্তিশালী রূপ উপস্থাপনের পরিবর্তে হয়ে ওঠে লরা মালভি বর্ণিত পুরুষ-দৃষ্টির তৃপ্তি নিশ্চিত করার গতানুগতিক কৌশল, চিন্তাশীল সংলাপের অনুপস্থিতি, কখনো অগভীর হাস্যরস প্রভৃতি দিক থাকার কারণে এই সিরিজগুলি ভিন্ন ধরনের হয়ে ওঠেনি। আরও বহু নাটক-চলচ্চিত্রের মতোই এই তিনটি ওয়েব সিরিজেও কেন অন্যায়ের সাথে যুক্ত ব্যক্তিরা সমাজে প্রভাবশালী হয়ে ওঠে তার গভীর বিশ্লেষণ নেই। নেই সাধারণ মানুষকে একতাবদ্ধ হয়ে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হতে উৎসাহিত করার মতো কোনো বার্তা। সিরিজগুলোতে দেখানো হয় সমাজে কার্যকরভাবে প্রতিবাদ করতে পারে কেবল কোনো সৎ পুলিশ অফিসার, তেমন কেউ যার ক্ষমতা আছে। আর সাধারণ মানুষ ক্ষমতাহীন, ভোগান্তিই হলো তার নিয়তি। মূলধারার বাণিজ্যিক ছবির গতানুগতিক কাহিনিতে একজন নায়ক যেভাবে অন্যায়কারীকে প্রতিরোধ করে সাধারণ মানুষকে বিপদমুক্ত করে, এই সিরিজগুলিতে সৎ পুলিশ অফিসাররা তেমন নায়ক রূপেই উপস্থিত। কিন্তু বাস্তবে দীর্ঘস্থায়ী সামাজিক পরিবর্তনের জন্য যে একা বা কয়েকজন ক্ষমতাশালী ব্যক্তির প্রতিবাদ নয়, প্রয়োজন শোষণ আর অন্যায়ের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের সম্মিলিত প্রতিরোধ সেই সচেতনতা সৃষ্টি করার কোনো চেষ্টা মূলধারার বাণিজ্যিক ছবিতে যেমন করা হয় না, একইভাবে তা করা হয়নি এই সিরিজগুলোতেও।
সামাজিক সমালোচনা তুলে ধরা হয়েছে নানা দেশে তৈরি এমন বিভিন্ন ছবিতেই সমাজে পরিবর্তন নিশ্চিত করার জন্য সাধারণ মানুষের একতাবদ্ধ শক্তির প্রয়োজনীয়তার প্রতি নির্মাতারা দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। উল্লেখ করা যায় উৎপলেন্দু চক্রবর্তীর চোখ (১৯৮৩) চলচ্চিত্রের শেষ দৃশ্যের কথা। ক্ষমতাহীন, সুবিধা-বঞ্চিত শ্রমজীবী মানুষরা ক্ষমতাশালীদের অন্যায়ের বিরুদ্ধে এক হয়ে প্রতিবাদ করতে এগিয়ে আসে। আর তাদের পথরোধ করে দাঁড়ায় পুলিশ। কিন্তু সেই মানুষরা তখন অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার জন্য একতাবদ্ধ। তাদের দমিয়ে রাখা বা ধোঁকা দেয়া আর সম্ভব না। যে ধরনের সাংস্কৃতিক উপাদান সমাজে টিকে থাকা সমস্যার মূল কারণ বিশ্লেষণ করার পরিবর্তে দর্শককে উত্তেজনাপূর্ণ এবং চাকচিক্যময় কাহিনি দেখার তৃপ্তি দেয়ার মাধ্যমে ব্যবসায়িক লাভ অর্জনের চেষ্টা করে তা গণসংস্কৃতি নামে পরিচিত। সুবিধাভোগী এবং ক্ষমতাশালী মানুষদের মতাদর্শ এবং চিন্তার বিরুদ্ধে যায় এমন বক্তব্য গণসংস্কৃতিতে কখনোই প্রচার করা হয় না। বহু দর্শককে জৌলুশ আর উত্তেজনাপূর্ণ কাহিনির মাধ্যমে আকৃষ্ট করে মুনাফা অর্জনই গণসংস্কৃতিতে মূখ্য ফলে এই সাংস্কৃতিক উপাদানে প্রাধান্য পায় হালকা বিনোদন। মানুষের মধ্যে তৈরি করা হয় বিভিন্ন ভোগ্যপণ্য বা বিলাসবহুল জীবনযাত্রার প্রতি চাহিদা যা সাধারণ মানুষের কোনো উপকারে আসে না কিন্তু আর্থিক লাভ নিশ্চিত করে ভোগ্যপণ্য উৎপাদনকারীদের। ফলে গণসংস্কৃতি বিদ্যমান ব্যবস্থার শোষণই নিশ্চিত করে। টিকে থাকা সামাজিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে এক হয়ে প্রতিবাদ করলে এই ব্যবস্থা ভেঙ্গে যাবে, এমন বার্তা গণসংস্কৃতিতে আসে না। কিছু মানুষের ক্ষমতা প্রদর্শন যে অনেককে ক্ষমতাহীন করে রেখেছে তা বোঝানোর পরিবর্তে সাধারণ মানুষের দুর্দশা স্বাভাবিক এবং ক্ষমতাশালী কোনো ব্যক্তির সহায়তা না থাকলে সাধারণ মানুষের এক হয়ে প্রতিবাদের মাধ্যমে সামাজিক অন্যায় নির্মূল করার কোনো সুযোগ নেই এমন বার্তাই গণসংস্কৃতির উপাদানে দেয়া হয়। ফলে, এমন সংস্কৃতি শোষণের অবসান ঘটানোর জন্য সাধারণ মানুষকে উদ্যোগী হতে প্রাণিত করে না। চিন্তাবিদ হার্বার্ট মারকিউজ তাই বলেছিলেন, গণসংস্কৃতি রাজনৈতিক শোষণ আরও সংহত করে।
ওটিটি প্ল্যাটফর্মে পরিবেশিত এমন গতানুগতিক সাংস্কৃতিক উপাদানের ব্যাপক প্রচার চলছে আমাদের সমাজে। প্রচারের কারণে স্বাভাবিকভাবেই এমন উপাদান দেখছে বিভিন্ন শ্রেণির বহু মানুষ। কিন্তু সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধিতে এমন উপাদান কোনো ভূমিকা রাখছে না কারণ সমাজে সমস্যা সৃষ্টি হওয়ার মূল কারণ এবং সমস্যা নির্মূল করার প্রকৃত উপায় সম্পর্কে এমন নাটক-চলচ্চিত্রে কোনো বার্তা নেই। অথচ বিদ্যমান ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখার ক্ষেত্রে সহায়ক এমন নানা পদ্ধতিতে বিনোদন যোগানো আর ভোগবাদী জীবনযাত্রার প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি করা সাংস্কৃতিক উপাদানেরই প্রশংসা করা হচ্ছে আমাদের সমাজে। সমাজের সমস্যা নিয়ে নির্মিত এই ধরনের কাজে সমাজের গভীর বাস্তবধর্মী বিশ্লেষণ উঠে এসেছে কিনা, তা নিয়ে কি চিন্তা করা হচ্ছে? ওটিটি প্ল্যাটফর্মে নাটক-চলচ্চিত্র দেখার প্রবণতা দিন দিন বাড়বে। সিস্টেম টিকিয়ে রাখতে সহায়ক গণসংস্কৃতির এমন গতানুগতিক উপাদানই কি এখানে প্রাধান্য পাবে? নাকি সামাজিক এবং রাজনৈতিক সচেতনতা, নান্দনিক ও শৈল্পিক বোধ, ইতিহাসজ্ঞান, আর সামাজিক অন্যায় বাস্তবে কার্যকরভাবে প্রতিরোধ করার প্রকৃত উপায় প্রভৃতি সম্পর্কে দর্শক-মনে ধারণা সৃষ্টি করতে পারে এমন উপাদানের প্রতিই এই প্ল্যাটফর্মে বেশি গুরুত্ব দেয়া হবে? এই প্রশ্নগুলি নিয়েই চিন্তা করা জরুরি কারণ উপাদানের গুণগত মান না বাড়লে কোনো নতুন মাধ্যমের সাহায্যেই মানুষের এবং সমাজের কল্যাণ সাধন সম্ভব নয়।
লেখক: অধ্যাপক, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।