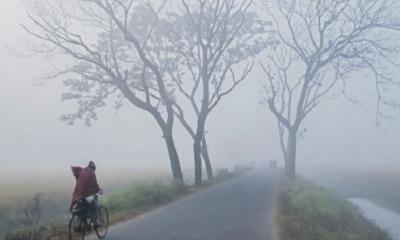একটি গল্প বা উপন্যাসের মধ্যে আমরা কতটুকু দর্শন চাই, অথবা একজন লেখক তার দর্শনকে লেখায় কতখানি নিয়ে আসতে চান? মনে হয় এটা বললে অন্যায় হবে না যে রবীন্দ্রনাথ-পরবর্তী বিংশ শতাব্দীর একটা বড় অংশ জুড়ে বাংলা সাহিত্যে মার্ক্সবাদী দর্শনের প্রায়োগিক অংশ (তাত্ত্বিক অংশ নয়) এক বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে। মার্ক্সের উৎস হলো জার্মানি, সেই জার্মানি গত তিনশ বছর ধরে দর্শন চর্চার অন্যতম ভিত্তিভূমি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর বিশ্বসাহিত্যে জার্মান দর্শন বেশ কিছু জায়গায় প্রভাব রেখেছে। আজকের আলোচনাটি মার্ক্সীয় প্রভাব নিয়ে নয়, বরং কিছুটা ধ্রুপপি জার্মান দর্শন নিয়ে। আলোচনাটি সম্পূর্ণ নয়, বরং জার্মান বা পশ্চিমের সাহিত্যে একক মানুষের অন্তর্দ্বন্দ্ব নিয়ে কিছু তথ্যের অবতারণা।
ইমানুয়েল কান্ট দিয়ে শুরু করি, উনি বললেন, বাস্তবের জিনিসপত্র আমরা তাদের স্বরূপে দর্শন বা অনুভব করতে পারি না, শুধু তার প্রকাশ্য রূপটা প্রতীয়মান হয় মনের ভেতর। আর এই যে মনের মধ্যে বাইরের জিনিসটার যে বৈশিষ্ট্য আমরা দেখি, তা আমাদের মন কীভাবে গঠিত তার ওপর নির্ভর করে। আর দর্শিত জিনিসটির অন্তর্নিহিত রূপ একটি রয়েছে, কিন্তু সেটি থাকবে আমাদের মনোজগতের বাইরে। একক ব্যক্তির ভূমিকা এখানে অপরিসীম। ইউরোপে রোমান্টিক আন্দোলনে কান্টের ভূমিকা রয়েছে, শিল্পীর স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশেই সৃজন, ব্যক্তির ভূমিকা সেখানে মুখ্য। কিন্তু এটা এমন নয় যে লেখকরা কান্ট পড়ে অনুপ্রাণিত হয়ে রোমান্টিক লেখা লিখেছেন, চিত্রকররা রোমান্টিক ছবি এঁকেছেন। বরং শিল্প-বিপ্লবের শুরুতে যান্ত্রিক সভ্যতা থেকে দূরে থাকতে চেয়ে অনেকে মানুষের ব্যক্তিগত বোধকে গুরুত্ব দিতে চেয়েছেন। ইউরোপে সেসময় ওয়ার্ডসওয়ার্থ লিখলেন Tintern Abbey, কিছু পরে এমিলি ব্রন্টি লিখলেন ‘Wuthering Heights’, আর বাংলায় বঙ্কিমচন্দ্র ‘কপালকুণ্ডলা’।
জার্মান ভাষায় একটা কথা আছে জাইটগাইস্ট (zeitgeist), যা কিনা একটা যুগের সত্তা, আমি রোমান্টিসিজমকে একটা সময়ের বা যুগের সামগ্রিক বোধ হিসেবে ভাবতে পারি। ‘জাইটগাইস্ট’ কথাটি কান্টের উত্তরসূরি গিওর্গ হেগেলের সঙ্গে অনেকে যুক্ত করেন, হেগেল ব্যক্তিগত বোধের বদলে ঐতিহাসিক একটি বোধকে সামাজিক নিয়ন্ত্রক হিসেবে দেখেছিলেন। হেগেল বলেছিলেন মানুষের সমস্ত বুদ্ধিবৃত্তিক ইতিহাস হলো মনোজগতের সঙ্গে প্রাকৃতিক বাস্তবতার ক্রিয়া, প্রতিক্রিয়া ও সংশ্লেষণের প্রক্রিয়া – একধরনের দ্বান্দ্বিক ঘটনা। এখানে আমি মনোজগৎকেও ‘জাইটগাইস্ট’ হিসেবে ধরে নিতে পারি। অন্যদিকে মার্ক্সবাদী দ্বান্দ্বিকতায় ব্যক্তিগত মনোজগতের ভূমিকা প্রায় নেই, সেখানে সামাজিক সম্পর্কগুলোর মধ্যেকার (যেমন অর্থনৈতিক শ্রেণিসমূহের মধ্যে) দ্বন্দ্বই প্রধান। মার্ক্স ও এঙ্গেলস ধ্রুপদিমনোবাদী জার্মান দর্শন (যা কিনা প্রথমে কান্ট ও হেগেল, এবং পরে শোপেনহাওয়ার দিয়ে প্রভাবিত হয়েছিলে) থেকে বেরিয়ে আসতে চেয়েছিলেন।
শোপেনহাওয়ার বলেছিলেন বেঁচে থাকার ইচ্ছাই হলো মূল চালিকাশক্তি, কিন্তু বেঁচে থাকতে হলে এককের সাথে সমাজের দ্বন্দ্ব অনিবার্য, আর তা নিয়ে আসে একধরনের বেদনা, হতাশাবোধ। এর থেকে মুক্তির উপায় হতে পারে হয় বুদ্ধিবৃত্তিক নান্দনিক সৌন্দর্যচর্চা, অথবা জীবনের থেকে একধরনের দার্শনিক বিযুক্তি। অন্যদিকে ফ্রিডরিখ নিচা (Nietzsche) শোপেনহাওয়ারের হতাশাবোধ নাকচ করে দিয়ে বললেন, মানুষের মুক্তির পথ হলো এক প্রবল ইচ্ছাশক্তির জোরে সমস্ত বাধাবিপত্তি পেরিয়ে নিজেকে ‘অতিমানব’ (Ubermensch) বানানো। নিচা তাঁর Thus Spake Zarathustra উপন্যাসে এই ধরনের অতিমানবের ধারণাটি উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছিলেন। জারাথুস্ট্রকে ঠিক উপন্যাস বলা হয়তো সংগত নয়, এবং সেখানে নিচা কী বলতে চেয়েছেন তা কিছুটা ধোঁয়াশাই থেকে গেছে।
অনেকে দস্তয়েভস্কির ‘অপরাধ ও শাস্তি’ উপন্যাসটিকে ফ্রিডরিখ নিচার দর্শনের উপস্থাপনা মনে করেন। রাসকলনিকভ, উপন্যাসের মূল চরিত্র, মানুষকে উত্তম আর অধম বৈশিষ্ট্য দিয়ে ভাগ করেছিল। উত্তম, বা অতিমানব, তার প্রবল ইচ্ছাশক্তিতে নৈতিকতার বন্ধনকে খর্ব করতে পারে, অন্যদিকে অধম সামাজিক রীতিনীতিকে মেনে চলতে বাধ্য। হেগেলও মাঝেমধ্যে মানুষকে এ রকম অতিমানব চরিত্রে ভূষিত করেছিলেন যে কিনা কোনো ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করবে সাধারণ মানুষের নীতিবোধের বাইরে।
অন্যদিকে শোপেনহাওয়ারের অবস্থানের সঙ্গে বৌদ্ধ নির্বাণের একটি সংযোগ সহজেই দেখা যায়। হেরমান হেসের ‘সিদ্ধার্থ’ উপন্যাসটি সেটির একটি সরাসরি উপস্থাপনা। আমি এখানে এই উপন্যাসটির একটি সারসংক্ষেপ দিচ্ছি, পাঠক চাইলে সেটি উপেক্ষা করে পরবর্তী প্যারায় যেতে পারেন।
সিদ্ধার্থ মোক্ষ লাভের উদ্দেশ্যে গৃহত্যাগ করে দেহ ও মনের নিয়ন্ত্রণের জন্য যে সমস্ত পদ্ধতি আছে তা সবই আয়ত্ত করেছে। তবু সে অতৃপ্ত। এই পর্যায়ে সে গৌতম বুদ্ধের সান্নিধ্যে আসে, বুদ্ধের কথা শোনে – নির্বাণের পথ হল জগৎসংসারের সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা থেকে নিজেকে সরিয়ে নেওয়া। সিদ্ধার্থ যে এই পথে অবিশ্বাস করে এমন নয়, কিন্তু সে মনে করছে এই পথ তাকে আত্মোপলব্ধি – নিজেকে চিনতে – সাহায্য করবে না। সিদ্ধার্থ আত্মসংযমের পথ থেকে সরে এসে নিজেকে ভোগবাদে বিসর্জিত করে। সে ধনী হয়, কমলা নামে এক বারনারীকে প্রেমিকা হিসেবে গ্রহণ করে, কিন্তু তার আত্মার তৃপ্তি হয় না। সমস্ত বিষয়বস্তু ত্যাগ করে সিদ্ধার্থ এক নদীর পাড়ে তার জীবন গড়ে তোলে, যেখানে তার পথপ্রদর্শক হয় এক সাধারণ মাঝি বাসুদেব এবং সেই নদী। অনেক বছর পরে কমলা, যে তখন গৌতম বুদ্ধের শিষ্যা, বুদ্ধকে দেখতে যাবার উদ্দেশ্য এই নদীপাড়ে এলে, এক সাপ দিয়ে দংশিত হয়। মৃত্যুপথযাত্রী কমলা তার সঙ্গের বালকটিকে সিদ্ধার্থর ছেলে বলে পরিচয় করিয়ে দেয়। সিদ্ধার্থ তার ছেলেকে পালন করতে গিয়ে ব্যর্থ হয় এবং বিদ্রোহী ছেলে বাড়ি ছেড়ে চলে যায়। বাসুদেব সিদ্ধার্থকে উপদেশ দেয় যে, সিদ্ধার্থ যেমন নিজের জীবনের পথ খুঁজতে বাড়িছাড়া হয়েছে তেমনই তার সন্তানকেও তার নিজের পথ খুঁজে নিতে হবে এবং সিদ্ধার্থকে নদীর স্রোতের মধ্যে জীবনের উত্তর খুঁজতে বলে। সিদ্ধার্থ মনোযোগ দিয়ে নদীকে দেখে, শুনতে চায় নদী কী বলছে, তার মধ্যে আবিষ্কার করে জন্ম ও মৃত্যুর খেলা, চরাচরের একাত্মতা। বাসুদেব সিদ্ধার্থর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বনে চলে যায়। বহু বছর পর সিদ্ধার্থর বাল্যবন্ধু গোবিন্দ, যে কিনা গৌতম বুদ্ধের শিষ্যত্ব গ্রহণ করছিল, শুনতে পায় এক জ্ঞানী খেয়াপারের মাঝির কথা। সিদ্ধার্থর সঙ্গে গোবিন্দের দেখা হয়; গোবিন্দকে সিদ্ধার্থ বলে, জ্ঞান বিতরণ করা যায়, কিন্তু গভীর জ্ঞানকে শেখানো যায় না, নদী ও একজন সাধারণ মানুষ বাসুদেবের কাছ থেকে সে এই শিখেছে।
হেরমান হেস সিদ্ধার্থর মধ্যে এমন এক চরিত্র গঠন করলেন, যে কিনা গৌতম বুদ্ধকে আত্মস্থ করে তাঁকে ছাড়িয়ে যেতে চাইল। তাঁর উপন্যাসের ভাষা সহজ, সেই সরলতায় জীবনের পথকে বর্ণনা করা হয়েছে। ‘সিদ্ধার্থে’ হেস শোপেনহাওয়ারের ‘জীবন থেকে বিযুক্তি’ এনেছেন, বুদ্ধের ‘নিরাসক্ত জীবন’ এনেছেন, কিন্তু সেটাকে ছাড়িয়ে নিয়ে এলেন ভালোবাসা – যা কিনা ‘নিরাসক্ত ভালোবাসা’ নয়। একইসাথে এই অভিব্যক্তিটিও স্পষ্ট যে, শেষ উত্তর বা মুক্তির পথ বলে কিছু নেই, পুরোটাই হলো অভিযান – সেই নদীর মতো।
কিন্তু দার্শনিক রচনা লিখতে হলে লেখককে হয় একধরনের দর্শনে নিমজ্জিত থাকতে হবে (রবীন্দ্রনাথ যেমন ছিলেন) অথবা একধরনের আধ্যাত্মিক শূন্যতায় (হয়তো জীবনানন্দ যেমন) থাকতে হবে। হেরমান হেসকে সেই শূন্যতা গ্রাস করেছিল যেখান থেকে থেকে তিনি বার হতে চাইছিলেন। সিদ্ধার্থর পরে তিনি ‘স্টেপেনওলফ’ নামে একটি উপন্যাস লিখেছিলেন। মূল চরিত্র হান্স হ্যালার, এক মধ্য বয়সী পুরুষ, তার তথাকথিত বুর্জোয়া অস্তিত্বকে ঘৃণা করত কিন্তু তার থেকে বার হয়ে আসতে পারত না। হান্স হ্যালারকে হেস নেকড়ে’ বলে অভিহিত করেছিলেন, তাকে মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে একটি সেতু হিসেবে দেখাতে চেয়েছিলেন।
এই আলোচনায় টমাস মান বা কাফকাকে নিয়ে আসা যায়। তাদের সাহিত্যেও, যেখানে একক মানুষের অন্তর্দ্বন্দ্ব প্রধান হয়ে দেখা দেয়, সেখানে বাংলা সাহিত্যে একক মানুষ অনেকাংশে সমষ্টির মধ্যে বিলীন হয়ে যায়। মার্ক্সবাদী শ্রেণিদর্শন সেখানে মুখ্য হয়ে দাঁড়ায়। একক মানুষকে চিত্রিত করা হয় তাঁর শ্রেণিগত সংযোগের তুলিতে, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সে বিদ্রোহী হলেও অসহায়, কারণ অন্যায় ও ন্যায়ের ভূমিকা আর্থসামাজিক শ্রেণি দিয়ে নিয়ন্ত্রিত। এই আলোচনার প্রেক্ষিতে ‘গল্পপাঠে’ প্রকাশিত গল্পগুলোকে পাঠক পর্যালোচনা করতে পারেন, সেগুলিতে লেখকেরা কি তাদের প্রটাগনিস্টদের সৃষ্টি করেছেন অনন্য গুণাবলি দিয়ে নাকি তাদের বৈশিষ্ট্যগুলি সামাজিক প্রেক্ষাপট দিয়ে নির্দিষ্ট হয়েছে। এটার হয়তো সরাসরি উত্তর নেই, সবকিছুই হলো বোধের মিশ্রণ, হয়তো সময়ের (যুগের) ‘জাইটগাইস্ট’ সবকিছু নির্ধারণ করছে। তবু এটা হতে পারে ভাবনার খোরাক।